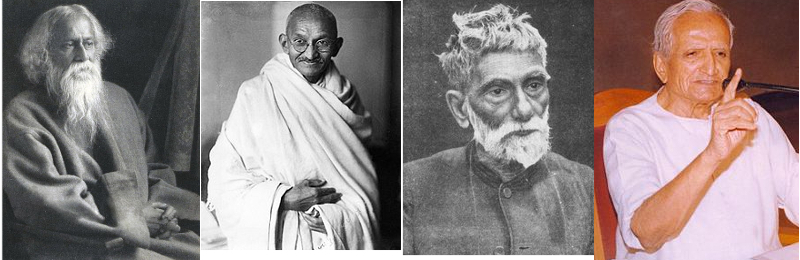দেখতে দেখতে স্বাধীনতার সাত দশক অতিক্রান্ত হল। স্বাধীন ভারতবর্ষ আজ সত্তরোর্ধ। যদিও জাতীয় জীবনে সত্তর বছর এমন কিছু নয় তবুও অনুসন্ধিৎসু মন মূল্যায়ন করতে চায়। মনে হয় বিশ্লেষণ করে দেখি এই সত্তর বছরে দেশ কতদূর এগোল। অগ্রগতির পথে কতটা সাফল্য পেল, ব্যর্থই বা হল কোন ক্ষেত্রে। একটি দেশের সাফল্য ব্যর্থতা বিশ্লেষণের তো অনেক ক্ষেত্র আছে বর্তমান প্রবন্ধে আমরা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দেশের সাফল্য ব্যর্থতা খতিয়ে দেখবো।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর যখন বিধ্বস্ত ইয়োরোপের দেশসমূহের হাত থেকে তাদের এশিয়া ও আফ্রিকাস্থিত উপনিবেশগুলি স্বাধীন হল তখন তারা প্রত্যেকেই চেয়েছিল তাদের দেশের অর্থনীতির উন্নতি করতে। এই তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহ বিগত দুই বা তিনদশক ধরে ইয়োরোপের দেশগুলির অধীন ছিল। এই দুই বা তিনদশকে তাদের রীতিমত শোষণ করে ইয়োরোপের দেশগুলি তখন নিজেদের দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করেছিল আর ক্রমাগত শোষিত হতে হতে এশিয়া ও আফ্রিকাস্থিত দেশগুলির অর্থনীতি তখন পতনের শেষ সীমায়। স্বাধীনতার পর স্বাভাবিকভাবেই সেই দেশগুলি চেয়েছিল তাদের এতদিন পরাধীন করে রাখা ইয়োরোপের দেশগুলির মত অর্থনীতিতে সমৃদ্ধ হতে এবং তখন তাদের মনে হয়েছিল যে ইয়োরোপের দেশগুলির মত উন্নত অর্থনীতির অধিকারী হতে গেলে তাদের সেই অর্থনৈতিক পথেরই পথিক হতে হবে অর্থনীতির যে পথের পথিক ছিল তৎকালীন ইয়োরোপীয় দেশসমূহ। শুধু ইয়োরোপ কেন তৎকালীন সমগ্র বিশ্বের অর্থনীতি মূলতঃ দুটি ধারাপথে প্রবহমান ছিল, একটি সোভিয়েত রাশিয়া নির্ভর সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি যা মার্কস্ প্রণীত এবং অন্যটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নির্ভর ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি যা মূলতঃ কেইন্স প্রণীত। সদ্যস্বাধীন এশিয়া ও আফ্রিকার দেশসমূহ (যাদেরকে একত্রে তৃতীয় বিশ্ব বলা হত) এই দুটি ধারার মধ্যে যে কোনও একটিকে বেছে নিয়েছিল। হয়তো তাদের এহেন অনুকরণের মানসিকতার পেছনে দীর্ঘ পরাধীনতার জন্য সৃষ্ট “দাসসুলভ দুর্বলতা” (স্বামী বিবেকানন্দ কথিত) দায়ী ছিল। কিন্তু ভারত ছিল এব্যাপারে ব্যতিক্রম, স্বাধীনতার পর ভারতের অর্থনীতি চালিত হয়েছিল মিশ্র অর্থনীতি নামক এক আলাদা অর্থনৈতিক পথে। তা বলে একথা ভেবে আত্মশ্লাঘা বোধ করা উচিত নয় যে ভারত পরানুকরণ না করে অর্থনীতির নিজস্ব কোনও পন্থা অবলম্বন করেছিল। মিশ্র অর্থনীতি অনুকরণমুক্ত আলাদা কোনও অর্থনৈতিক পথ নয় বরং মিশ্র অর্থনীতি গড়ে উঠেছিল সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি এবং ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি উভয়কেই অনুসরণ করে। মিশ্র অর্থনীতি ছিল সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির মত রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত আবার ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির মত ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও ব্যক্তিগত বিনিয়োগের অধিকার ছিল তাতে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, সোভিয়েত ইউনিয়নের ভক্ত ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নেহরু দেশকে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ধারাপথেই প্রবাহিত করতে চেয়েছিল কিন্তু শাসকদল কংগ্রেসের অনেক নেতাই ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির সমর্থক হওয়ায় দেশকে সম্পূর্ণভাবে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির পথেই প্রবাহিত করতে ব্যর্থ হয় নেহরু, আবার প্রধানমন্ত্রীর মত অগ্রাহ্য করে দেশ সম্পূর্ণ ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির পথে চলতেও অপরাগ হয়। সেকারণে ভারতীয় অর্থনীতি তখন চালিত হয়েছিল ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক উভয় প্রকার অর্থনীতিরই অনুকরণে সৃষ্ট মিশ্র অর্থনীতি নামক এক হাঁসজারু অর্থনীতির দ্বারা।
এই মিশ্র অর্থনীতিতে সোভিয়েত ধাঁচে বড় বড় রাষ্ট্রায়ত্ব কলকারখানা ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হল, পাশাপাশি ব্যক্তিগত বিনিয়োগে স্থাপিত কলকারখানা ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান সমূহও রইলো কিন্তু সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির নিয়মানুসারে তাদের মধ্যে ছিল না কোনও পারস্পরিক প্রতিযোগিতা। বিনিয়োগ ও বিপণনের ক্ষেত্র পৃথক করা ছিল রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের দ্বারা।
এই হাঁসজারু অর্থনীতির ফল হল মারাত্মক, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা না থাকার কারণে অন্যান্য ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মত শিল্প ও পরিষেবাক্ষেত্রের গুণগত মানের উৎকর্ষ সাধন ঘটলো না, উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশও ঘটলো না, বিনিয়োগের ক্ষেত্র রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের অধীন থাকায় নতুন বিনিয়োগকারীরা উঠে আসতে পারলেন না আবার বিপণনের ক্ষেত্র রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের অধীন থাকায় আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতির প্রকোপও বৃদ্ধি পেল সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির দ্বারা চালিত অন্যান্য দেশগুলির মতোই, আবার সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির দ্বারা চালিত অন্যান্য দেশগুলিতে বিপুল রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগের মাধ্যমে যেমন উন্নত পরিকাঠামো ও শক্তিশালী ভারী শিল্পক্ষেত্র সৃষ্টি হয়েছিল, ভারতে তাও হল না, কারণ ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার, ব্যক্তিগত বিনিয়োগের অধিকার ও ব্যক্তিগত লভ্যাংশ কুক্ষিগত করার অধিকার বজায় থাকায় রাষ্ট্রের হাতে বিনিয়োগ করার মত প্রয়োজনীয় অর্থ ছিল না, সেই অর্থ কুক্ষিগত হয়েছিল কতিপয় ব্যবসায়ীর হাতে অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক দেশগুলির মতোই আর্থিক বৈষম্য দেখা গেল ভারতে অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক উভয় অর্থনীতির যা যা ক্ষতিকর দিক তা দেখা গেল এই মিশ্র-অর্থনীতির মধ্যে, কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক উভয় অর্থনীতির যে সামান্য ভালো দিক আছে তার থেকেও বঞ্চিত হল ভারতীয় অর্থনীতি, ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে অবাধ প্রতিযোগিতা “SERVIVAL OF THE FITEST” বা “যোগ্যতমের উৰ্দ্ধতন ঘটায়, “মিশ্র অর্থনীতিতে” “SERVIVAL OF THE RICHEST” বা ধনীতমের উৰ্দ্ধতন ঘটল, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে বিপুল রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ “BIG PUSH” নীতির দ্বারা অর্থনীতির বিকাশ সাধন করে, মিশ্র অর্থনীতিতে স্বল্প রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ “SMALL PUSH” নীতিতে পরিণত হয়ে শুধুমাত্র দুর্নীতি মহীরুহের গোড়ায় সার জল দিল।
একারণে এই সময় দেশে মৌলিক বুদ্ধির অধিকারীরা তাদের পরিকল্পনার বিকাশ সাধনে সফল হয়নি, সেই সুযোগ তারা পাননি এদেশে, তাদের মধ্যে অনেকেই তাই দেশত্যাগ করে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির দেশে গিয়ে সেখানকার মুক্ত পরিবেশে নিজেদের উদ্ভাবনী ক্ষমতার বিকাশ ঘটালেন, ফলস্বরূপ উপকৃত হল সেইসব দেশের অর্থনীতি, ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির সুফল তারা তুলল পুরোমাত্রায়, ব্যর্থ হল ভারত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় মণি ভৌমিকের কথা, উন্নত মেধার অধিকারী এই মহান গবেষক তার কাজের উপযুক্ত পরিবেশ ভারতে না পেয়ে চলে গেছিলেন ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রধান পৃষ্ঠপোষক দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, সেখানে মুক্ত অর্থনীতির মুক্ত পরিবেশে তার প্রতিভা, বিকাশের সর্বোচ্চ সোপানে আরোহন করে, ভারতীয় প্রতিভাবানের প্রতিভায় লাভবান হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।
ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির সুফল লাভে ভারত বঞ্চিত হলেও ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির কুফল লাভে ভারত বঞ্চিত হয়নি। ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও ব্যক্তিগত বিনিয়োগের অধিকার থাকায় অন্যান্য ধনতান্ত্রিক দেশসমূহের মতো আর্থিক বৈষম্য দেখা গেল ভারতের অর্থনীতিতে।
এ প্রসঙ্গে একটি কথা বলা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না, যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও ব্যক্তিগত বিনিয়োগের অধিকার থাকা সত্বেও স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতে ‘BIG PUSH নীতির প্রয়োগ করে দেশের হাল ফেরানোর জন্য প্রচুর বিনিয়োগ করার মত ক্ষমতা ভারত সরকারের ছিল, কিভাবে, দেখা যাক। ভারত যখন স্বাধীন হয় তখন ভারতে ৫৬৩টি দেশীয় রাজ্য ছিল, ভারত সরকার শর্ত দিয়েছিল যদি কোনও দেশীয় রাজ্য স্বেচ্ছায় ভারতে যোগ দেয় তাহলে সেই দেশীয় রাজ্যের রাজারা নিজেদের সম্পত্তি নিজেদের দখলে রাখতে পারবে, কিন্তু যদি কোনও রাজ্য স্বেচ্ছায় ভারতে যোগ না দেয় তাহলে সেই রাজ্যের রাজার সম্পত্তি ভারত সরকার ক্রোক করে নিতে পারবে। অন্য রাজ্যগুলি কেউ আগে কেউ পরে স্বেচ্ছায় ভারতে যোগ দিয়েছিল। কিন্তু নিজাম স্বেচ্ছায় ভারতে যোগ দেয়নি তাকে ভারতে যোগ দেওয়ানোর জন্য ভারত সরকারকে সেনা পাঠাতে হয়েছিল। এই নিজাম ছিল তৎকালীন বিশ্বের ধনীতম ব্যক্তি, সেসময় তার সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ২০০০ কোটি টাকা তখন ভারতের জাতীয় বাজেট পেশ হতো ৩৬৩ কোটি টাকার। যেহেতু নিজাম স্বেচ্ছায় ভারতে যোগ দেয়নি তাই শর্ত অনুযায়ী ভারত সরকার তার সম্পত্তি ক্রোক করতে পারতো। সেই বিপুল পরিমাণ সম্পদ যা তৎকালীন ভারতের ছ’বছরের বাজেটের সমান তা দিয়ে ভারত সরকার সহজেই দেশে বিপুল পরিকাঠামোগত উন্নতি অর্থাৎ (BIG PUSH) করে দেশের উন্নতি করতে পারতো।
এতো গেল দেশের অর্থনীতির শিল্প নির্ভর অংশের কথা, দেশের কৃষিব্যবস্থাতে এসময় মঞ্চস্থ হচ্ছিল ভূমিসংস্কার নামক নাটক, ভূমি সংস্কারের নামে বড় জোতের মালিকদের অলাভজনক জমির ক্ষতিপূরণ পাইয়ে দিয়ে বিনিময়ে নিজেদের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করার এবং ভূমিহীন কৃষকদের সামান্য জমি পাইয়ে দেওয়ার নামে তাদের রাজনৈতিক আনুগত্য ক্রয় করে নিজেদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিল তৎকালীন শাসকবর্গ। তাতে সরকারের কৃষকবন্ধু হওয়ার। ঢক্কানিনাদ শ্রুত হয়েছিল উচ্চধ্বনিতে কিন্তু কৃষি বা কৃষকের প্রকৃত উপকার কিছুই হয়নি। কৃষিক্ষেত্রের প্রকৃত উপকারের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ, যেমন, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, কৃষকের জ্ঞান বৃদ্ধি প্রভৃতি কিছুই হয়নি সঠিকভাবে। তবে হ্যা, সেচব্যবস্থার উন্নতিকল্পে এসময় প্রচুর অর্থব্যয় হয়েছিল, দেশজুড়ে প্রচুর বড় বড় বাঁধ নির্মিত হয়েছিল, সাময়িকভাবে সেচব্যবস্থার উন্নতিও হয়েছিল, ফলস্বরূপ এসময়ে কৃষি উৎপাদনও বেড়ে ছিল লক্ষ্যণীয়ভাবে, কিন্তু এই নব প্রবর্তিত সেচব্যবস্থা দেশের পরিবেশ ও প্রকৃতির অনুরূপ ছিল না, ছিল পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ, তাই এই সেচব্যব্যবস্থা ভারতবর্ষের পরিবেশে স্থায়িত্ব লাভ করতে ব্যর্থ হয়েছিল, তাই কৃষির সাময়িক যে উৎপাদন বৃদ্ধি এসময় ঘটেছিল তা পরবর্তীকালে বিপরীত ফল প্রদান করেছিল।
আলোচ্য সময় আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা ছিল তুলনায় ভালো, ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মতো পশ্চিমবঙ্গ দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনৈতিক নেতাদের তখনও প্রত্যক্ষ করেনি। পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন শাসকবর্গের দক্ষতায় পশ্চিমবঙ্গ শিল্পে খুব দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিল, বাকি ভারতের শিল্পক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার যখন স্বাধীনতার পর প্রথম দু’দশকে ঘটেছিল মাত্র ৩ শতাংশ হারে তখন পশ্চিমবঙ্গের শিল্পক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার ছিল ৫ শতাংশের কিছু বেশী। শিল্পক্ষেত্রে এই বৃদ্ধি পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতে কিন্তু সেরকম কোনও সদর্থক প্রভাব ফেলেনি। এর কারণ অবশ্য অর্থনীতি-জগৎ -উদ্ভূত নয় বরং রাজনীতি জগতেই আছে এর উত্তর। স্বাধীনতা-আশীর্বাদের সঙ্গে সঙ্গে অভিশাপের মত আসা দেশভাগ পশ্চিমবঙ্গকেই আঘাত করেছিল সবচেয়ে বেশী। দেশভাগের ফলে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে বিতাড়িত ছিন্নমূল মানুষের ভীড় পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির চাহিদা-জোগান ভারসাম্যে আঘাত করেছিল। ১৯৪৭ সালের ১ কোটি ২০ লক্ষ জনসংখ্যার পশ্চিমবঙ্গে স্বাধীনতার পর প্রথম একদশকে উদ্বাস্তু এসেছিলেন প্রায় ৮০ লক্ষ, এই বাড়তি চাহিদা পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন শিল্পবৃদ্ধিজনিত সুফলকে শুষে নিয়েছিল ব্লটিং কাগজের মতো। তবে পাশাপাশি একথাও বলা যায় যে পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন শিল্পবৃদ্ধি হয়তো উদ্বাস্তু সমস্যায় দীর্ণ পশ্চিমবঙ্গকে অর্থনৈতিক ভরাডুবির হাত থেকে রক্ষা করেছিল। অর্থনৈতিক উন্নতি না ঘটলেও দেশভাগের আঘাতকে সামলে পশ্চিমবঙ্গ নিজ অবস্থানে অটুট থাকতে পেরেছিল তৎকালীন শিল্পবৃদ্ধির জন্যই।
পশ্চিমবঙ্গ শিল্পক্ষেত্রে দেশভাগজনিত আঘাতকে সামলে উঠতে পারলেও কৃষিক্ষেত্রে পারেনি। দেশভাগজনিত কারণে স্বল্প জমি, উদ্বাস্তুজনিত কারণে প্রচুর জনসংখ্যা ফলস্বরূপ মাত্রাতিরক্ত জনঘনত্ব অর্থাৎ বাড়তি চাহিদা এবং কম জোগান, এই জোড়া ফলার আক্রমণ • সামলাতে পারেনি তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের কৃষিক্ষেত্র। তাই অনাদিকাল থেকে সুজলা সুফলা এই প্রদেশে তখন দেখা গেছিল খাদ্য ঘাটতি। এই খাদ্য ঘাটতি শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিকে প্রভাবিত করেনি, অর্থনীতির সীমানা ছাড়িয়ে এই খাদ্যাভাবের যুগান্তকারী প্রভাব পড়েছিল তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্য, চলচ্চিত্র এমনকি রাজনীতিতেও।
এভাবেই কাটলো প্রথম দু’দশক। ইতিমধ্যে হাকিম বদলালো। দু’এক হাত ঘুরে প্রধানমন্ত্রী হলেন নেহরুতনয়া ইন্দিরা। হাকিম বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে হুকুমও কিছুটা বদলালো। এবার শুরু হল ব্যক্তিগত বিনিয়োগে চলা সংস্থাগুলির রাষ্ট্রায়ত্বকরণ। বিপুল অর্থ ক্ষতিপূরণ পেয়ে নিজেদের পুঁকতে থাকা সংস্থাগুলিকে রাষ্ট্রের হাতে অর্পণ করে স্বস্তির শ্বাস ফেলল মালিকপক্ষ, জনগণের করের টাকার অপচয় করে সেই সব ডুবন্ত সংস্থাগুলির রাষ্ট্রায়ত্বকরণ করে তৎকালীন শাসকদল ভোট-বৈতরণী পেরলো আর অর্থনীতির ক্ষেত্রে সৃষ্টি হল এক নতুন শ্রেণীর, ট্রেড ইউনিয়ন লিডার নামক সেই নতুন শ্ৰেণী রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থার কর্মীসমূহের ওপর ছড়ি ঘোরানোর পরিস্থিতিপ্রদত্ত অধিকারের অসদ্ব্যবহার করে ঢুকে পড়লো দুর্নীতির বৃত্তে। দু’দশক ধরে জাতীয় অর্থনীতিতে অবস্থিত রাজনীতিবিদ- আমলা- ব্যবসায়ী, দুষ্ট -এয়ী বদলে রাজনীতিবিদ – আমলাব্যবসায়ী-ট্রেড ইউনিয়ন লিডার এই দুষ্ট-চতুষ্টয়ে পরিণত হল। একমাত্র ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র বাদ দিয়ে অন্য কোনো ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্বকরণ সুফল প্রদানকারী হয় নি।
এই কালখণ্ডে দেশের কৃষিক্ষেত্র সাক্ষী ছিল সবুজ বিপ্লবের। রাসায়নিক সার, কৃত্রিম বীজ প্রভৃতির সাহায্যে কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি হল ভালোই, হয়তো সাময়িকভাবে তা অর্থনীতির পালে কিছুটা হাওয়াও দিল, কিন্তু কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে গৃহীত এই পদক্ষেপ ছিল না পরিবেশবান্ধব, তাই কিছু বছর পর থেকেই এর বিষময় ফল প্রত্যক্ষ করলো গোটা দেশ, সে কথা পরবর্তীতে আলোচ্য।
পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে এই সময়টি ছিল অত্যন্ত ভয়ংকর, সারা দেশের মতো এই সময় পশ্চিমবঙ্গেও হাকিম বদলানোর পালা চলছিল, তবে পশ্চিমবঙ্গে হাকিম এবং হুকুম দুইই বদলাচ্ছিল অত্যন্ত দ্রুতগতিতে এবং ঘন ঘন। বলা চলে নতুন নতুন হাকিম আর হুকুমের পরীক্ষাগার হয়ে উঠেছিল পশ্চিমবঙ্গ। এই ঘন ঘন পরিবর্তনের সুযোগে উপরোক্ত দুষ্ট চতুষ্টয় প্রভাব বিস্তার করেছিল সবচেয়ে বেশী। স্বাধীনতার পর প্রথম দু’দশক দুর্নীতি দৈত্যের উপদ্রব গোটা দেশের চেয়ে পশ্চিমবঙ্গে অনেক কম থাকলেও তার পরবর্তী কালখণ্ডে তার উপদ্রব গোটা দেশের চেয়ে পশ্চিমবঙ্গে ছিল অনেক বেশী। ক্ষুদ্র দলগত স্বার্থ ও ব্যক্তিগত স্বার্থ তখন রাজ্যের স্বার্থের তুলনায় বেশী গুরুত্ব পাচ্ছিল। এই কালখণ্ডেই পশ্চিমবঙ্গ ধীরে ধীরে সুশিক্ষিত, মেধাবী, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রীর অধিকারী ও সৎ নেতাদের বদলে অর্ধশিক্ষিত, মস্তান পরিবৃত ও অসৎ নেতাদের ক্ষমতার অলিন্দে আনাগোনা প্রত্যক্ষ করলো। স্বাধীনতার পরের প্রথম দু’দশকের খাদ্য ঘাটতি জনিত জনক্ষোভ হয়তো এই “পালাবদলের পালা” রূপায়ণে কিছুটা হলেও নেতিবাচক ভূমিকা নিয়েছিল। অধিক উৎপাদন (যা জোগান বাড়িয়ে বাজারে সংশ্লিষ্ট জিনিসের দাম কমিয়ে মালিকের মুনাফা কমায়) রোধে মালিকের সঙ্গে গোপন বোঝাপড়ায় ধর্মঘট ডাকতে শুরু করলো শ্রমিক নেতারা। কোথাও কোথাও এই ধর্মঘট মালিকের গণেশ উল্টোনোর কাজে সহায়ক হবার জন্য দীর্ঘস্থায়ী হতে হতে চিরস্থায়ী হয়ে গেল। পশ্চিমবঙ্গ ধীরে ধীরে ক্ষয়িষ্ণু শিল্প ও বর্ধিষ্ণু শিল্পপতি এবং ক্ষয়িষ্ণু শ্রমিক ও বর্ধিষ্ণু শ্রমিক নেতার সংগ্রহশালায় পরিণত হল। শিল্পের সঙ্গে শিল্পপতির এবং শ্রমিকের সঙ্গে শ্রমিক নেতার এই ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিকে ঠেলে দিল পঙ্গুত্বের দিকে। এভাবেই কেটে গেল একটি দশক। বঙ্গ রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে “পালাবদলের পালা” সম্পূর্ণ হল এবং পোহালে শর্বরী দেখা গেল রাজদণ্ড পাকাপাকি ভাবে হস্তগত করেছে দুষ্ট-চতুষ্টয় এবং দুষ্ট-চতুষ্টয় শুধুমাত্র সিংহাসনের চারটি পায়া হয়েই সন্তুষ্ট থাকে নি বরং সিংহাসনে উঠে বসেছিল। এরপর হাকিম আর হুকুম কোনওটিই বদলায়নি দীর্ঘদিন। অর্থনৈতিক পঙ্গুত্ব স্থায়িত্ব লাভ করেছে। পরবর্তীকালে হাকিম চরিত্রের কুশীলব পরিবর্তন ঘটেছে কিন্তু চিত্রনাট্য একই থেকে গেছে। পশ্চিমবঙ্গ অর্থনৈতিক পঙ্গুত্বের হাত থেকে রক্ষা পায়নি।
শিল্পক্ষেত্রের তো ছিল এই হাল আর ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গের কৃষিক্ষেত্রে ঘটে চলেছে এক নতুন নাটক। এক্ষেত্রেও সৎ রাজনীতির বিপ্রতীপ রূপ হিসেবে চূড়ান্ত অসৎ রাজনীতির প্রয়োগ দেখা গেল। ভূমিসংস্কারকে কেন্দ্র করে স্বাধীনতার পরের দু’দশকে গোটা দেশে যে নাটক পরিলক্ষিত হয়েছিল (অত্যন্ত সৌভাগ্যজনকভাবে যা সেসময় পশ্চিমবঙ্গে পরিলক্ষিত হয়নি), তা সময় সারণীর এই পর্বে পশ্চিমবঙ্গে দৃশ্যমান হল এবং অত্যন্ত অধিক পরিমাণে। অধিক জনঘনত্বের কারণে এমনিতেই মাথাপিছু খুব কম জমির রাজ্যে বারংবার জমির খণ্ডীকরণ ভাগচাষীকে জমির কাগুজে অধিকার হয়তো পাইয়ে দিল, কিন্তু অত ছোট জমিতে চাষ করে গ্রাসাচ্ছাদন করা হল অসম্ভব। জমির উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর জন্য আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারও অত ছোট জমিতে সম্ভব হল না। শাসকশ্রেণীর ভোটব্যাঙ্ক মজবুত করা ছাড়া এই ভূমিসংস্কার আর কোনও কাজে লাগলো না।
জাতীয় অর্থনীতির এই গড্ডালিকা-প্রবাহ ধাক্কা খেল ১৯৯১ সালে, সোভিয়েত-পতনের সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েত-নির্ভর সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির পূতিগন্ধময় অস্তিত্ব বিলুপ্ত হল গোটা দুনিয়া থেকে। ফুটো নৌকো থেকে রক্ষা পাবার তাগিদে ভারতীয় নেতৃত্বের নিদ্রাভঙ্গ হল। কিন্তু হা হতোশ্মি। কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হল কিন্তু সে উঠে বসল না বরং বাঁ দিক থেকে ডান দিকে ঘুরে আবার ঘুমিয়ে পড়লো। ধ্বংসপ্রাপ্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন-এর বদলে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রকে এবার আদর্শ করলো জাতীয় নীতিনির্ধারকরা। অবশ্য মিশ্র অর্থনীতির মিশ্র ভাবটি অটুট রইলো শুধু সমাজতান্ত্রিক ঝোঁক ধনতান্ত্রিক ঝেকে বদলে গেল। অর্থাৎ এখনও সরকারি-বেসরকারি উভয় সংস্থাই অর্থনীতিতে থাকলো কিন্তু এখন তাদের মধ্যে থাকলো প্রতিযোগিতা। বিনিয়োগের এবং বিপণনের ক্ষেত্র নিয়ন্ত্রণামুক্ত হল, লাইসেন্স রাজ ঠাই পেল ইতিহাসের পাতায়। তা বলে দুর্নীতি দূর হল না, দুষ্ট-চতুষ্টয়ের প্রাধান্য অটুট রইলো শুধু দুর্নীতির পদ্ধতি বদল হল, কারণ এরপর দেখা গেল উলটপুরাণ, বেসরকারি সংস্থার রাষ্ট্রায়ত্বকরণের বদলে এবার শুরু হল রাষ্ট্রায়াত্ত সংস্থার বিলগ্নিকরণ, লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাকে অলাভজনক দেখিয়ে স্বল্পমূল্যে বিক্রি করে দেওয়ার নয়া দুর্নীতি চালু হল। আমলাতন্ত্র লাইসেন্স রাজের বদলে হিসেবে কারচুপিকে দুর্নীতির নতুন হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করলো। সংস্থার বিলগ্নিকরণ রোধ করার নামে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সাজানো লড়াই করে পরে উপযুক্ত রজতচক্রের বিনিময়ে বিলগ্নিকরণ মেনে নেওয়ার মাধ্যমে নিজের দুর্নীতিক্ষেত্র বজায় রাখলো ট্রেড ইউনিয়ন লিডাররাও, তবে হ্যা, বাজারে প্রতিযোগিতা থাকায় শিল্প ও পরিষেবাক্ষেত্রের গুণগত মানের উৎকর্ষ সাধিত হল। উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশও ঘটলো। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ না থাকায় নতুন বিনিয়োগকারীদের উঠে আসার পথও প্রশস্ত হল কিন্তু উপযুক্ত পরিকাঠামো তৈরী না থাকায় ও সরল করবিধি না থাকায় নতুন বিনিয়োগকারীরা উঠে আসতে ব্যর্থ হল। দেশের মাথাপিছু গড় আয়ের (জি ডি পি) বৃদ্ধির হার সামান্য বৃদ্ধি পেলেও অর্থাৎ জাতীয় অর্থনীতির সামান্য শ্রীবৃদ্ধি ঘটলেও সেই সুফল পুরোটাই চলে গেল দুষ্ট-চতুষ্টয়ের অজগর গ্রাসে, সাধারণ মানুষ রইল বঞ্চিতই।
এই সময় থেকে পরিষেবা নামক অর্থনীতির আর একটি ক্ষেত্র ভারতীয় অর্থনীতিতে প্রভাবশালী হয়ে উঠলো। ব্যাঙ্ক, পরিবহন, তথ্যপ্রযুক্তি প্রভৃতি নিয়ে গড়ে ওঠা এই ক্ষেত্র ভারতীয় অর্থনীতিতে পঞ্চাশ শতাংশের বেশী অবদান রাখতে শুরু করলো।
এসময় থেকে ভারতীয় অর্থনীতি দুটি নতুন ধরনের দুর্নীতির সম্মুখীন হল, একটি হল ব্যাঙ্কের স্বেচ্ছা-ঋণখেলাপীকৃত দুর্নীতি অন্যটি প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠন।
ব্যাঙ্কের স্বেচ্ছা-ঋণখেলাপীকৃত দুর্নীতি কি এবং অর্থনীতিতে তার প্রভাব কতখানি ভয়ঙ্কর তা জানতে হলে আমাদের জানতে হবে ব্যাঙ্ক কি? এবং অর্থনীতিতে তার গুরুত্ব কতটা।
কোনও জীবদেহের মধ্যে প্রাণের সার্থক বিকাশ সাধনের জন্য যেমন সেই দেহকাঠামোর সর্বাঙ্গে প্রাণরস প্রয়োজন, তেমনিই কোনও অর্থনীতির বিকাশসাধনের জন্য সেই রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে অর্থের সামগ্রিক সঞ্চালন প্রয়োজন। অর্থ হল বিনিময়ের মাধ্যম বা ক্রয়ক্ষমতার মাপকাঠি অর্থাৎ প্রাণীদেহের অন্তর্গত অসংখ্য কোষসমূহের ন্যায়। রাষ্ট্রকাঠামোর অন্তর্গত অসংখ্য মানুষের প্রত্যেকে তার কর্মের ফল হিসেবে যে ক্রয়ক্ষমতার অধিকারী হয় তা অর্থের মাধ্যমে লাভ করে। এই লভ্য অর্থ দু’ভাবে ব্যয়িত হতে পারে। এক ভোগ্য বস্তু ক্রয়ের মাধ্যমে, দুই বিনিয়োগের মাধ্যমে। এই দুই পদ্ধতিতে ব্যয়ের পরেও কোনও ব্যক্তি উদ্বৃত্ত অর্থ বা ক্রয়ক্ষমতার অধিকারী থাকতে পারে আবার কোনও ব্যক্তির প্রাপ্য অর্থের অতিরিক্ত অর্থের দরকার হতে পারে উপরোক্ত দুই পদ্ধতিতে ব্যয়ের কারণে। এরকম ক্ষেত্রে এই দুই ব্যক্তি অর্থাৎ রাষ্ট্রদেহের দুই পৃথক জীবকোষ পরস্পরের পরিপূরক হয়ে যায় এবং এদের পরস্পর বিপরীতমুখী প্রয়োজনকে পরস্পরের প্রয়োজন নিবারক হতে সাহায্য করে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা, এই ব্যবস্থা একদিকে উদ্বৃত্ত অর্থ বা ক্রয়ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিকে দেয় সঞ্চয়ের সুযোগ ভবিষ্যতের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে, অন্যদিকে অধিক অর্থ বা ক্রয়ক্ষমতা আকাঙ্খী ব্যক্তিকে তার প্রয়োজনীয় অর্থ বা ক্রয়ক্ষমতা প্রদান করে ভবিষ্যতে নিজের অর্জিত অর্থ বা ক্রয়ক্ষমতা থেকে তা পরিশোধ করার চুক্তির বিনিময়ে। এভাবেই উদ্বৃত্ত অর্থের জোগান ও প্রয়োজনীয় অর্থের চাহিদার মধ্যে সমন্বয় সাধন করে অর্থনীতির অগ্রগতির পথ প্রশস্ত করে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা। ধরা যাক কোনও একজন ব্যক্তি রামবাবু তার কাজের জন্য মাসে ১০ হাজার টাকা পান, কিন্তু প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্যাদি কিনতে তার মাসে আটহাজার টাকা লাগে, বাকি দু’হাজার টাকা তিনি সঞ্চয় করেন ভবিষ্যতের জন্য। আবার শ্যামবাবু তারও আয়-ব্যয় রামবাবুর মতোই কিন্তু তার মনে এক বিশেষ পরিকল্পনা আছে, যে পরিকল্পনা ভবিষ্যতে অধিক উপার্জনের দরজা খুলে দেবে, কিন্তু তার জন্য প্রয়োজনীয় বস্তু ও শ্রম ক্রয় করতে বর্তমানে তার পাঁচ লক্ষ টাকা প্রয়োজন যা তাঁর কাছে বর্তমানে নেই। এখানেই ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার ভূমিকা। সে রামবাবু এবং তার মতো আরও আড়াইশ লোকের সঞ্চয় একত্রিত করে শ্যামবাবুকে দেয় বিনিয়োগ করার জন্য। এর ফলে রামবাবু পান তার সঞ্চয়ের অধিক মূল্য এবং নিরাপত্তা এবং শ্যামবাবু পান তার পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার রসদ আর সামগ্রিক অর্থনীতি পায় বৃদ্ধির পথে চলার শক্তি। সেজন্য পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন সময়ে গড়ে ওঠা সমস্ত মানবসভ্যতাতেই ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার অস্তিত্ব দেখা যায়। আর যদি কোনও দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার বিপর্যয় দেখা দেয় তাহলে সেই দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিই বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। যেমন দেখা গেছিল ২০০৮ খ্রীস্টাব্দে আমেরিকায়।
দুর্ভাগ্যবশতঃ বিশ্বায়ন উত্তর ভারতীয় অর্থনীতিতে এই বিপদের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে তীব্রভাবে। তা শোনা যাচ্ছে ঋণগ্রহীতারা অর্থাৎ শ্যামবাবুরা ঋণ ফেরৎ না দেওয়ার কারণে। ঋণগ্রহীতারা ঋণ নিয়ে নিয়মিতভাবে ফেরৎ না দিলে ব্যাঙ্কের চাহিদা জোগানের স্বাভাবিক নিয়মে কিছুদিন পরে ব্যাঙ্ক আমানতকারীদের প্রাপ্য অর্থ ফেরত দিতে কিয়দংশে ব্যর্থ হবে। কিয়দংশে ব্যর্থ হলেই সকল আমানতকারীর মনে দেখা দেবে আশংকা। একসঙ্গে সকলে টাকা তুলে নিতে চাইবে, মেয়াদী ঋণে গচ্ছিত অর্থ ব্যস্ত থাকায় সেই টাকা ফেরত দিতেও ব্যর্থ হবে ব্যাঙ্ক অর্থাৎ ব্যাঙ্ক-ফেল হবে। অর্থনৈতিক সেই তীব্র অবিশ্বাসের পরিবেশে নতুন গ্রাহকরাও সঞ্চয়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যাঙ্ককে বেছে নেবে না। মৃত্যু হবে সমস্ত ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার। টাকা ফেরৎ না দেওয়া অসৎ শ্যামবাবুরা হবেন বিরাট ধনী আর বিনিয়োগকারী পরিকল্পনাকারী সৎ ভবিষ্যতের অসংখ্য শ্যামবাবু হবেন ঋণবঞ্চিত। সঞ্চিত অর্থ ফেরৎ না পেয়ে এযুগের রামবাবুরা হবেন সর্বস্বান্ত আর ভবিষ্যতের সমস্ত রামবাবু হবেন সঞ্চয়ের সুবিধা বঞ্চিত। ব্যাঙ্ক-ফেল হবার এই দুর্দশার উদাহরণ দেখা যায় গিরিশচন্দ্র ঘোষের “প্রফুল্ল” নাটকে এবং সত্যজিতের রায়ের “মহানগর” ছবিতে। এহেন বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেতে বা এই ধরণের বিপদের পরিস্থিতি যাতে সৃষ্টি না হয়। সেজন্য সাধারণত ঋণগ্রহীতারা ঋণ ফেরৎ না দিলে ব্যাঙ্ক ঋণগ্রহীতার সম্পত্তি ক্রোক করে সেই অর্থ আদায় করে। কিন্তু এক্ষেত্রে কোম্পানি আইনের সুবিধা নিয়ে কোম্পানি মালিকরা কোম্পানির নামে ঋণ নিয়ে সেই ঋণের অর্থ সাইফন করে নিজ নামে করে করে নেয় ঘুরপথে, অতঃপর হিসেবের কারচুপির দ্বারা কোম্পানিকে দেউলিয়া দেখিয়ে কোম্পানির নামে নেওয়া ঋণ প্রত্যার্পণে কোম্পানিকে অক্ষম প্রতিপন্ন করে। দেউলিয়া কোম্পানির ক্রোক করার মত তেমন কোনও সম্পত্তিও থাকে না, কিন্তু কোম্পানি মালিকের সম্পত্তি দিনের পর দিন বেড়েই চলে। এককথায় বলা যায় কোম্পানি আইনের সুবিধা নিয়ে ক্ষয়িষ্ণু শিল্পের বর্ধিষ্ণু শিল্পপতিরা এখন দেউলিয়া শিল্পের অবুদপতি শিল্পপতিতে পরিণত হচ্ছে। এই অনাদায়ী ঋণের সমস্যা গত দু-দশক ধরেই ক্রমবর্ধমান, কিন্তু এতদিন হিসেবের খাতায় এই অনুৎপাদক সম্পদকে না দেখিয়ে চোখ বন্ধ করে প্রলয়কে ঠেকানোর চেষ্টা হয়েছিল। গত তিনবছরে এই অনুৎপাদক সম্পদকে হিসেবের খাতায় দেখানো হচ্ছে ফলে বিপদের হিমশৈলকে গোড়া থেকে চূড়া পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। দেশের অর্থনৈতিক মহল আঁতকে উঠছে।
এই সময়ের দ্বিতীয় বিপদ হল দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠন। প্রাকৃতিক সম্পদের দিক দিয়ে ভারতবর্ষ বরাবরই প্রকৃতি দেবীর আশীর্বাদধন্য, শুধুমাত্র উর্বর কৃষিভূমি নয়, বনজ সম্পদ এবং খনিজ সম্পদের দিক দিয়েও ভারত পৃথিবীর অন্য অনেক দেশের তুলনায় সম্পন্নতর। ১৯৯১ সালের আগে অর্থাৎ ভারত বিশ্বায়নে সামিল হওয়ার আগে পর্যন্ত এই প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের অধিকার শুধুমাত্র সরকারের ছিল। সরকার সেই সম্পদের সঠিক ব্যবহার করতে পারেনি তাই সেই সম্পদ অব্যবহৃত ছিল কিন্তু ১৯৯১ সালের অর্থাৎ ভারত বিশ্বায়নে সামিল হওয়ার পর থেকে উপযুক্ত অনুমতির বিনিময়ে সেই প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের অধিকার পেয়ে গেল বেসরকারি সংস্থাগুলিও। মুদ্রারাক্ষসের বদিত মুখগহ্বরে আত্মসমর্পিত দুষ্ট-চতুষ্টয় উপযুক্ত অনুমতি বিতরণে কার্পণ্য করলো না। বিদেশী বহুজাতিকের হাতে পড়ে এতদিনের অব্যবহৃত প্রাকৃতিক সম্পদ এখন অপব্যবহৃত হতে থাকলো। এরকম একটি লুণ্ঠনের ঘটনা গোচরে এসেছিল ২০১৩ সালে, কয়লা খনিগুলির বিতরণজনিত ১০ লক্ষ কোটি টাকারও বেশী সেই কোলগেট দুর্নীতি সেসময় সত্যিই দেশবাসীর হৃৎকম্প ঘটিয়েছিল। ২০১৪-র পর কোলগেট দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ হলেও, দুর্নীতির এই নবোদ্ভাবিত সরণী জাগ্রত জনসমাজের নিরবচ্ছিন্ন নজরদারির দাবি রাখে।
এসময় থেকে দেশের কৃষিব্যবস্থা অন্য ধরনের বিপদের সম্মুখীন হয়েছে। আগেই বলা হয়েছে, স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে নির্মিত বড় বাঁধগুলি দেশের পরিবেশ ও প্রকৃতির অনুরূপ ছিল না। ছিল পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ। তাই এই সেচব্যবস্থা ভারতবর্ষের পরিবেশে স্থায়িত্ব লাভ করতে ব্যর্থ হয়েছিল। পলি পরে বাঁধগুলি কিছুদিন পরেই ভর্তি হয়ে গিয়েছিল তখন এগুলি কর্মক্ষমতা হারায়। সেগুলি শুখা মরসুমে সেচে সাহায্য তো করেই না বরং বর্ষার মরসুমে বন্যা ঘটাতে তারা অনেক পটু। আবার পূর্বে উল্লিখিত সবুজ বিপ্লবের ফলে গৃহীত কৃষিব্যবস্থায় প্রচুর জলের প্রয়োজন হয়, ফলে কৃষককে বাধ্য হয়ে অধিক ব্যয় করে পাম্প চালিয়ে সেচের ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। আবার অন্যদিকে সবুজ বিপ্লবের ফলে গৃহীত কৃষিব্যবস্থায় ব্যবহৃত রাসায়নিক সার ও কীটনাশক পরিবেশ বান্ধব না হওয়ায় তা দেশের বাস্তুতন্ত্রে ও উৎপাদিত শস্য ব্যবহারকারীর স্বাস্থ্যের ওপর আঘাত করলো এবং এই সার ও কীটনাশকের জন্য কৃষক সম্পূর্ণভাবে বাজারের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ল। এই সুযোগে সার ও কীটনাশক উৎপাদক কোম্পানিগুলি (যার মধ্যে বেশীরভাগই বিদেশী) নিজেদের ইচ্ছেমতো সার ও কীটনাশকের দাম বাড়াতে লাগলো। একদিকে সেচের বর্ধিত খরচ অন্যদিকে দামী সার ও কীটনাশক, অসহায় চাষী আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হল। এতদিন জৈব কৃষি ব্যবস্থায় কৃষিকার্যের জন্য প্রয়োজনীয় জৈব সার ও কীটনাশক কৃষক নিজেই তৈরি করে নিত, ফলে তাকে বাজারের ওপর নির্ভর করতে হত না অর্থাৎ সার ও কীটনাশক কোম্পানির মালিকের দয়ায় জীবন যাপন করতে হত না এবং জৈব কৃষি পরিবেশবান্ধব হওয়ায় তা কৃষিব্যবস্থার কোনও স্থায়ী ক্ষতিও করতো না। জৈব কৃষি উৎপাদনশীলতার দিক দিয়েও রাসায়নিক পদ্ধতির কৃষিব্যবস্থার চেয়ে পেছিয়ে নেই। ব্রিটিশ আমলের শেষার্ধে ভারতের কৃষি উৎপাদন হ্রাস পেয়েছিল। রাসায়নিক সার ও কীটনাশক কোম্পানিগুলির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তখন সকলে ভেবেছিল যে জৈব কৃষিব্যবস্থাই এই স্বল্প উৎপাদনশীলতার জন্য দায়ী এবং সকলেই রাসায়নিক কৃষিব্যবস্থায় আস্থাশীল হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ আমলে জল চলাচলের নালা না রেখে তৈরী করা অপরিকল্পিত রেলপথ আমাদের দেশের প্রাকৃতিক সেচব্যবস্থাকে নষ্ট করে ফেলেছিল ফলস্বরূপ কৃষি উৎপাদন হ্রাস পেয়েছিল, এর জন্য জৈব কৃষিব্যবস্থা দায়ী নয়, বরং রেলপথ স্থাপনের আগে ভারতে জৈব কৃষিব্যবস্থায় যে উৎপাদনশীলতা ছিল (যার তথ্য সেসময়কার ব্রিটিশ গেজেটে পাওয়া যায়) তা বর্তমান রাসায়নিক কৃষি ব্যবস্থার উৎপাদনশীলতার চেয়ে কম নয়।
এই সমস্যার হাত থেকে রেহাই পেতে তাই কৃষক সমাজের উচিত পুনরায় জৈব কৃষিব্যবস্থায় ফিরে যাওয়া। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, শরীরের ওপর রাসায়নিক কৃষিব্যবস্থায় উৎপন্ন খাদ্যের ক্ষতিকর প্রভাবের ব্যাপারে অবহিত হয়ে এখন ক্রেতারা অনেকেই জৈব কৃষিব্যবস্থায় উৎপন্ন খাদ্যের খোঁজ করছেন, এখন কৃতকসমাজ সম্পূর্ণরূপে জৈব কৃষিব্যবস্থায় ফিরে এলে সকলেরই মঙ্গল।
ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির কিছু সুফল যেমন ভারতীয় অর্থনীতি পেল সেরকমই ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির এক অভিশাপও ভারতীয় অর্থনীতির শিরঃপীড়ার কারণ হল। ১৯৯১ সালের আগে অর্থাৎ ভারত বিশ্বায়নে সামিল হওয়ার আগে পর্যন্ত ভারতের বাজারে বিদেশী কোম্পানির প্রবেশ নিয়ন্ত্রিত ছিল, পণ্য বা পরিষেবার বাজারে ক্রেতার বাছাই করার কোনও সুযোগ ছিল না, ১৯৯১ সালের আগে অর্থাৎ ভারত বিশ্বায়নে সামিল হওয়ার আগে পর্যন্ত ভারতের বাজারে বিদেশী কোম্পানির প্রবেশ নিয়ন্ত্রিত ছিল, পণ্য বা পরিষেবার বাজারে ক্রেতার বা
ছাই করার কোনও সুযোগ ছিল না, ১৯৯১ সালের পরে বিশ্বায়িত বাজারে ক্রেতার হাতে এল বাছাই করার অধিকার। এতদিনের অনভ্যস্ত ভারতীয় ক্রেতারা এই বাছাই করার ব্যাপারে ভুল করতে শুরু করলো, বিজ্ঞাপনী চটক এবং বিদেশী বহুজাতিকের আরও নানা বিপণন কৌশলে ধরাশায়ী হল তারা। বিদেশী বহুজাতিকগুলির নামীদামী ব্র্যান্ডের প্রতি অন্ধ আকর্ষণ এই পতনের ব্যাপারে সহায়ক হল, হয়তো স্বামীজী কথিত দাসসুলভ দুর্বলতা এই অন্ধ আকর্ষণের পেছনেও কাজ করেছিল। অপ্রয়োজনীয় এবং শরীর ও পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকর নানান বিদেশী দ্রব্যে ভরে যেতে শুরু করলো দেশের বাজার এবং দেশবাসীর গৃহ। শুহু হল পুনরায় দেশ থেকে সম্পদের বহির্গমন। প্রথম আঘাত এল পাশ্চাত্যের দিক থেকে, দেশে উৎপাদিত আলু ১০ টাকা কিলো দরে পাশ্চাত্যের কোম্পানিকে বিক্রি করে সেই আলুই ভাজা হিসেবে পটাটো চিপস নামে ১০০ টাকা কিলো দরে তাদের থেকেই দেশবাসী কিনতে শুরু করলো শুধুমাত্র প্যাকেজিংয়ের মোহে পড়ে। ঠাণ্ডা পানীয় কোম্পানীদ্বয় কেবল ব্র্যান্ড নেম সম্বল করে দখল করলো দেশবাসীর ভোগব্যয়ের সিংহভাগ। তাদের হিসেবের খাতায় লাভের অঙ্কে শূন্যের সংখ্যা বাড়তে থাকলো দেশবাসীর অসচেতনতার সুযোগ নিয়ে।
এব্যাপারে দেশবাসীকে সচেতন হতে হবে। বিশ্বায়ণ পছন্দের যে অধিকার এনে দিয়েছে তা দায়িত্ব সহকারে পালন করতে হবে। কিসে নিজের এবং দেশের ভালো হয় তা ভাবতে হবে। দুধ, দই আর ডাবের জলের দেশে কোক-পেপসির বিজয়রথের গতি যেন অপ্রতিরোধ্য না হয় তা দেখতে হবে দেশবাসীকেই।
শুধু পাশ্চাত্য নয়, বিদেশী বস্তুর বিপদ আসছে অন্য দেশ থেকেও। শুধুমাত্র ব্যান্ডনেমশোভিত, প্যাকেজিংখচিত, বিজ্ঞাপনপোষিত, মহার্ঘ বিদেশী বস্তুর দ্বারা নয়, দেশের বাজার আজ আক্রান্ত হচ্ছে ব্যান্ডনেমহীন, মোড়কহীন, বিজ্ঞাপনহীন, সস্তার। বিদেশী বস্তুর দ্বারাও আর দেশের বাজারে এই আক্রমণ আসছে চীনের দিক থেকে।
কোনও মানুষের শান্তিশৃঙ্খলা যেমন অনেকাংশে নির্ভর করে তার প্রতিবেশীর আচরণের ওপর সেরকমই কোনও দেশের শান্তিশৃঙ্খলা অনেকাংশে নির্ভর করে তার প্রতিবেশী দেশের আচরণের ওপর। প্রতিবেশী দেশ যদি আগ্রাসী মানসিকতার হয় তাহলে সংশ্লিষ্ট দেশকে খুব দুশ্চিন্তার মধ্যে কাটাতে হয়, বর্তমানে ভারতের ঠিক সেই অবস্থা হয়েছে, ভারতের বৃহত্তম প্রতিবেশী দেশ চিন তার আগ্রাসী মনোভাবের দ্বারা ভারতকে ক্রমাগত বিপদে ফেলে চলেছে। চিন ভারতের ওপর এই আগ্রাসন নানাবিধ পদ্ধতিতে চালাচ্ছে। তার মধ্যে অন্যতম হল অর্থনৈতিক আগ্রাসন। আর এই অর্থনৈতিক আগ্রাসন চালাচ্ছে সস্তা পণ্যের জোয়ারে ভারতের বাজারকে ভাসিয়ে দিয়ে। গত অর্থবর্ষে চীনের সঙ্গে আমাদের মোট বাণিজ্যের পরিমাণ প্রায় ৭০• ৮ বিলিয়ন ডলার বা পাঁচ লক্ষ তেইশ হাজার নশ কুড়ি কোটি টাকা। এর মধ্যে ৬১• ৮ বিলিয়ন ডলার বা ৪ লক্ষ ৫৭ হাজার। ৩২০ কোটি টাকা হল চীন থেকে ভারতে হওয়া আমদানি এবং মাত্র ৯ বিলিয়ন ডলার বা ৬৬ হাজার ৬০০ কোটি টাকা হল ভারত থেকে চীনে হওয়া রপ্তানি। অর্থাৎ বাণিজ্য ঘাটতি হল ৫২৯ বিলিয়ন ডলার বা ৩ লক্ষ ৯০ হাজার ৭২০ কোটি টাকা। চীনের থেকে ভারতের আমদানীর মধ্যে পেট্রোলিয়াম নেই, তবু এই বিপুল বাণিজ্য ঘাটতির কারণ চীনে নির্মিত সস্তা পণ্যের ভারতীয় বাজারে ব্যাপক বিক্রি হওয়া। সাধারণ ভারতীয় ক্রেতা সস্তার মোহে পড়ে ভারতীয় পণ্যের বদলে চিনা পণ্য কিনে ফেলেন। কোনও ব্যক্তি যখন সস্তার মমাহে পড়ে চিনা জিনিস কেনেন তখন তিনি দেশের ক্ষতি তো করেনই নিজেরও উপকার করেন না। চিনা জিনিষ সস্তার হলেও স্বল্পায়ু, অর্থাৎ কম দিন চলে, তাই কিছুদিন পরই সেই জিনিসটি আবার নতুন করে কিনতে হয় ফলে ক্রেতার খরচ বাড়ে। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক কোনও ব্যক্তি স্বদেশী কামারের তৈরী ছুরি ২০ টাকা দিয়ে না কিনে চিনা ছুরি কিনলো মাত্র ১০ টাকায়, ছুরিটি দেখতেও খুব সুন্দর ও চকচকে। কিন্তু ছুরিটি কিছুদিন পরেই অকেজো হয়ে গেল এবং ব্যবহার ও নিক্ষেপ (Use and throw) পদ্ধতির হওয়ায় সেটিতে পুনরায় ধার-ও দেওয়া গেল না। ক্রেতাকে পুনরায় আরেকটি ছুরি কিনতে হল, সেটি খারাপ হওয়ার পর পুনরায় আরেকটি। এভাবে তিনটি ছুরি কিনতে গিয়ে ক্রেতার ৩০ টাকা খরচ হল, এর বদলে ক্রেতা ২০ টাকা দিয়ে স্বদেশী কামারের কাছ থেকে ছুরি কিনলে তার এককালীন খরচ বেশি হলেও সামগ্রিক খরচ কম হত, কারণ ধার কমে গেলে ছুরিটি ফেলে দিতে হত না, নামমাত্র মূল্যে ধার দিয়ে নিলেই হত। আরেকটি উদাহরণ দেখা যাক, কোনও একজন ব্যক্তি স্বদেশী মাটির প্রদীপ বা স্বদেশে তৈরি ভারতীয় টুনি বাল্ব না কিনে কালীপূজোর সময় নিজের বাড়িকে আলোকিত করার জন্য চিনা লেড-বাল্ব কিনলেন, হয়তো তার এককালীন খরচ কম পড়লো কিন্তু দেখা গেল দু’একবছর পর সেই আলোগুলি খারাপ হয়ে গেল, তখন তাকে আবার নতুন করে আলো কিনতে হবে, অর্থাৎ আবার খরচ হবে, তার বদলে স্বদেশী মাটির প্রদীপ বা স্বদেশে তৈরি ভারতীয় টুনি বান্ধ কিনলে তা দীর্ঘদিন চলতো অর্থাৎ তার এককালীন খরচ বেশি হলেও সামগ্রিক খরচ কম হত, অতএব একথা বলা যেতে পারে যে, যে উদ্দেশ্যে ক্রেতারা চিনা জিনিস কিনতে আগ্রহী হচ্ছেন ক্রেতাদের সেই উদ্দেশ্য সাধিত হচ্ছে না। সেই উদ্দেশ্য তো সাধিত হল না কিন্তু ক্রেতারা নিজেদের অজান্তে আরও বড় এক বিপদের সম্মুখীন হলেন। চিনা জিনিসগুলি অধিকাংশই ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে তৈরী হয়, ক্রেতা চিনা জিনিস ব্যবহারকালে নিজের অজান্তেই স্বাস্থ্যহানির শিকার হচ্ছেন। অর্থাৎ সামান্য কিছু অর্থনৈতিক লাভের জন্য চিনা জিনিস কিনে সেই লাভ তো পাচ্ছেনই বরং কঠিন অসুখের এবং তজ্জনিত বিপুল খরচের সম্মুখীন হচ্ছেন ক্রেতারা।
ক্রেতারা তো প্রতারিত হলেনই, যেহেতু প্রত্যেক ক্রেতাই মহান ভারতীয় নাগরিক, তাই ক্রেতারা অর্থনৈতিক এবং স্বাস্থ্যগত ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলে সামগ্রিকভাবে ভারতবর্ষেরই অর্থনৈতিক ও মানবসম্পদগত ক্ষতি হল। এছাড়াও চিনা পণ্য জাতীয় অর্থনীতির আর কি কি ক্ষতি করলো দেখা যাক।
প্রথমত:, প্রত্যক্ষ চিনা পণ্যের বিক্রি বাড়ার সঙ্গে ভারতীয় পণ্যসমূহের বিক্রি হ্রাস পাচ্ছে অর্থাৎ ভারতীয় পণ্য বাজার হারাচ্ছে। ফলে ভারতীয় শিল্প চাহিদার অভাবে ভুগছে। চাহিদা হ্রাসের ফলে শিল্পগুলিতে উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে, ফলস্বরূপ কুটিরশিল্পগুলি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং বৃহৎশিল্পগুলি শ্রমিক ছাঁটাই-এর পথে হাঁটতে বাধ্য হচ্ছে। অর্থাৎ কুটিরশিল্পের শিল্পী এবং বৃহৎ শিল্পের শ্রমিক উভয়ই বেকারত্বের শিকার হচ্ছে, অর্থাৎ তাদের উপার্জন এবং ক্রয়ক্ষমতা দুইই হ্রাস পাচ্ছে। তাদের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার ফলে অর্থনীতির অন্য দুই ক্ষেত্র কৃষি ও পরিষেবা চাহিদা হ্রাসের মুখে পড়ে, ফলস্বরূপ তাদেরও উৎপাদন হ্রাস করতে হয় ও কর্মী ছাঁটাইয়ের পথ ধরতে হয়। ফলে পুনরায় চাহিদা হ্রাস ও অর্থনীতির সবকটি ক্ষেত্রেই পুনরায় উৎপাদন হ্রাস ঘটে। অর্থাৎ ভারতীয় অর্থনীতি বেকারত্ব-ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস-চাহিদা হ্রাস-উৎপাদন হ্রাস-পুনরায় বেকারত্ব—এইরূপ পতনের এক চক্রে প্রবেশ করে। এখন দেখা যাক, বেকারত্বের শিকার হওয়া এবং ফলস্বরূপ উপার্জন থেকে বঞ্চিত হওয়া শ্রমিকদের মোট সংখ্যা কত এবং চিনা পণ্যের অনুপ্রবেশের ফলে ভারতীয় অর্থনীতি বছরে ঠিক কত টাকা ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে।
গত আর্থিক বছরে চীন থেকে ভারতে হওয়া আমদানি হল ১-৮২৯২৮ বিলিয়ন ডলার বা ৪ লক্ষ ৫৭ হাজার ৩২০ কোটি টাকা। এই আমদানি কাঁচামাল হিসেবে হয় না, পুরোটাই হয় নির্মিত বস্তু হিসেবে, অর্থাৎ এই বিপুল পরিমাণ নির্মিত বস্তু ভারতের বাজারে বিক্রি হওয়ায় ভারতীয় শিল্পসামগ্রী এই পরিমাণ বাজার হারালো বা ভারতীয় শিল্পক্ষেত্রের বছরে ৪ লক্ষ ৫৭ হাজার ৩২০ কোটি টাকার চাহিদা হ্রাস হল, অর্থাৎ ভারতীয় শিল্পী ও শ্রমিকদের ৪ লক্ষ ৫৭ হাজার ৩২০ কোটি টাকা উপার্জন হ্রাস হল। শিল্পক্ষেত্রে হওয়া এই বিপুল অর্থনৈতিক ক্ষতির প্রভাব কিন্তু শুধু শিল্পক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকলো না, এর পরোক্ষ প্রভাব পড়ছে কৃষিক্ষেত্রে, শিল্পী ও শ্রমিকরা উপার্জনহীন হওয়ায় তাদের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে। ফলে তারা কৃষিপণ্য কম কিনতে পারছে অর্থাৎ কৃষিপণ্যের চাহিদাও হ্রাস পাচ্ছে, অর্থাৎ কৃষিক্ষেত্রেও উৎপাদন হ্রাস ও ফলস্বরূপ কৃষকদের উপার্জন হ্রাস ঘটছে। চীনা পণ্যের ভারতীয় বাজার দখলের কারণে ভারতীয় কৃষিক্ষেত্রের এই পরোক্ষ ক্ষতি হওয়া ছাড়াও কিছু প্রত্যক্ষ ক্ষতির সম্মুখীনও হচ্ছে ভারতীয় কৃষিক্ষেত্র, কারণ চীনে তৈরী নকল চাল, নকল ডিমের মত অনেক জিনিস ভারতীয় বাজারে ছেয়ে গেছে, বাইরে থেকে দেখে জিনিসগুলিকে ক্রেতারা আসলের থেকে আলাদা করতে পারেন না এবং শরীরের পক্ষে চরম ক্ষতিকর এইসব জিনিস কিনে ফেলেন, ফলে ভারতীয় কৃষিক্ষেত্রও বাজার হারায়। নকল চাল ও নকল ডিমের মত সামগ্রী বাজারে প্রবেশ করে চোরাপথে অর্থাৎ অনথিভুক্ত অবস্থায়, তাই এইসব সামগ্রী বাজারে কত পরিমাণে বিক্রি হল এবং তার ফলে ভারতীয় কৃষিক্ষেত্র প্রত্যক্ষভাবে কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হল তার সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া সম্ভব হয় না, কিন্তু পরোক্ষভাবে কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তার পরিসংখ্যান পাওয়া যায়। দেখা যাক, এ কথা পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে ভারতীয় শিল্পক্ষেত্রের উপার্জন হ্রাস ঘটেছে মোট ৪ লক্ষ ৫৭ হাজার ৩২০ কোটি টাকা, বর্তমান ভারতীয় অর্থনীতিতে যে কোনও মানুষের সার্বিক ভোগব্যয়ের গড়ে প্রায় ৪০ শতাংশ কৃষিপণ্য বা কৃষিজাত পণ্য কেনার জন্য ব্যয় হয়, অর্থাৎ চীনা পণ্যের জন্য শিল্পক্ষেত্রের যে ৪ লক্ষ ৫৭ হাজার ৩২০ কোটি টাকা উপার্জন হ্রাস ঘটছে তার পরোক্ষ ফলস্বরূপ বছরে ১• ৮২৯২৮ লক্ষ কোটি টাকার (৪• ৫৭৩২০ X ৪০ ১০০) কৃষিপণ্যের বিক্রয়-হ্রাস ঘটছে অর্থাৎ কৃষক সমাজের বছরে ১• ৮২৯২৮ লক্ষ কোটি টাকার উপার্জন হ্রাস ঘটছে, এই উপার্জন হ্রাসের ফলে আবার পরোক্ষভাবে শিল্পক্ষেত্রের বিক্রয় তথা চাহিদা হ্রাস পাচ্ছে, কারণ যে কোনও মানুষের সার্বিক ভোগব্যয়ের গড়ে প্রায় ৪০ শতাংশ যেমন কৃষিপণ্য বা কৃষিজাত পণ্য কেনার জন্য ব্যয় হয়। সেইরকমই যে কোনও মানুষের সার্বিক ভোগব্যয়ের এক বড় অংশ শিল্পজাত পণ্য কেনার জন্য ব্যয় হয়, ভারতীয় অর্থনীতিতে এর পরিমাণ গড়ে প্রায় ৩৫ শতাংশ। অর্থাৎ কৃষিক্ষেত্রে ১ • ৮২৯২৮ লক্ষ কোটি টাকা উপার্জন হ্রাসের ফলে পরোক্ষভাবে শিল্পক্ষেত্রের বিক্রি বা চাহিদা হ্রাস পেল ০• ৬৪০২৪৮ লক্ষ কোটি টাকা (১• ৮২৯২৮ X ৩৫/১০০) অর্থাৎ শিল্পক্ষেত্রের শ্রমিক ও শিল্পীদের এই বিপুল পরিমাণ অর্থ উপার্জন-হ্রাস ঘটলো, এই উপার্জন হ্রাসের পর্বে পূর্বোল্লিখিত পদ্ধতিতে বেকারত্ব ও কর্মহীনতার সৃষ্টি হয়, কিন্তু এখানেই শেষ নয়, শিল্পক্ষেত্রের এই উপার্জন-হ্রাস পুনরায় কৃষিক্ষেত্রের উপার্জন হ্রাসের কারণ হয় এবং কৃষিক্ষেত্রের সেই উপার্জন হ্রাস পুনরায় শিল্পক্ষেত্রের উপার্জন হ্রাসের কারণ হয়, এভাবেই পরোক্ষভাবে শিল্প-কৃষি উভয় ক্ষেত্রেরই ক্রমান্বয়ে উপার্জন-হ্রাস ঘটতে থাকে। প্রত্যক্ষ ভাবে ঘটা উপার্জন-হ্রাস এবং পরোক্ষভাবে ঘটা প্রাথমিক উপার্জন-হ্রাস পরিমাপযোগ্য হলেও পরোক্ষভাবে ঘটা পরবর্তী উপার্জন হ্রাস পরিমাপযোগ্য নয়, অর্থনীতিতে এর সুদূরপ্রসারী ক্ষতি দেখা যায়, এবং এই পুনঃ পরোক্ষ ক্ষতির প্রভাব শুধুমাত্র বর্তমান সময়ে আবদ্ধ থাকে না বরং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেও এই ক্ষতির ভার বহন করতে হয়। শিল্পক্ষেত্র ও কৃষিক্ষেত্র মিলিয়ে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রাথমিক ক্ষতির মোট পরিমাণ হল (৪• ৫৭৩২০ +১• ৮২৯২৮ + ০ • ৬৪০২৪৮) ৭• ০৪২৭২৮ লক্ষ কোটি টাকা, প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রাথমিক ক্ষতির কিন্তু এখানেই শেষ নয়, শিল্পক্ষেত্র ও কৃষিক্ষেত্র উপার্জন-হ্রাসের শিকার হলে তার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে অর্থনীতির তৃতীয় ক্ষেত্র পরিষেবা ক্ষেত্রের ওপর, যে কোনও মানুষের সার্বিক ভোগব্যয়ের এক বড় অংশ পরিষেবা ক্ষেত্রের জন্য ব্যয় হয়, ভারতীয় অর্থনীতিতে এর পরিমাণ গড়ে সার্বিক ব্যয়ের প্রায় ১৫ শতাংশ, অর্থাৎ ভারতীয় শিল্পক্ষেত্র ও কৃষিক্ষেত্র যখন ৭• ০৪২৭২৮ লক্ষ কোটি টাকার উপার্জন-হ্রাসের শিকার হচ্ছে তখন ভারতীয় পরিষেবা ক্ষেত্রও (৭ • ০৪২৭২৮ X ১৫/১০০) ১• ০৫৬৪০৯২ লক্ষ কোটি টাকার চাহিদা হ্রাসের অর্থাৎ সমপরিমাণ অর্থের উপার্জন-হ্রাসের সম্মুখীন হয়। পরিষেবা ক্ষেত্র এই পরিমাণ উপার্জন-হ্রাসের শিকার হলে তার প্রাথমিক পরোক্ষ প্রভাব পড়ে কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রের ওপর। পরিষেবাক্ষেত্রে ১• ০৫৬৪০৯২ লক্ষ কোটি টাকা উপার্জন হ্রাসের ফলে পরোক্ষভাবে কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রের বিক্রি বা চাহিদা হ্রাস পেল ০• ৭৯২৩০৬৯ লক্ষ কোটি টাকা {১০০৫৬৪০৯২X (৩৫+৪০)/১০০}। কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রের এই উপার্জন হ্রাস আবার পরোক্ষভাবে পরিষেবাক্ষেত্রের উপার্জন হ্রাস এবং তার ফলে পুনরায় কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রের উপার্জন হ্রাস, উপার্জন হ্রাসের পূর্বোল্লিখিত চক্রের দর্শন এক্ষেত্রেও দেখা যায়।
শুধুমাত্র পরিমাপযোগ্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ক্ষতি নিয়েই আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাক। চিনা পণ্যের বিক্রয় বৃদ্ধির জন্য ভারতীয় অর্থনীতির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ক্ষতি হচ্ছে। (৪• ৫৭৩২০ + ১• ৮২৯২৮ + ০• ৬৪০২৪৮ + ১ ০৫৬৪০৯২ + ০• ৭৯২৩০৬৯ ) ৮• ৮৯১৪৪৪১ লক্ষ কোটি টাকা, সীমাহীন পুনঃপরোক্ষ ক্ষতি তো পরিমাপের অতীত, কিন্তু সংখ্যাতত্বর নিয়মানুসারে চলতি বছরে হওয়া পুনঃপরোক্ষ ক্ষতির পরিমাণ ধরা হয় প্রত্যক্ষ ও প্রাথমিক পরোক্ষ ক্ষতির ৫০ শতাংশ, অর্থাৎ চীনা পণ্যের অনুপ্রবেশের জন্য এক বছরে হওয়া পুনঃপরোক্ষ ক্ষতির পরিমাণ ৪• ৪৪৫৭২২০৫ (৮• ৮৯১৪৪৪১ X ৫০ ১০০) লক্ষ কোটি টাকা। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও পুনঃপরোক্ষ মিলিয়ে মোট ক্ষতির পরিমাণ ১৩ • ৩৩৭১৬৬১৫ (৪• ৪৪৫৭২২০৫+৮• ৮৯১৪৪৪১) লক্ষ কোটি টাকা বা ১৩ লক্ষ ৩৩ হাজার ৭১৭ কোটি টাকা। এই অর্থ আমাদের এক বছরে কেন্দ্রীয় বাজেটের সমান। আমাদের দেশে শিক্ষাখাতে বার্ষিক খরচ হয় চল্লিশ হাজার কোটি টাকা। চিনা পণ্যর জন্য ভারতীয় অর্থনীতির ক্ষতি পরিমাণের দিক দিয়ে এর তেত্রিশ গুণ। আমাদের দেশে স্বাস্থ্যখাতে বার্ষিক খরচ হয় ছত্রিশ হাজার কোটি টাকা। চিনা পণ্যর জন্য ভারতীয় অর্থনীতির ক্ষতি, পরিমাণের দিক দিয়ে এর সাঁইত্রিশ গুণ। আমাদের দেশে সামরিক খাতে বার্ষিক খরচ হয় প্রায় দু’লক্ষ চল্লিশ হাজার কোটি টাকা। চিনা পণ্যর জন্য ভারতীয় অর্থনীতির ক্ষতি, পরিমাণের দিক দিয়ে এর সাড়ে পাঁচ গুণ। অর্থাৎ শুধুমাত্র সস্তার মোহে পড়ে চিনা জিনিস কিনে আমরা প্রতি বছর যে পরিমাণ অর্থ চীনের হাতে তুলে দিচ্ছি তা দিয়ে তেত্রিশ বছর ধরে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার সামগ্রিক ব্যয় বহন করা যেত, সাঁইত্রিশ বছর ধরে দেশের স্বাস্থ্য খাতে হওয়া যাবতীয় ব্যয় বহন করা যেত এবং সামরিক খাতে ব্যয়বরাদ্দ সাড়ে পাঁচ গুণ বাড়ানো যেত যার ফলে সামরিক বলে সাড়ে পাঁচ গুণ বলে বলীয়ান হয়ে আমরা সামরিক দিক দিয়ে গোটা বিশ্বে অপরাজেয় হয়ে উঠতে পারতাম, এছাড়াও কর্মসংস্থানের দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে এই ১৩ লক্ষ ৩৩ হাজার ৭১৭ কোটি টাকায় এগারো কোটি লোকের কর্মসংস্থান হত এবং তাদের প্রত্যেকের মাসে ১০০০০ টাকা করে বছরে এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা উপার্জন হতে পারতো কিন্তু এসব কিছু হচ্ছে না শুধুমাত্র আমরা সস্তার মোহে পড়ে চিনা দ্রব্য কিনছি বলে।
এছাড়াও চিনা পণ্যের অনুপ্রবেশের ফলে ভারতীয় অর্থনীতি আরও কিছু ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। প্রথমত:, চিনা দ্রব্যগুলি ব্যবহার ও নিক্ষেপ (Use and Throw) পদ্ধতির হওয়ায় পুরনো জিনিস সারাইয়ের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা কর্মচ্যুত হয়, মূলতঃ অসংগঠিত ক্ষেত্রে হওয়ায় এই কর্মচ্যুতির সাংখ্যিক হিসাব সম্ভব নয়, কিন্তু বড় সংখ্যক নিম্নবিত্ত ভারতবাসী যে এর ফলে বেকারত্বের জ্বালায় দগ্ধ হয় তা অনস্বীকার্য।
দ্বিতীয়ত:, বংশপরম্পরায় চলে আসা বহু হস্তশিল্প যেগুলি শুধু ভারতের গৌরব-ই নয় বরং বহির্ভারতে ভারতের পরিচয়জ্ঞাপক (যেমন-বেনারসী শাড়ি, কাষ্ঠশিল্প, বাঁশের কাজ, টেরাকোটার কাজ প্রভৃতি) সেই হস্তশিল্পগুলির হুবহু নকল চিনা পণ্যে ভারতীয় বাজার ছেয়ে গেছে, ফলে সেই হস্তশিল্পগুলি বাজার হারাচ্ছে এবং হতাশ হয়ে শিল্পীরা কাজ ছেড়ে দিচ্ছে, ফলস্বরূপ ভারতের গৌরব হিসেবে পরিচিত সেই হস্তশিল্পগুলি চিরতরে লোপ পেতে চলেছে। এককালে ব্রিটিশ অত্যাচারে যেমন ঢাকাই মসলিন বন্ধ হয়ে গেছিল, হয়তো একালে চৈনিক অত্যাচারে আরও অনেক হস্তশিল্প বন্ধ হয়ে যাবে।
ক্ষতি ভবিষ্যতেরও : চিনা পণ্যের জোয়ারে ভারতের বাজারকে ভাসিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে চিন ভারতীয় অর্থনীতির কি কি ক্ষতি করছে তা তো বোঝা গেল, কিন্তু ক্ষতির এখানেই শেষ নয়, দেশের অর্থনীতির ভয়ংকরতম অবস্থা দেখা যাবে ভবিষ্যতে। বিশ্লেষণে দেখা যাক, চিনা পণ্যগুলি তুলনামূলকভাবে সস্তা হয় কারণ চিনা পণ্যগুলি উৎপাদন খরচের চেয়ে কম মূল্যে ভারতের বাজারে পাঠানো হয়, অর্থাৎ চিনা পণ্যগুলি ভারতে পাঠানো হয় সাময়িকভাবে ক্ষতি স্বীকার করে। সাময়িকভাবে এই ক্ষতি স্বীকারের পেছনে থাকে এক দীর্ঘমেয়াদী দুরভিসন্ধি, চীনের সস্তা পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হয়ে ভারতীয় কারখানাসমূহ বন্ধ হয়ে যাবে। কুটীর শিল্পের শিল্পীরাও অভ্যাসের অভাবে ধীরে ধীরে তাদের দক্ষতা হারাবে। ভারতবর্ষ তখন বন্ধ শিল্পের এক শ্মশানভূমিতে পরিণত হবে। ভারতীয় ক্রেতারা তখন সম্পূর্ণরূপে চীনের পণ্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে আর সেই সময়ে ভারতীয় বাজারের ওপর সেই একচেটিয়া আধিপত্যের সুযোগ নেবে চীন। তখন তারা যে দাম ধার্য করবে ভারতীয় ক্রেতাদের সেই দামেই কিনতে হবে চীনের সামগ্রী। অর্থনীতির পরিভাষায় এই অপকৌশলকে বলা হয় ডাম্পিং। এই ডাম্পিং -এর চুড়ান্ত অপপ্রয়োগ যদি অবিলম্বে রোধ করা না যায় তাহলে দেশের যে দুরবস্থা হবে, অনাগত সেই ভয়ংকর ভবিষ্যত যেন কল্পনাকেও হার মানায়।
ক্ষতি পশ্চিমবঙ্গেরও :
গোটা দেশের কি ক্ষতি হবে তা তো বোঝা গেল। রাষ্ট্রের এক অঙ্গরাজ্য হিসেবে পশ্চিমবঙ্গও এই ক্ষতির শিকার হবে। কিন্তু বিশেষ আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির জন্য পশ্চিমবঙ্গের ক্ষতি হবে বেশি, বিশ্লেষণে দেখা যাক। বিশেষ আর্থ-রাজনৈতিক কারণে পশ্চিমবঙ্গের বৃহৎশিল্পগুলি আগেই বেশিরভাগ বন্ধ হয়ে গেছে, এখন পশ্চিমবঙ্গের যুবসমাজের উপার্জনের সবেধন নীলমণি ক্ষুদ্র শিল্পগুলি, চিনা সস্তা পণ্যের আগ্রাসনে সবচেয়ে বেশি বিপদে পড়েছে মূলত: ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেক্ট্রনিক্যাল দ্রব্যের উৎপাদনকারী এই ক্ষুদ্র শিল্পগুলিই, পশ্চিমবঙ্গের যুবককুলের সামনে তাই বেকারত্বের হাতছানি বড় প্রকট। এছাড়াও চীনের সস্তা লেড় আলো বিপদে ফেলেছে পশ্চিমবঙ্গের মৃৎ-শিল্পীকুলকে, চীনের সফট টয় বিপদে ফেলেছে এখানকার খেলনা নির্মাণকারী কুটিরশিল্পীদের। পশ্চিমবঙ্গের কুটিরশিল্পীরাও তাই আজ বড় বিপদাপন্ন।
পশ্চিমবঙ্গের বৃহৎশিল্পের মধ্যে টিম টিম করে টিকে থাকা একমাত্র শিল্প পাটশিল্পও আজ বিপদের মুখে। চীনের তৈরী বিভিন্ন সস্তা বিকল্প, পশ্চিমবঙ্গের পাটশিল্পের নাভিশ্বাস তুলছে। দেশের মধ্যে সর্বাধিক জনঘনত্ব বিশিষ্ট রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ শুধুমাত্র কৃষির ওপর নির্ভরশীল হতে পারবে না এবং পশ্চিমবঙ্গ খনিজ সম্পদেও ন্যূন। অর্থাৎ একথা অনস্বীকার্য যে চীনের অর্থনৈতিক আগ্রাসনে গোটা দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থাই সবচেয়ে খারাপ আর তাই পশ্চিমবঙ্গের লোকেদেরই সর্বাপেক্ষা বেশি প্রতিরোধ গড়ে তোলা উচিত।
পরিবেশের ক্ষতি :
চিনা দ্রব্য ব্যবহারের ফলে অর্থনীতির চরম ক্ষতি তো হয়ই কিন্তু এই ক্ষতি শুধুমাত্র অর্থনীতির সীমানায় আবদ্ধ নেই। পরিবেশও চরম ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে, কারণ, এসব চিনা পণ্য সাধারণতঃ ক্ষতিকর কিছু রাসায়নিকের দ্বারা নির্মিত হয় যা দামে সস্তা হলেও পরিবেশের ও ব্যবহারকারীর স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। শুধুমাত্র ব্যবহারকালে নয়, বরং ব্যবহারের পরে ফেলে দেবার পরও এই বস্তুগুলি বিশ্লিষ্ট হয়ে পরিবেশে মিশে যায় না, বরং দীর্ঘদিন ধরে পরিবেশে পড়ে থেকে পরিবেশকে বিষাক্ত করে। ফলে দেশের স্বাভাবিক বাস্তুতন্ত্র ব্যাহত হয়, এবং এর ফলে একদিকে যেমন দেশের কৃষি-উৎপাদন হ্রাস পায় অন্যদিকে সাধারণ নাগরিকের ও সরকারের স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত ব্যয়ও বৃদ্ধি পায়।
স্বাস্থ্যের ক্ষতি
ক্ষতিকর রাসায়নিকের দ্বারা নির্মিত পরিবেশশত্রু চিনা পণ্যগুলি মানুষের শরীরের পক্ষেও একই রকম ক্ষতিকর। চিনা পণ্য ব্যবহারকারী ব্যক্তিবর্গ কঠিন অসুখের শিকার হচ্ছেন, বিশেষ করে শিশুদের ওপর এর প্রভাব পড়ছে অসীম। শুধুমাত্র চিকিৎসাব্যয়ের অর্থনৈতিক ক্ষতির মাপকাঠিতে এই ক্ষতি পরিমাপযোগ্য নয়। স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব সৃষ্টিকারী চিনা পণ্য চিরস্থায়ী ক্ষতি করছে দেশের মানবসম্পদে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, আমেরিকা বা অন্যান্য পাশ্চাত্যের দেশ থেকে আসা ফাস্ট ফুড, জাঙ্কফুড এবং ঠান্ডা পানীয়গুলিও শরীরের এবং পরিবেশের প্রচুর ক্ষতি করে তাই সেগুলি থেকেও জনগণের সচেতন থাকা উচিত।
ভারতের প্রতি চীনের ঐতিহাসিক শত্রুতা :
ভারতের সঙ্গে এই সর্বাত্মক শত্রুতা চীন শুধু ভারতের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে করছে তাই নয়, বিশ্ব রাজনীতিতেও চীন ভারতের প্রতি একই রকম বৈরী ভাবাপন্ন। রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যপদের জন্য ভারতকে মনোনীত করেছিল নিরাপত্তা পরিষদের বর্তমান সদস্য সব কটি দেশ কিন্তু চীন ভেটো প্রয়োগ করে ভারতকে সেই মর্যাদা পাওয়া থেকে বঞ্চিত করেছে। কূটনীতি জগতের নির্মম পরিহাস হল এই যে চীন নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হয়েছে এবং তজ্জনিত কারণে ভেটো প্রয়োগের অধিকারী হয়েছে ভারতেরই দয়ায়।
দুঃখবহ হলেও সেই ইতিহাসকে একটু স্মরণ করা যাক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানে ১৯৪৫ সালে রাষ্ট্রপুঞ্জ স্থাপিত হয়, বিশ্বযুদ্ধজয়ী চার দেশ অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ফ্রান্স রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিদের চার সদস্য দেশ হিসেবে ভেটো প্রয়োগের অধিকার লাভ করে। ১৯৫৫ সালে রাষ্ট্রপুঞ্জ ঠিক করে বিশ্বের বৃহত্তম মহাদেশ এশিয়ার একটি দেশকে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য করা হবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিধ্বস্ত জাপান তখন এশিয়ার প্রথম সারির দেশ হিসেবে গণ্য হত না। এশিয়ার বৃহৎ দুই দেশ ভারত এবং চীনের মধ্যে যে কোনও একটি দেশকে রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য করার কথা পরিষদে গৃহীত হয়। কমুনিষ্ট চীনকে সমর্থন করে কম্যুনিষ্ট সোভিয়েত ইউনিয়ন আর গণতান্ত্রিক দেশ ভারতকে সমর্থন করে গণতান্ত্রিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্স। সংখ্যাধিক্যে জয়ী ভারত তখন রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য পদ লাভ করার যোগ্যতা অর্জন করেছিল কিন্তু ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নেহেরু সেই স্থায়ী সদস্যপদ গ্রহণ না করে চীনকে সেই পদ ছেড়ে দেন। চীন সেই উপকারের প্রতিদান দিচ্ছে আজ ভারতের বিরুদ্ধেই ভেটো প্রয়োগ করে।
এই অভিনব চৈনিক কৃতঘ্নতারই আরেক নিদর্শন দেখা যাচ্ছে চিনা পণ্যের ক্ষেত্রে। ভারতের দয়ায় রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যপদ লাভ করে চীন যেমন ভারতের বিরুদ্ধেই ভেটো প্রয়োগ করেছিল সেরকমই ভারতে পণ্যসামগ্রী বিক্রি করে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে তারা ভারতের সঙ্গেই শত্রুতা করছে।
ক্ষতির অপর দিক, সীমান্তের ওপারে : চিনা পণ্যের ব্যবহার যে শুধুমাত্র উপরিউক্ত পদ্ধতিতে ভারতীয় অর্থনীতির এবং মানবসম্পদের ক্ষতিসাধন করছে তা নয়, চিন যে সাড়ে চার লক্ষ কোটি টাকা বাড়তি লাভ করছে সেই অর্থ তারা কিভাবে ব্যয় করছে দেখা যাক, চিন এই অর্থের দ্বারা নিজের এবং পাকিস্তানের সেনাবাহিনীকে উন্নত করছে, তাদের জন্য অত্যাধুনিক অস্ত্র ক্রয় করছে এবং সেই অত্যাধুনিক অস্ত্রের বলে বলীয়ান চিনা এবং পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ভারতের সীমান্তে হামলা করছে এবং আমাদের দেশের বীর জওয়ানদের মৃত্যুর কারণ হচ্ছে।
ভারতের সীমান্তে চীনের হামলা অবশ্য আজ নতুন নয়, অতীতেও এর নজির রয়েছে এবং সেই উদাহরণ খুব সুখকর নয়, ১৯৫০ সালেই ভারত ও চীনের একমাত্র মধ্যবর্তী রাষ্ট্র (বাফার স্টেট) তিব্বতকে আক্রমণ করে চিন। স্বাধীনতার পর ‘হিন্দি-চিনি ভাই ভাই’ নীতিতে কুঁদ হয়ে থাকা আমাদের রাষ্ট্রপ্রধান নেহেরু কান দেননি চিনা ড্রাগনের আক্রমণে বিপন্ন তিব্বতের আর্তচিৎকারে, চীনের আগ্রাসনের হাত থেকে রক্ষা করেননি প্রতিবেশী বন্ধুরাষ্ট্র তিব্বতকে। ফল ফলতে দেরি হয়নি, তিব্বতকে হজম করার পর চীনের সঙ্গে ভারতের সরাসরি সীমানা স্থাপিত হয়েছিল, আগ্রাসনকারীর স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অনুযায়ী চিন সেই সীমানাকে লঙ্ঘন করে ঝাপিয়ে পড়েছিল ভারতের ওপর ১৯৬২ সালে, তৎকালীন নিষ্ক্রিয় ভারত সরকার ব্যর্থ হয়েছিল সেই আক্রমণকে ঠেকাতে। চিন দখল করেছিল ভারতের ৬২০০০ বর্গ কিলোমিটার পরিমাণ ভূখণ্ড, হিমালয়ের বরফাবৃত প্রান্তরে অবস্থিত সেই বিপুল পরিমাণ ভূখণ্ডের গুরুত্ব অনুধাবন করতে ভুল করেছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নেহেরু, ঊষর সেই প্রান্তর সম্পর্কে বলেছিলেন, “Not a blade of grass grows there” (সেখানে তো একটা ঘাসও গজায় না, অর্থাৎ কৃষিকাজ হয় না)। কিন্তু সে ঊষর প্রান্তরের গুরুত্ব ছিল অন্য জায়গায়, সমভূমিপ্রধান ভারত এবং মরুভূমিপ্রধান চীনের মধ্যে প্রাকৃতিক প্রাচীর নির্মাণকারী চিন নিজের ভূপ্রাকৃতিক অবস্থানের কারণেই বিশাল সামরিক গুরুত্বের অধিকারী, হিমালয় কজায় থাকায় এখন সেই সামরিক সুবিধা ষোলআনা উশুল করছে চীন, হিমালয়ের ওপরে অপেক্ষাকৃত উঁচুস্থানে প্রচুর পরিমাণ সমরোপকরণ মজুত এবং সময়োপযোগী পরিকাঠামো নির্মাণ করেছে চীন। প্রতি বছরে শতাধিক বার তারা ভারতের সীমান্ত অতিক্রম করে। হিমালয়ের উচ্চস্থান চীনের হাতে ছেড়ে অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমিতে অবস্থানরত ভারত সেই অনুপ্রবেশসমূহ ঠেকাতে প্রতি বছর খরচ করে কয়েক হাজার কোটি টাকা। ঘাস না গজানো সেই কয়েক হাজার বর্গকিলোমিটার ঊষর এলাকা ভারতের হাতে থাকলে সেই বাৎসরিক অর্থব্যয় ভারতের না হয়ে চীনের হত।
শুধুমাত্র সামরিক গুরুত্বই নয়, এই উষর জায়গাটির অর্থনৈতিক গুরুত্বও যথেষ্ট, বর্তমানে সারা বিশ্বে পানীয় জলের ব্যবসা প্রায় কুড়ি হাজার কোটি ডলারের (টাকার মূল্যে প্রায় ১৫ লক্ষ কোটি টাকা)। বর্তমানে এই ব্যবসার প্রায় পুরোটাই কুক্ষিগত আছে পাশ্চাত্যের দেশগুলি হাতে। বিশেষতঃ ঠান্ডা পানীয় কোম্পানীগুলি এই বাজারকে দখল করেছে। ভারতেও পানীয় জলের ব্যবসা বর্তমানে প্রায় দেড় হাজার কোটি ডলারের (টাকার অঙ্কে প্রায় ১ লক্ষ কোটি টাকা)। এই টাকার বহির্গমন প্রতিবছরই হচ্ছে বা বলা যায় এই টাকা প্রতি বছরই জলে যাচ্ছে। অর্থনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে এই পরিমাণ আগামীদিনে আরও বাড়বে তীব্র গতিতে, বর্তমান অর্থনৈতিক বিশ্ব যদি খনিজ তেলের হয় তাহলে আগামী অর্থনৈতিক বিশ্ব হবে পানীয় জলের, পানীয় জলের দ্বিতীয় বৃহত্তম ভাণ্ডার (পানীয় জলের বৃহত্তম ভাণ্ডার কুমেরু কোনও একটি দেশের অধিকৃত নয়, রাষ্ট্রপুঞ্জের সরাসরি আওতায়) হিমালয় নিজের হাতে থাকায় সেই অনাগত আগামীতে চীন বিশ্ব অর্থনীতিতে কি বিপুল সুবিধা পাবে এবং হিমালয় হস্তচ্যুত হওয়ায় আগামীর ভারত বিশ্ব অর্থনীতিতে কি বিপুল সুবিধা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হবে তা চিন্তার বাইরে। এখানেই শেষ নয়, নদীমাতৃক ভারতবর্ষের প্রধান তিনটি নদনদীর অন্যতম ব্রহ্মপুত্রের উৎস সেই সময় থেকে চীনের দখলে, ইতিমধ্যেই সেই উৎসের পরবর্তী অংশে তারা বাঁধ নির্মাণ করেছে, যে কোনও মুহূর্তে তারা ব্রহ্মপুত্রের গতিপথ পরিবর্তন করে দিতে পারে, সেক্ষেত্রে আসাম সহ সমস্ত উত্তর-পূর্ব ভারত সংকটাপন্ন হবে।
আগ্রাসী চীন কিন্তু এতেই সন্তুষ্ট নয়, হিমালয়ের বাকি অংশ এবং অরুণাচল প্রদেশ সহ সমস্ত উত্তর-পূর্ব ভারত তারা ছলে-বলে-কৌশলে দখল করতে চায়। হিমালয়ের বুকে অবস্থিত ঐতিহাসিক ভারতবন্ধু নেপাল আজ চীনের কৌশলে এবং পূর্বতন ভারত সরকারের উদাসীনতায় বর্তমানে কমুনিষ্ট প্রভাবিত হয়ে চীনের করালগ্রাসে, হিমালয়ে অবস্থিত আরেক ভারত বন্ধু ভুটান চীনের কৌশলের কাছে নতিস্বীকার না করায় সেখানে বলপ্রয়োগের আশ্রয় নিয়েছে তারা।
পরিস্থিতি আজও সেই একই, পঞ্চাশের দশকে আক্রান্ত হয়েছিল বন্ধুরাষ্ট্র তিব্বত, ২০১৭-য় আক্রান্ত হয়েছে বন্ধুরাষ্ট্র ভুটান, এবারকার মত ভারত সরকারের সতর্কবাণীতে কান দিয়ে চীন পশ্চাদপসরণ করেছে, তা বলে কর্তব্যকর্ম বিস্মৃত হলে হবে না, সেদিনের মত আজও যদি কর্তব্যকর্ম বিস্মৃত হয়ে আমরা বন্ধুরাষ্ট্র ভুটানকে রক্ষা না করি, তাহলে আগ্রাসী চীনের ব্যাদিত মুখগহ্বর আমাদেরও ছেড়ে কথা বলবে না। চিন-ভুটান বিবাদের স্থান ডোকলাম থেকে ভারতের সীমান্ত মাত্র আধঘন্টার পথ, ডোকলাম নির্বিবাদে হজম করার পর সেই সামান্য পথ অতিক্রম করে আমাদের উত্তরবঙ্গ সংলগ্ন সীমানায় তারা আক্রমণ করবে এবং উত্তরবঙ্গকে বিপন্ন করার পাশাপাশি উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে অবশিষ্ট ভারতের যোগাযোগের একমাত্র পথটিকেও (দিনাজপুর- জলপাইগুড়ি- দার্জিলিং নিয়ে গঠিত ‘মুরগীকণ্ঠ’ বা ‘Chicken’s Neck’) আনবে নিজের অধিকারে, উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে অবশিষ্ট ভারতের যোগাযোগ বিনষ্ট হবার ফলে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে সোনার খনিসদৃশ অরুণাচল প্রদেশ আসবে তাদের অধিকারে।
এ প্রসঙ্গে বলা যায়, অরুণাচল প্রদেশ সহ সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতকেও নেহরুর ভাষা অনুযায়ী বলা যায় “Not a blade of grass grows there”, এখানকার ভূপ্রকৃতি পাহাড়ী ঢালবিশিষ্ট হওয়ায় কৃষিতে এই অঞ্চল খুব পিছিয়ে। কৃষিতে উত্তর-পূর্ব ভারত খুবই পিছিয়ে, কিন্তু উত্তর-পূর্ব ভারতের গুরুত্ব অন্য জায়গায়, হিমালয়ের ঠিক প্রান্তদেশে অবস্থিত এই অঞ্চলটি হিমালয়ের বরফ গলা জলে সমৃদ্ধ থাকে সারাবছর, পাহাড়ী ঢাল বরাবর সেই জল প্রচণ্ড গতিতে নিম্নমুখী হয়, ফলে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে অরুণাচল প্রদেশ সহ সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারত সোনার খনিসদৃশ। বিশেষজ্ঞদের মতে শুধুমাত্র অরুণাচল প্রদেশেই বছরে এক লক্ষ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হতে পারে, সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারত মিলিয়ে পরিমাণ আরও বেশী হতে পারে। আজ ক্ৰমক্ষয়িষ্ণু খনিজ তেলের ভাণ্ডারের ওপর এবং ক্রমক্ষয়িষ্ণু খনিজ কয়লাজাত তাপবিদ্যুতের ওপর নির্ভরশীল গোটা বিশ্বের শিল্প ও পরিষেবা ক্ষেত্র যখন বিকল্প শক্তির সন্ধানরত তখন এই বিপুল পরিমাণ জলবিদ্যুৎ ভারতীয় অর্থনীতির এক চিরস্থায়ী সম্পদে পরিণত হতে পারে। কিন্তু চীনের সেনাবাহিনীর আগ্রাসী নীতির কারণে সেই সম্ভাবনা বাস্তবায়িত হচ্ছে না।
ক্ষতি উত্তর-পশ্চিমেও :
চৈনিক আগ্রাসন শুধুমাত্র উত্তরবঙ্গ এবং উত্তর-পূর্ব ভারতে আবদ্ধ থাকবে তা নয়, তারা আক্রমণ করবে কাশ্মীর সীমান্তে আর এখানে তাদের দোসর হবে তাদেরই এবং আমেরিকার প্রদেয় অস্ত্র ও অর্থে বলীয়ান পাকিস্তান।
কাশ্মীরের ওপর পাকিস্তান ও চীনের লালসাজর্জর দৃষ্টিনিক্ষেপ আজকের কথা নয়, স্বাধীনতার পর থেকেই মধ্য এশিয়ার সঙ্গে ভারতের স্থলপথে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম কাশ্মীরকে ভারতের কাছ থে
কে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে চলেছে পাকিস্তান এবং সেই কাজ তারা করছে চীন ও আমেরিকা প্রদত্ত অর্থবলে এবং অস্ত্রবলে।
কাশ্মীরের ওপর পাকিস্তান ও চীনের এত আকর্ষণ থাকার বেশ কিছু কারণ আছে। প্রথমত:, কাশ্মীরের প্রকৃতি যেন ঈশ্বরের কাছ থেকে বিশেষ আশীর্বাদপ্রাপ্ত, তুলনারহিত নৈসর্গিক সৌন্দর্যের অধিকারী কাশ্মীর যেন আক্ষরিক অর্থেই ভূস্বর্গ। স্মরণাতীত কাল থেকেই পর্যটকদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করে এসেছে কাশ্মীর। কাশ্মীরের প্রতি পর্যটকদের এই আকর্ষণকে কেন্দ্র করে পর্যটন শিল্পে কাশ্মীরকে অনেক উন্নত করে তোলা যেত এবং প্রচুর পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা যেত। সেই বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ কত দেখা যাক, ১৯৬০ সালে সুইজারল্যান্ডের পর্যটন খাতে আয় ছিল মাত্র ৯৫.২ লক্ষ ডলার বা ৪ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা, ২০১৪ সালে সুইজারল্যান্ডের পর্যটন খাতে আয় ছিল ৭০৯১৮ কোটি ডলার বা ৪৪২০৩১৮ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা। ১৯৬০ সালে কাশ্মীরের পর্যটন খাতে আয় ছিল ৩৭ কোটি ডলার বা ১৭৬ কোটি ১২ লক্ষ টাকা, ২০১৪ সালে কাশ্মীরের পর্যটন খাতে আয় ছিল মাত্র ২৫০০ কোটি ডলার বা ১৫৫৮২৫ কোটি টাকা। উপরোক্ত পরিসংখ্যান থেকে দেখা গেল ১৯৬০ সালে কাশ্মীরের পর্যটন খাতে আয় সুইজারল্যান্ডের পর্যটন খাতে আয়ের ৩৯ গুণ ছিল কিন্তু ২০১৪ সালে সুইজারল্যান্ডের পর্যটন খাতে আয় কাশ্মীরের পর্যটন খাতে আয়ের ২৫ গুণ। ১৯৬০ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত এই ৫৪ বছরে সুইজারল্যান্ডের আয়বৃদ্ধি হয়েছে ৭৪৫০০ গুণ, একই সময়কালে কাশ্মীরের আয়বৃদ্ধি হয়েছে মাত্র ৭০ গুণ। এই সময়কালে কাশ্মীরের আয়বৃদ্ধি যদি সুইজারল্যান্ডের আয়বৃদ্ধির সমহারে হত তাহলে ২০১৪ সালে কাশ্মীরের পর্যটন খাতে আয় হত ২৭৫৬২৭০ কোটি * ডলার বা ১৭১৭৯৮১১০ কোটি টাকা যা গোটা ভারতের মোট জিডিপি-র ৮ গুণ। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কাশ্মীর ও সুইজারল্যান্ডের আয়বৃদ্ধির এই বিপরীতমুখী অবস্থানের একটাই কারণ, সুইজারল্যান্ড পর্যটন শিল্পে যত উন্নতি করতে পেরেছে কাশ্মীর তা করতে পারেনি। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিক দিয়ে কাশ্মীরের তুলনায় অনেক পিছিয়ে থাকা সুইজারল্যান্ড পর্যটন শিল্পে এত বেশী উন্নতি করলো অথচ কাশ্মীর গহন তিমিরে তলিয়ে গেল এর একটাই কারণ কাশ্মীরে উগ্রপন্থার জন্য পর্যটকদের স্বাভাবিক ভীতি। এই ভীতি সৃষ্টি করেছে পাকিস্তান চীনের সাহায্যে, তাদের লক্ষ্য একটাই, উগ্রপন্থার ক্রমবর্ধমান চাপে অতিষ্ঠ হয়ে ভারত যদি কাশ্মীরকে পাকিস্তানের হাতে তুলে দেয় তাহলে পর্যটন শিল্পে কাশ্মীরের সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে পাকিস্তান ও চীন নিজেদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি করবে। চীন এবং চীন প্রদত্ত অর্থ এবং অস্ত্র সাহায্যে বলীয়ান পাকিস্তান না থাকলে শুধু কাশ্মীরের পর্যটন শিল্পের সাহায্যেই ভারত আজ বছরে উপরোক্ত পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আয় করতে পারতো যা ভারতের অর্থনীতিকে উন্নতির শিখরে নিয়ে যেতে পারতো এবং পর্যটন শিল্পে প্রচুর লোকের কর্মসংস্থানও হতে পারতো। . প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, কাশ্মীর পর্যটন শিল্পে উন্নত হোক এটা সুইজারল্যান্ডসহ স্ক্যান্ডিনেভিয়ার অন্য দেশগুলি এবং পাশ্চাত্যের অন্য কোনও দেশ চায় না তা হলে তাদের পর্যটন শিল্পের রমরমায় ভাগ পড়বে। সেজন্য তারাও কাশ্মীরের ওপর পাকিস্তানের আগ্রাসনে গোপনে অর্থনৈতিক সাহায্য করে।
ক্ষতির আরেক দিক :
চিন তার অর্থবলে এবং অস্ত্র বলে শুধুমাত্র নিজেদের এবং পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর দ্বারাই যে ভারতের ক্ষতি করছে তা নয় সেই অর্থবল এবং অস্ত্রবল ভারতের অভ্যন্তরেও নিয়মিত প্রযুক্ত হচ্ছে ভারতের ক্ষতি সাধনের জন্য।
মূলত: কৃষিপ্রধান ভারত খনিজ সম্পদেও সমৃদ্ধ, ভারতের প্রায় আশীটি এমন জেলা আছে যে জেলাগুলি বিভিন্ন খনিজ পদার্থে সমৃদ্ধ, জেলাগুলি মূলতঃ মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের কিছু অংশে অবস্থিত। এই খনিজ পদার্থের সঠিক ব্যবহার করা সম্ভব হলে ভারত শিল্পে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশে পরিণত হত। কিন্তু ভারত শিল্পে স্বয়ম্ভর হলে চীনের বাজার নষ্ট হবে, চীন তার উৎপাদিত পণ্য ভারতে রপ্তানি করতে পারবে না, তাই চীন ভারতের শিল্পক্ষেত্রের এই বিপুল সম্ভাবনাকে নষ্ট করার জন্য এই জেলাগুলিতে মাওবাদী নামক উগ্রপন্থীদের অর্থ এবং অস্ত্রদ্বারা সাহায্য করছে। চীনপ্রদত্ত অর্থবলে এবং অস্ত্রবলে বলীয়ান মাওবাদীরা এই সমস্ত এলাকায় এমন অশান্তির পরিবেশ তৈরী করেছে যে এখানে ন্যূনতম পরিকাঠামো তৈরী করতে ব্যর্থ হয়েছে দেশের শাসনব্যবস্থা, ফলে ভারতের শিল্পে উন্নত হওয়ার সম্ভাবনা বাস্তবায়িত হচ্ছে না।
ভারতের শিল্পোন্নয়নের সমস্ত সম্ভাবনাকে চীন অঙ্কুরেই বিনষ্ট করতে চায়, তার লক্ষ্য সে ভারতকে তার উৎপাদিত পণ্যের বাজার এবং কাঁচামাল সরবরাহকারী দেশ হিসেবে রেখে দিতে চায়, ঠিক ঔপনিবেশিক আমলের ব্রিটিশের মতো। বস্তুতঃ পলাশীর যুদ্ধের আগের মানদণ্ডধারী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বণিকের সঙ্গে আজকের চীনের কার্যপদ্ধতির অদ্ভুত সাদৃশ্য।
উদাহরণ :
সমস্ত সমস্যাটাকে একটা কল্পবাস্তব উদাহরণের মাধ্যমে একবার মানসপটে অঙ্কিত করে নেওয়া যাক।
রামবাবু বাজারে গেলেন, নিজের পকেটের টাকা দিয়ে ভারতীয় পণ্য না কিনে বিদেশী পণ্য কিনলেন, বিক্রির অভাবে কুম্ভকার শ্যামবাবু বেকার হলেন, বিক্রির অভাবে ভারতীয় শিল্প বন্ধ হল, শিল্পের শ্রমিক যদুবাবু বেকার হলেন, বিদেশী পণ্য ক্রয়ে ব্যয়িত রামবাবুর পকেটের টাকা চীনে এবং আমেরিকায় চলে গেল, তারই একটা অংশ মাওবাদীরা অর্থসাহায্য হিসেবে পেল, তারা খনিজ সম্পদের উত্তোলন বন্ধ রাখলো, রামবাবুর পকেটের টাকার আরেকটি অংশের সাহায্যে চিনা অনুপ্রবেশকারীরা উত্তর-পূর্ব ভারতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন। করার কাজে ব্যাঘাত ঘটালো। রামবাবুর পকেটের টাকার আরেকটি অংশের সাহায্যে (যেটি আমেরিকার মাধ্যমে পাকিস্তানের কাছে গেছে। পাকিস্তান কাশ্মীরে উগ্রপন্থা বজায় রাখলো।
১২ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, ভারতীয় শিল্প বলতে দেশে কিছু অবশিষ্ট নেই, বাজারে শুধু বিদেশী পণ্য, দাম অবশ্য আগের মত সস্তা নয়, আকাশছোঁয়া। রামবাবু বাধ্য হয়ে তাই কেনেন, ওনার সময়ও ভালো যাচ্ছে না, ওনার ছেলে উচ্চশিক্ষিত, ইঞ্জিনিয়ার, কিন্তু খনিজ পদার্থ ও বিদ্যুৎশক্তির অভাবে দেশে বৃহৎশিল্প কিছু নেই, ফলে ওনার ছেলে ভালো কোনও চাকরি না পেয়ে বাধ্য হয়ে সেনাবাহিনীতে নাম লিখিয়েছে, বর্ডার-এ পোস্টিং, অবশ্য একা নয়, শ্যামবাবু আর যদুবাবুর ছেলেও বেকারত্বের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে বাধ্য হয়ে সেনাবাহিনীতে নাম লিখিয়েছে, ওরাও রামবাবুর ছেলের সঙ্গে একই ব্যাটেলিয়নে আছে।
বাজার থেকে বিরস বদনে ফিরে রামবাবু দেখলেন সেনাবাহিনীর থেকে একটা চিঠি এসেছে, ছেলের খবর আছে বুঝতে পেরে আনন্দিত মনে রামবাবু চিঠি খুলে পড়লেন আর চিৎকার করে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। বিদেশী পণ্য ক্রয়ে ব্যয়িত রামবাবুর পকেটের টাকার সাহায্যে চিনা ও পাকিস্তানি সেনাবাহিনী যে স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র কিনেছে তার গুলিতে রামবাবু, শ্যামবাবু আর যদুবাবুর ছেলে মারা গেছে।
রামবাবু নিজের পকেটের টাকায় নিজেরই সর্বনাশ করলেন।
বিপদ বহুমুখী হলেও একটা কথা বলা যায়, এসময় থেকে অর্থাৎ ১৯৯১ সালের পর থেকে কেন্দ্রীয় স্তরেও হাকিম আর হুকুম দুইয়েরই বদল নিয়মিত ব্যবধানে হতে থাকলো, অর্থনীতির মতো রাজনীতির ক্ষেত্রেও প্রতিদ্বন্দ্বীতা দেখা গেল। অসৎ রাজনীতিবিদরাও গদির লোভে কিছুটা হলেও দেশবাসীর কথা ভাবতে লাগলো। নতুন সহস্রাব্দের প্রথম অর্ধদশকে এতদিনের অবহেলিত পরিকাঠামো ক্ষেত্র কিছুটা হলেও গুরুত্ব পেল। পরিকাঠামো ক্ষেত্রে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি পেল। সোনালী স্বর্ণ চতুর্ভুজ ইত্যাদি নানানরকম পরিকল্পনার দ্বারা দেশের পরিবহনের হাল ফেরানোর এবং নতুন বিনিয়োগকারীদের উঠে আসার পথ তৈরীর চেষ্টা হয়েছিল। দুষ্ট-চতুষ্টয়ের কায়েমী স্বার্থে ঘা লেগেছিল, ফলে হাকিম বদলাতে দেরি হয়নি। পরের দশ বছর পুতুল হাকিম আর দুষ্ট-চতুষ্টয়ের অন্তরাত্মার হুকুমে দুর্নীতি হয়েছিল দুর্নিবার। জর্জরিত জনসাধারণ হাকিম বদলেছিল সোৎসাহে। নতুন হাকিমের হুকুমে দুর্নীতি-দৈত্য আজ কিছুটা হলেও বোতলবন্দী। সরাসরি অ্যাকাউন্টে টাকা ট্রান্সফার, আধার-প্যান সংযোগ সাধন, বিমুদ্রাকরণ ইত্যাদি নানান অস্ত্রের আঘাতে সে আজ খানিকটা হলেও ঘায়েল। তবে এতেই কিন্তু নিশ্চিন্ত হলে চলবে না স্বেচ্ছাকৃত ঋণখেলাপীদের এবং প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠনকারীদের বিরুদ্ধে আরও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ বাঞ্ছনীয়।
দেশ দুর্নীতিমুক্ত হওয়ার দিকে কিছুটা হলেও এগোল, তুলনামূলকভাবে কিছুটা অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধিও ঘটলো, জনসাধারণ কিছুটা হলেও “আচ্ছে দিন”-এর স্বাদ পেল। কিন্তু এরপর কি? ১৯৯১-র সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির মত আজকের পৃথিবীতে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিও তো সঙ্কটে। জাতীয় অর্থনীতিকে বাঁচাতে গেলে তো এই জীর্ণ তরণীকে ত্যাগ করতে হবে। এ বার বিকল্প কি? বিদেশী অর্থনীতির অক্ষম ও সক্ষম অনুসরণ করে সাতটি দশক তো অতিক্রম করা গেল। কিন্তু হিসেবের খাতা খুলে দেখা গেল হাতে রয়েছে পেন্সিল। বাঁদিকে হাঁটার প্রথম চুয়াল্লিশ বছরে দেশের মাথাপিছু গড় আয়ের (জি ডি পি) বৃদ্ধি ছিল বছরে ৩.৫ থেকে ৪ শতাংশ, ডানদিকে হাঁটার পরবর্তী ২৭ বছরে আমাদের আমাদের দেশের মাথাপিছু গড় আয়ের (জি ডি পি) বৃদ্ধি ছিল বছরে ৫.৫ থেকে ৮ শতাংশ । আমাদের সঙ্গে একইসময়ে যাত্রা শুরু করেছিল আনবিক বোমা বিধ্বস্ত জাপান এবং নবগঠিত মরুময় ইস্রায়েল। আজ মাথাপিছু গড় আয়ের (জি ডি পি) দিক দিয়ে তারা বিশ্বের শীর্ষস্থানীয়। গত সাত দশকে জাপানের জি ডি পি’র বৃদ্ধির হার ছিল বছরে গড়ে ১০ শতাংশ আর ইস্রায়েলের ৮ থেকে ৯.৫ শতাংশ। এক যাত্রায় পৃথক ফলের একটাই কারণ। জাপান এবং ইস্রায়েল নিজেদের দেশের উন্নতির জন্য নিজেদের দেশের উপযোগী। অর্থনীতিই গ্রহণ করেছিল আর অর্থনীতি শাস্ত্রের আবিষ্কর্তা দেশ ভারতবর্ষ (অর্থশাস্ত্র-কোটিল্য) নিজেদের দেশের উন্নতির জন্য মুখাপেক্ষী হয়েছিল বিদেশের।
তাই আর বিদেশী অর্থনীতির অনুকরণ নয়, বরং ভারতের এখন গ্রহণ করা উচিত স্বদেশী অর্থনীতি যার সাহায্যে একসময় ভারত অর্থনীতির দিক দিয়ে জগৎ শ্রেষ্ঠ হয়েছিল।
কি এই স্বদেশী অর্থনীতি যার সাহায্যে ভারত অতীতে জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করেছিল?
স্বদেশী অর্থনীতি হচ্ছে অর্থনীতির সেই পথ যে পথে চলে গত আড়াই হাজার বছর ধরে ভারতীয় অর্থনীতি পৌঁছেছিল উন্নতির শিখরে। স্বদেশী অর্থনীতিতে দেশের সামগ্রিক চাহিদা দেশের মানুষের দ্বারাই যাতে পূরিত হয় সে ব্যবস্থা করা হত। এর জন্য দেশের মানুষের চাহিদা কৌশলে নিয়ন্ত্রিতও হত। এছাড়াও দেশের সমস্ত সামাজিক অনুষ্ঠানের উপাসনা পদ্ধতির নিয়ম এমনভাবে গঠিত ছিল যাতে সমাজের সকল পেশার মানুষের কর্মের চাহিদা তৈরি হয় এবং যেসমস্ত বস্তুর উৎপাদন দেশে হত না সেসমস্ত বস্তুর ব্যবহার সমস্ত সামাজিক অনুষ্ঠানে ও উপাসনা পদ্ধতিতে নিষিদ্ধ ছিল। এই চাহিদার জোগান ঘটাতে গিয়ে সমাজের সকল পেশার মানুষের হাতেই এসে যেত কিছু কাজ অর্থাৎ দেশে বেকারত্ব বলে কিছু থাকতো না। এছাড়াও দেশের সামগ্রিক চাহিদা দেশেই পূরিত হওয়ায় অর্থাৎ বিদেশে উৎপাদিত বস্তু আমদানি করতে না হওয়ায় দেশের অর্থ বিদেশে যেত না। বরং হস্তশিল্প ও অন্যান্য নানান বস্তু রপ্তানি করার মাধ্যমে বিদেশের সম্পদ। স্বর্ণরূপে ভারতে আসতো। ‘বঙ্গের মসলিন, বোগদাদ, রোম, চীন। কাঞ্চন তৌলেই কিনতেন একদিন।
স্বদেশী অর্থনীতি ভারতীয় অর্থনতিকে অতীতে কিভাবে সমৃদ্ধ করেছিল তা জানতে হলে একটু ফিরে তাকাতে হবে ভারতবর্ষের দুহাজার বছরের অর্থনৈতিক ইতিহাসের দিকে।
২৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সমগ্র বিশ্বের অর্থনীতির চল্লিশ শতাংশ ছিল ভারতের দখলে। এই অবস্থা চলেছিল প্রায় ১০০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। মনে রাখা দরকার আলোচ্য সময়কালে আলেকজান্ডারের গ্রীস সাম্রাজ্য তার দ্রুত উত্থান ও পতন সহকারে বিশ্ব ইতিহাসে জায়গা করে নিয়েছে, প্রায় চারশ বছর ধরে দাপটের সঙ্গে ইউরোপ শাসন করেছে রোম, আরব সাম্রাজ্যে তার আগ্রাসী অস্তিত্ত্বের দ্বারা কম্পিত করেছে এশিয়া ও ইউরোপের এক বড় অংশকে, তবু অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ভারতের সঙ্গে পেরে ওঠেনি কেউ। ভারত কিন্তু নিজ দেশের বাইরে কোনও দেশ দখল করেনি, কোনও সাম্রাজ্য স্থাপন করেনি বরং নিজ দেশের বাইরে থেকে আসা গ্রীক, শক, হূণ, কুশান আরব প্রভৃতি একের পর এক আক্রমণকারীকে প্রতিরোধ করেছে ক্রমাগত আর পারসিক ইহুদি প্রভৃতি আশ্রয়প্রার্থীদের আশ্রয় দিয়েছে পরম যতনে। ১০০০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ভারত তীব্রভাবে আক্রান্ত, পরাভূত এবং লুণ্ঠিত হয় মামুদের দ্বারা। ভারতের অর্থনীতিতে এর কিছুটা হলেও প্রভাব পড়ে, সেজন্য দেখা যায় এই সময় থেকে বিশ্ব অর্থনীতিতে ভারতের অবদান চল্লিশ শতাংশ থেকে তিরিশ শতাংশে নেমে আসছে অধিকারী হচ্ছে। তা সত্বেও তখনও কিন্তু ভারত বিশ্বের অন্য দেশসমূহের তুলনায় তখনও অর্থনীতিতে অনেক এগিয়ে ছিল, বাকি কোনও দেশই তখনকার বিশ্ব অর্থনীতির তিরিশ শতাংশের অধিকারী ছিল না। এরকম অবস্থায় কাটে আরও দু’শতক। এরপর আসে আরও ভয়ংকর অবস্থা, ভারত পরাধীন হয় তুকী আক্রমণকারীদের দ্বারা। পরাধীনতার স্বাভাবিক নিয়মেই আমাদের দেশ তখন প্রবল অর্থনৈতিক শোষণের শিকার হয়। ফলস্বরূপ ভারতের অর্থনীতি গোটা বিশ্বের অর্থনীতিতে মাত্র কুড়ি শতাংশ অবদান রাখতে সক্ষম হয়। তবুও ভারত বিশ্বের অন্য দেশসমূহের তুলনায় তখনও অর্থনীতিতে অনেক এগিয়ে ছিল, বাকি কোনও দেশই এককভাবে তখনকার বিশ্ব অর্থনীতির কুড়ি শতাংশের অধিকারী ছিল না। এমনকি ভারত যাদের হাতে পরাধীন ছিল সেই তুর্কীদের নিজেদের দেশ তুর্কিস্থানও তখন অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ভারতের তুলনায় পশ্চাৎপদ ছিল। দাস বংশ থেকে মোগল বংশ তুর্কীদের অধীনে ভারত ছিল প্রায় সাড়ে পাঁচশো বছর। এই কালখণ্ডে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা ঐ কুড়ি শতাংশের আশেপাশেই আটকে ছিল। এরপর এর ভারতীয় অর্থনীতির পক্ষে সবচেয়ে কালো দিন, যখন ব্রিটিশ শক্তির অধীন হল। পলাশীর প্রান্তরে যখন ক্লাইভের খঞ্জর লাল হয়েছিল তখনও বিশ্ব অর্থনীতিতে ভারতের অবদান কুড়ির নীচে নামেনি আর ১৯৪৭-এ ব্রিটিশ যখন ভারত থেকে বিতাড়িত হল তখন বিশ্ব অর্থনীতিতে ভারতের অবদান মাত্র দুশতাংশ। স্বাধীনতার সাত দশক পর আজ বিশ্ব অর্থনীতিতে ভারতের অবদান মাত্র পাঁচ শতাংশ।
এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য দেশকে আবার সেই বৈভব ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য তাই আজ চাই সেই স্বদেশী অর্থনীতির পথে ফিরে যাওয়া।
স্বদেশী অর্থনীতির সঙ্গে বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত সমস্ত রকম অর্থনীতির কি পার্থক্য একটু বিশ্লেষণে দেখা যাক।
বর্তমানে যে কোন অর্থনীতিতে, যে কোন একটি বস্তুর উৎপাদন, একেকটি ক্ষেত্রে হয়ে থাকে ব্যাপকভাবে কিন্তু অন্য কোনও বস্তুর উৎপাদন সেই ক্ষেত্রে একেবারেই হয় না। ধরা যাক এক জায়গায় ধান চাষ হচ্ছে, সেখানে খালি ধানই চাষ হচ্ছে, এক জায়গায় আখ চাষ হচ্ছে সেখানে খালি আখেরই চাষ হচ্ছে, চাষের মাধ্যমে উৎপাদিত হওয়া এসব সামগ্রী সারাদেশে পরিবহনের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ছে। বণিকদের কাছে চাষিরা নিজেদের উৎপাদিত সামগ্রী সম্পূর্ণ বিক্রি করে দিচ্ছে। বিক্রয়লব্ধ অর্থ দিয়ে নিজেদের প্রয়োজনীয় জিনিস বণিকের কাছ থেকে কিনছে, জিনিসগুলি আবার সারা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন জায়গায় আলাদা আলাদাভাবে উৎপাদিত হচ্ছে, সেখানকার চাষীরাও তাদের উৎপাদন বণিকদের কাছে বিক্রি করে দিচ্ছে। অর্থনীতির এই বিশেষ পরিকাঠামোয় একটি জিনিসের উৎপাদক অপরাপর জিনিসের উৎপাদন খরচ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয়। তাই অপরাপর জিনিসের বিনিময় মূল্য সম্পর্কেও সে অবহিত নয় তাই নিজেদের প্রয়োজনীয় যে সব জিনিস সে বণিকের কাছ থেকে কিনছে সেই সব জিনিসের মূল্য হিসেবে সে বণিকের দ্বারা কথিত দাম প্রদান করছে। আবার তার দ্বারা উৎপাদিত জিনিসের দাম হিসেবে বণিক অন্য জায়গার উপভোক্তাদের থেকে কত টাকা নিচ্ছে তাও সে জানে না তাই বণিকের কথিত দামেই সে বণিকের কাছে তার নিজের উৎপাদন বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক, যেখানে ধান উৎপাদন হচ্ছে সেখানকার ধান চাষীরা জানে না যে এই ধানের বাজারদর কত, ধানের ক্রেতার কাছে সে নিজে সরাসরি পৌঁছতেও পারছে
ফলে বণিকের কথিত দামেই সে বণিকের কাছে তার নিজের উৎপাদিত ধান বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে। আবার নিজের প্রয়োজনীয় যে বস্তু বা আখজাত চিনি সে বণিকের কাছ থেকে কিনছে সেই সব বস্ত্র বা আখের উৎপাদন খরচ সে জানে না, সেই সব বস্ত্র বা আখের উৎপাদকের কাছে সে নিজে সরাসরি পৌঁছতেও পারছে না ফলে বস্ত্র বা আখের মূল্যের হিসেবের ব্যাপারে পুরোপুরি বণিকের উপর নির্ভরশীল থাকছে, এর ফলে বণিকরা উৎপাদকের কাছ থেকে কম দামে জিনিস ক্রয় করে সেই একই জিনিস উপভোক্তাদের কাছে বেশী দামে বিক্রি করে অর্থনৈতিক শোষণ চালানোর সুযোগ পেয়ে যাচ্ছে। বর্তমান পৃথিবীর সমস্ত অর্থনীতির ধারা এই শোষণের পদ্ধতির তারতম্যের ওপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে। যখন এই শোষণ করার সুযোগ কোনও বড় বণিকের একচেটিয়া অধিকারে এসে যায় তখন বর্তমান পৃথিবীর অর্থনীতির পরিভাষা অনুযায়ী সেই পরিস্থিতিকে বলা হয় “একচেটিয়া বাজার অর্থনীতি বা মনোপলি মার্কেট ইকনমিক্স”, আবার যখন এই শোষণ করার সুযোগ একাধিক বড় বণিকের মিলিত একচেটিয়া অধিকারে এসে যায় তখন পৃথিবীর অর্থনীতির পরিভাষা অনুযায়ী সেই পরিস্থিতিকে বলা হয় “অলিগোপলি মার্কেট ইকনমিক্স”, আবার যখন এই শোষণ করার সুযোগ কোনও এক একাধিক বড় বণিকের একক বা মিলিত একচেটিয়া অধিকারে না থেকে যে কোনও বণিকের আয়ত্বের মধ্যে থাকে তখন বর্তমান পৃথিবীর অর্থনীতির পরিভাষা অনুযায়ী সেই পরিস্থিতিকে বলা হয় “বিশুদ্ধ প্রতিযোগিতা-নির্ভর বাজার অর্থনীতি বা পিওর কম্পিটিটিভ মার্কেট ইকনমিক্স”, আবার যখন এই শোষণ করার সুযোগ বণিকের অধিকারে না থেকে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে থাকে তখন বর্তমান পৃথিবীর অর্থনীতির পরিভাষা অনুযায়ী সেই পরিস্থিতিকে বলা হয় “সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি বা সোশ্যালিস্ট বা কমিউনিস্ট ইকনমিক্স”, এই “সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি বা সোশ্যালিস্ট বা কমিউনিস্ট ইকনমিক্স”রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে থাকছে, উৎপাদিত সামগ্রীর দামও রাষ্ট্র ঠিক করে দিচ্ছে। তা বলে অর্থনীতির এই বিশেষ ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক শোষণ হয় না তা নয়। শুধু শোষকের পরিবর্তন হয়, বণিকের বদলে রাষ্ট্র অর্থাৎ রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রক রাজনীতিবিদ বা আমলারা শোষকের ভূমিকা গ্রহণ করে। “বিশুদ্ধ প্রতিযোগিতা-নির্ভর বাজার অর্থনীতি বা পিওর কম্পিটিটিভ মার্কেট ইকনমিক্স”-এ প্রচুর সংখ্যক বণিক বা শোষক থাকায় এই শোষণ তুলনায় কম হয় কারণ নিজেদের বাজারের পরিধি বিস্তারের লক্ষ্যে প্রত্যেক বণিকই নিজেকে উপভোক্তাদের কাছে আকর্ষনীয় করে তুলতে চায় ও সেকারণে একক প্রতি লাভ কম রেখেও উপভোক্তাদের কাছে জিনিসের মূল্য কম রাখে। কিন্তু শোষণ তুলনায় কম হলেও এ পদ্ধতিতেও শোষণ একেবারে বন্ধ হয় না কারণ উপভোক্তাদের কাছে নিজেদের আকর্ষণীয় করে তুলতে বণিকরা একক প্রতি লাভ কম রাখলেও লাভ তো একেবারে শূণ্য করে না, যেটুকু বণিকের লাভ সেটুকুই উৎপাদক ও উপভোক্তাদের কাছে শোষণ। তাছাড়া এই “বিশুদ্ধ প্রতিযোগিতা-নির্ভর বাজার অর্থনীতি বা পিওর কম্পিটিটিভ মার্কেট ইকনমিক্স”কোনও অর্থনীতিতে বেশিদিন থাকতে পারে না,
কারণ অপেক্ষাকৃত অল্প শোষণের এই অর্থনীতি বড় বণিকদের শিরঃপীড়ার কারণ হয়, তখন তারা ডাম্পিং পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে ক্রেতাদের সাময়িক সন্তুষ্ট করে ছোটো বণিকদের বাজার থেকে বার করে দিয়ে নিজেরা বাজারের একচেটিয়া অধিকার নিয়ে নেয়, আবার শুরু হয় মনোপলি বা অলিগোপলি অর্থনীতির চেনা ছক। অর্থাৎ শোষণই হল। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী প্রচলিত সমস্ত রকম অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি। তাই শোষণ মুক্ত সমাজ গড়তে গেলে আমাদের তাকাতে হবে সেই স্বদেশী অর্থনীতির দিকেই।
প্রাচীন ভারতের স্বদেশী অর্থনীতি ছিল এর বিপরীত। সম্পূর্ণ অর্থনীতি ছিল কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককে বিভক্ত, সেই একক গুলিকে গ্রাম বলা হতো। প্রত্যেকটি গ্রাম ছিল অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ। একটি গ্রামে বসবাসকারী লোকেদের মধ্যে সব পেশার। লোক থাকত এবং তারা বিভিন্ন রকমের জিনিস উৎপাদন করত যে জিনিসগুলি গ্রামের মানুষের সামগ্রিক চাহিদা মেটানোর কাজে লাগতো। একজনের উৎপাদন অন্যজনের উৎপাদনের সঙ্গে বিনিময় প্রথার মাধ্যমে বা হয়তো মুদ্রার মাধ্যমে সরাসরি হাতবদল হত। অর্থাৎ একই গ্রামে একজন ধান চাষ করলেন, একজন বস্ত্র উৎপাদক বস্ত্র উৎপাদন করলেন, উৎপাদিত সামগ্রীর সরাসরি পারস্পরিক বিনিময় হলো। উৎপাদক সরাসরি উপভোক্তাদের কাছে উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রি করতেন। উপভোক্তা সরাসরি উৎপাদকদের কাছ থেকেই। তার প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় করতেন। ধান উৎপাদক বস্ত্র ও আখের উপভোক্তা হতেন, আখ উৎপাদক বস্ত্র ও ধানের উপভোক্তা হতেন, বস্ত্র উৎপাদক ধান ও আখের উপভোক্তা হতেন। উৎপাদক এবং উপভোক্তা কাছাকাছি অবস্থান করতেন, পরস্পরের উৎপাদন খরচ জানতেন, সরাসরি পারস্পরিক ক্রয়-বিক্রয় হত, সেজন্য জিনিসের ক্রয়-বিক্রয়, চাহিদা ও জোগানের নিয়ন্ত্রণ, উৎপাদিত সামগ্রীর দামের ওপর বাজারের, মধ্যস্বত্বভোগী বণিকের অথবা রাষ্ট্রের কোনও ভূমিকাই ছিল না। সেকারণেই সেই অর্থনীতিতে বণিকের অথবা রাষ্ট্রের কোনও শোষণ ছিল না। বর্তমানে যে কোন অর্থনৈতিক পরিকাঠামোতে যে শোষণ সহজেই পরিলক্ষিত হয়। যে কোনো ধরনের অর্থনৈতিক বৈষম্যের মূল কারণ এই। শোষণ। প্রকৃতপক্ষে উৎপাদক এবং উপভোক্তার মধ্যে দূরত্ব বৃদ্ধি করে এই অর্থনৈতিক শোষণ বৃদ্ধির রাষ্ট্র বা বণিককৃত প্রচেষ্টা প্রায়শঃই পরিলক্ষিত হয়। একটি উদাহরণ দেখা যাক, কলকাতা শহরে আগে খাটাল ছিল, ক্রমবর্ধমান জনঘনত্বের চাপে প্রপীড়িত বিপুল সংখ্যক কলকাতাবাসী এই খাটালগুলি থেকে দুধ কিনে তাদের দৈনিক দুধের বিপুল চাহিদা মেটাতো। উৎপাদক এবং উপভোক্তা কাছাকাছি অবস্থান করতো। উৎপাদক সরাসরি উপভোক্তাদের কাছে উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রি করতো। উপভোক্তা সরাসরি উৎপাদকদের। কাছ থেকেই তার প্রয়োজনীয় সমগ্রী ক্রয় করতো। ফলতঃ, কোনরকম অর্থনৈতিক শোষণ পরিলক্ষিত হত না। প্রায় তিনদশক আগে আকস্মিকভাবে তৎকালীন রাজ্য সরকার পরিবেশ দূষণের অজুহাতে কলকাতা শহরে খাটাল রাখা নিষিদ্ধ করে দিল। খাটালগুলি শহর থেকে অনেক দূরে চলে গেল, কলকাতাবাসী তাদের দৈনিক দুধের বিপুল চাহিদা মেটানোর জন্য দুগ্ধব্যবসায়ী বণিকের মুখাপেক্ষী হল। দুধের দাম বাড়লো, অর্থনৈতিক শোষণ চালু হল। খাটালের চেয়ে অনেক বেশী দূষণ সৃষ্টিকারী তৈলব্যবহারকারী যন্ত্রচালিত গাড়ি কিন্তু কলকাতা শহরে নিষিদ্ধ হয়নি, তবে হ্যা, তজ্জনিত দূষণ কমাবার জন্য নানান নিয়মতান্ত্রিক সংস্কার সাধিত হয়েছে। খাটালের ক্ষেত্রেও নিষিদ্ধ না করে নিয়মতান্ত্রিক সংস্কার সাধিত করে দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারতো, কিন্তু বণিকের মানদণ্ড যে আজ প্রকৃতপক্ষে রাজদণ্ডকে নিয়ন্ত্রণ করছে তাই বণিকের অর্থনৈতিক শোষণ করার উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করার কাজেই সে নিয়োজিত হল। এটি বণিকের অর্থনৈতিক শোষণের একটি ক্ষুদ্র উদাহরণ কিন্তু এই একই পদ্ধতিতে অনেক বড় অর্থনৈতিক শোষণ করে চলেছে বণিককূল বিশেষতঃ বিদেশী বণিককুল এবং সেই শোষণ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার করে নয় বরং হচ্ছে বিজ্ঞাপন ও প্রচার মাধ্যমের ঢক্কানিনাদের দ্বারা। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় ডাবের জল আর আখের রস খাওয়া গ্রীষ্মপ্রধান আমাদের দেশের জনসাধারণের চিরন্তন অভ্যাস ছিল। এক্ষেত্রেও উৎপাদক এবং উপভোক্তা কাছাকাছি অবস্থান করতো। উৎপাদক সরাসরি উপভোক্তাদের কাছে উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রি করতো। ফলস্বরূপ এখানেও কোনরকম অর্থনৈতিক শোষণ পরিলক্ষিত হত না। কিন্তু বিজ্ঞাপন ও প্রচার মাধ্যমের অমোঘ ঢক্কানিনাদের ফলস্বরূপ ডাবের জল আর আখের রসকে নির্বাসন দিয়ে ঠাণ্ডা পানীয়ের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে সকলে, উৎপাদক এবং উপভোক্তা পরস্পরের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, লাভ বাড়ছে মধ্যস্বত্বভোগী বণিকের। এক্ষেত্রে অবশ্য বণিক নিজেই উৎপাদক এবং উপভোক্তার থেকে বহু দূরে অবস্থানকারী। তাই অর্থনৈতিক শোষণ এখানে অনেক তীব্র। স্বদেশী অর্থনীতির বর্ণিত পথ থেকে সরে যাওয়ার ফলেই সৃষ্টি হয়েছে এই শোষণ। এই সংক্রান্ত আরেকটি ক্ষেত্রে স্বদেশী অর্থনীতির সঙ্গে বর্তমান অর্থনীতির পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এতক্ষণ ধরে বর্ণিত প্রয়োজনীয় সামগ্রী ছাড়াও উপভোক্তারা নানান বিলাসদ্রব্য বা শখসামগ্রী ক্রয় করে। এই বিলাসদ্রব্য বা শখসামগ্রী ক্রয়ের ক্ষেত্রে উপভোক্তাদের কোনও নির্দিষ্ট বাধ্যবাধকতা থাকে না। নিজেদের ইচ্ছেমত তারা এই বিলাসদ্রব্য বা শখসামগ্রী ক্রয় করে। বর্তমানকালে এই ইচ্ছে বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হয়। ফলস্বরূপ বিজ্ঞাপনদাতা বড় বণিকরা লাভবান হয় অর্থাৎ অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধি পায়। প্রাচীনকালে স্বদেশী অর্থনীতিতে এই ইচ্ছে সামাজিক ও ধর্মীয় নানান অনুশাসন ও নীতি দ্বারা প্রভাবিত হত। সামাজিক ও ধর্মীয় নানান অনুশাসন ও নীতিগুলিও এমন হত যা মানুষের ক্রয় করার ইচ্ছেকে এমন বস্তুসমূহের অভিমুখে চালিত করতো যে বস্তুসমূহের উৎপাদক সমাজের সব স্তরের সাধারণ মানুষ হত। ফলে সমাজের সব স্তরের সাধারণ মানুষের কর্মসংস্থান হত, ফলস্বরূপ অর্থনৈতিক বৈষম্য কম হত এবং সমাজে প্রকৃতপক্ষে অর্থনৈতিক সাম্য বজায় থাকতো। উদাহরণস্বরূপ দেখা যাক, স্বদেশী অর্থনীতি বর্ণিত পথে চালিত হওয়া আমাদের দেশের বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসবগুলিতে কর্মপদ্ধতি বা আচারপদ্ধতি এবং প্রয়োজনীয় বস্তু সামগ্রীর নির্বাচন এমনভাবে হতো যাতে স্থানীয় সমস্ত মানুষ কর্ম সংস্থানের সুযোগ পেতেন। যেমন দুর্গাপূজা, এর কর্মপদ্ধতি ও আচারপদ্ধতি এবং প্রয়োজনীয় বস্তু সামগ্রীর তালিকা দেখলেই বোঝা যাবে যে সেই বস্তুগুলির জোগান দিতে দিতে গিয়ে গ্রাম বাংলার প্রায় সব মানুষের কর্মসংস্থান হয়ে যেত। দুর্গাপূজা ও অন্যান্য ধর্মীয় বা সামাজিক উৎসবগুলিতে মূলতঃ ধনী ব্যক্তিরাই অর্থ ব্যয় করতেন এবং এই অর্থ ব্যয় তাদের সামাজিক কৌলিন্যের মাপকাঠি ছিল। কে কত অর্থ ব্যয় করতে পারেন তার ওপর নির্ভর করত কার মর্যাদা কত। আবার এই অর্থ ব্যয় করতে গিয়েই উপরিউক্ত পদ্ধতিতে সকলের কর্মসংস্থানও হয়ে যেত। এর পাশাপাশি দেখা যাক বর্তমান অর্থনীতিতে বিজ্ঞাপন দ্বারা চালিত বর্তমান ধনী সমাজের ব্যয়ের তালিকাকে। সেই তালিকায় সেই বস্তুগুলিই স্থান পেয়েছে যে বস্তুগুলি বিজ্ঞাপনদাতা বহুজাতিক কোম্পানীগুলি বিজ্ঞাপিত করেছিল এবং সেই বস্তুগুলি উৎপন্ন হয় সেই বহুজাতিক কোম্পানীগুলিরই আয়ত্বাধীন স্বয়ংক্রিয় কারখানাগুলিতে। অর্থাৎ অর্থ ব্যয় আগেকার কালের মত একই প্রকারের হল কিন্তু কর্ম সংস্থানের সৃষ্টি হল না। এখানেই স্বদেশী অর্থনীতির সঙ্গে বর্তমানকালে প্রচলিত সমস্ত অর্থনীতির পার্থক্য।
আজ স্বাধীনতার পুণ্যলগ্নে দেশের নীতি নির্ধারকদের কাছে একটাই প্রার্থনা বামপথে বা ডানপথে না হেঁটে একটু সোজাপথে হাঁটুন। সমাজতান্ত্রিক বা ধনতান্ত্রিক উভয় প্রকার অর্থনীতির পথ পরিত্যাগ করে যে অর্থনীতির ওপর ভিত্তি করে ভারত পরাধীনতার আগে দু’সহস্রাব্দ ধরে বিশ্বের সমৃদ্ধতম দেশ হিসেবে পরিগণিত ছিল সেই স্বদেশী অর্থনীতিকে গ্রহণ করুন তবেই অর্থনৈতিকভাবে “ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।”
জনসাধারণের দায়িত্ব :
ভারতবিরোধী সব কাজই চীন, পাকিস্তান এবং পাশ্চাত্যের দেশগুলি করছে এবং করবে আমাদের দেশে বিক্রিত বিদেশী পণ্যের মূল্যবাবদ প্রাপ্ত অর্থ থেকেই, তাই জনসাধারণ যদি বিদেশের পণ্য না কেনেন অর্থাৎ বিদেশের পণ্য বয়কট করেন তাহলে বিদেশীরা অর্থাভাবে ভারতবিরোধী কাজ করা থেকে বিরত থাকবে।
মনে হতে পারে এতবড় আন্তর্জাতিক শক্তি আমাদের দেশের ওপর আগ্রাসন চালাচ্ছে। শুধুমাত্র বয়কটকে অস্ত্র করে আমরা সাধারণ মানুষ কি পারবো এত বড় এক শক্তির সঙ্গে লড়াই করতে?
প্রমাণ ইতিহাসে :
করা যে যায় তার প্রমাণ পাওয়া যাবে ইতিহাসের দিকে একটু তাকালেই, মহাকালের সরণী ধরে পেছিয়ে যেতে হবে ১১৩টি বছর, ১৯০৫ সাল, ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করলো বঙ্গভঙ্গ-র, বললো, বঙ্গভঙ্গ একটি “SETTLED FACT” (স্থিরীকৃত সিদ্ধান্ত)। ভেবে দেখা যাক সেই সময়কার কথা, সেই ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে তখন সূর্য অস্ত যায় না। চেঙ্গিস খান, আলেকজান্ডার, তৈমুর লং এবং জুলিয়াস সিজারের সাম্রাজ্যকে যোগ করলে যে আয়তন হবে তার চেয়েও বড় আয়তন তখনকার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আর ভারত সেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীন একটি দেশ মাত্র, সৈন্যবলে অর্থবলে অস্ত্রবলে ব্রিটিশ শক্তি তখন অজেয়। ভারতবাসী তখন অর্থাভাবে দরিদ্র, অস্ত্র রাখার অনুমতিহীন। সেই শক্তিশালী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একটি “SETTLED FACT” (স্থিরীকৃত সিদ্ধান্ত) বঙ্গভঙ্গকে তৎকালীন দরিদ্র ভারতবাসী “UNSETTLED” করে দিয়েছিল শুধুমাত্র ব্রিটিশ পণ্য বয়কট করার মাধ্যমে। শুধুমাত্র ভারতীয়রা ব্রিটিশ পণ্য বয়কট করতে শুরু করতেই টনক নড়েছিল ব্রিটিশ সরকারের, বাধ্য হয়েছিল তারা পশ্চাদপসরণ করতে, বঙ্গভঙ্গ প্রত্যাহৃত হয়েছিল। সেদিন দরিদ্র পরাধীন অস্ত্রহীন ভারতবাসী যা করতে পেরেছিল আজ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বিশ্বের ষষ্ঠ এবং সামরিক শক্তির দিক দিয়ে বিশ্বের চতুর্থ শক্তিধর দেশের নাগরিক ভারতবাসী কি তা করতে পারবো না? অবশ্যই পারবো যদি সেদিনের মত আজও আমরা মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নিতে পারি।
অন্যান্য প্রশ্ন :
অর্থনীতির একটি ভিন্ন প্রশ্ন এখানে অনেক সময়ই উঠে আসছে, আমরা বিদেশী পণ্য বয়কট করলে বিদেশীরাও যদি আমাদের পণ্য বয়কট করে, সেক্ষেত্রেও তো আমাদের দেশের অর্থনীতি এবং কর্মসংস্থানের ক্ষতি হবে? এপ্রসঙ্গে একটা কথা বলা যাক, আমাদের দেশ থেকে বিদেশে নির্মিত ভোগ্যপণ্য রপ্তানি হয় না শুধুমাত্র কাঁচামাল এবং উৎপাদন বৃদ্ধিতে কাজে লাগে এমন জিনিস (যেমন-সফটওয়্যার, যন্ত্রাংশ) রপ্তানি হয়। নিজেদের শিল্পোৎপাদন বজায় রাখার জন্যই তারা কাঁচামালের আমদানি বন্ধ করতে পারবে না।
কারও কারও মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, বিদেশী জিনিস ব্যবহার করা যদি দেশের পক্ষে এতই ক্ষতিকর তাহলে সরকার বিদেশী জিনিস ব্যবহার আইন করে বন্ধ করে দিচ্ছে না কেন? বর্তমানে বিশ্বায়নের পৃথিবীতে আন্তর্জাতিক নিয়মানুসারে কোনও দেশই কিন্তু বিদেশের সব পণ্য বিক্রি আইনতঃ নিষিদ্ধ করতে পারে না। ভারত বিদেশের সামগ্রী বিক্রি নিষিদ্ধ না করতে পারলেও কোনও বস্তু কেনা বা না কেনা তো সম্পূর্ণ ক্রেতার হাতে। বিদেশী পণ্যে ভারতীয় বাজার ছেয়ে গেলেও বিদেশী পণ্য কিনবো কি কিনবো না সেই সিদ্ধান্ত তো সম্পূর্ণরূপে ক্রেতার নিজের। ক্রেতারা যদি বিদেশী পণ্য না কেনেন, তাহলে বিশ্বায়ন সংক্রান্ত আইনসমূহও বিদেশের পণ্যকে ভারতের বাজার দখল করার সুযোগ দিতে পারবে না। তবে ভারতের বাজার দখলে চীন যে ডাম্পিং-নীতির সাহা
য্য নিচ্ছে তাও বিশ্বায়নের আইন বিরোধী এবং ডাম্পিং প্রতিরোধে ভারত সরকার চীনের বেশ কিছু পণ্যের ওপর ডাম্পিং-বিরোধী শুল্ক বা অ্যান্টি ডাম্পিং ডিউটি বসিয়েছে, অর্থাৎ এ কথা বলা যায় যে সরকারের কাজ সরকার করেছে, এবার জনসাধারণকে জনসাধারণের কাজ করতে হবে, চিনা পণ্যকে সর্বাত্মক ভাবে বয়কট করতে হবে, এখানে আরও একটি কথা স্মর্তব্য, জনসাধারণ জাগ্রত থাকলে সরকারও সচেতন থাকবে এবং চীনের ও অন্যান্য বিদেশী দ্রব্যের বিরুদ্ধে যেখানে সম্ভব সেখানে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণে কখনও দুর্বলতা দেখাবে না।
প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকার হাতে আণবিক বোমায় বিধ্বস্ত হওয়ার পর জাপান বাধ্য হয়ে আমেরিকার অধীনতা স্বীকার করে, আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করে। তৎকালীন বিশ্বের সবচেয়ে ধনী এবং শিল্পের দিক দিয়ে সবচেয়ে উন্নত দেশ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র তার উৎপাদিত পণ্যের জোয়ারে ভাসিয়ে দিয়েছিল জাপানের বাজার। বোমাবিধ্বস্ত, শিল্পহীন তৎকালীন জাপান সরকার আইনগত বাধ্যতার কারণে তার কোনও প্রতিবাদ করেনি, কিন্তু জাপানের দেশপ্রেমিক নাগরিকেরা মার্কিন পণ্যকে সম্পূর্ণ বয়কট করেছিল, মার্কিন পণ্য জাপানের বাজারে পড়ে পড়ে নষ্ট হয়েছিল। ক্যালিফোর্নিয়ার আপেল, যা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আপেল, তা জাপানের বাজারে পড়ে পড়ে পচেছিল, মার্কিন আপেল বিক্রেতারা প্রথমে সস্তা দরে পরে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সেই আপেল বিলি করতে শুরু করেছিল, আপেলপ্রিয় জাপানীরা সেদিকে ফিরেও তাকায়নি, তারা বিনামূল্যের ক্যালিফোর্নিয়ার আপেল খেয়ে নিজেদের দেশের তুলনামূলক নিম্নমানের আপেল কিনে খেয়েছে, যাতে নিজেদের দেশের আপেল উৎপাদনকারীদের বিক্রি বজায় থাকে এবং তাদের উপার্জন বন্ধ না হয়। দেশের প্রতি এই নিঃস্বার্থ ভালোবাসা এবং কর্তব্যবোেধ ছিল বলেই জাপান আজ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ অর্থনীতি-সম্পন্ন দেশ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। আমরাও যদি তাদের মত দেশপ্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে পারি তবেই “ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে”।
আরও একটি বিষয় এখন বাংলা সংবাদপত্রগুলিতে বহুল আলোচিত, সেটা হল চীন বা অন্যান্য পাশ্চাত্যের দেশের সঙ্গে অর্থনৈতিক সংঘাতে গেলে যদি ভারত বিপন্ন হয়। ঐ দেশগুলি অত্যন্ত শক্তিশালী তারা যদি তাদের মিত্র দেশগুলিকে নিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে একটি অর্থনৈতিক প্রাচীর নির্মাণ করে? তারা যদি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতকে একঘরে করে ফেলে? এমনতর নানান দুশ্চিন্তায় আকীর্ণ ভারতীয় বুদ্ধিজীবীকুল আর তাদের এই চিন্তা স্বাভাবিকভাবেই প্রভাবিত ও ভীত করেছে সাধারণ মানুষকে, এ প্রসঙ্গে একটা কথাই বলা যায়, ১৯৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারত যখন পোখরানে পরীক্ষামূলক পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল তখন আমেরিকা ভারতকে অর্থনৈতিকভাবে বয়কট করেছিল, নিজের মিত্র দেশগুলিকে নিয়ে ভারতের ওপর অর্থনৈতিক অবরোধ জারি করেছিল, তাতে কিন্তু ভারতবর্ষের অর্থনীতিতে কোনও প্রভাব পড়েনি, বরং মার্কিন অর্থনীতিই বিপন্ন হয়েছিল ভারতীয় বাজারে প্রবেশাধিকার হারিয়ে, অবশেষে তারা বাধ্য হয়েছিল ভারতের বিরুদ্ধে জারি করা অর্থনৈতিক অবরোধ তুলে নিতে। সেদিনের আমেরিকার মতো আজকের চীনও ভারতের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ জারি করলে নিজেরাই অপদস্থ হবে, ভারতের ওপর কোনও প্রভাব পড়বে না, কারণ খাদ্য ও অর্থনীতির অন্যান্য প্রাথমিক বিষয়গুলিতে। ভারত স্বয়ম্ভর, তাই ভারতীয়দের নির্ভীক হয়ে চীনের পণ্যকে বয়কট করা উচিত।
ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সুদীর্ঘ সংগ্রামের পর আমাদের ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছিল স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মহান আত্মত্যাগের দ্বারা। আজ দেশের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বিপন্ন, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উত্তরসূরী হিসেবে সেই অর্থনৈতিক স্বাধীনতা রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের, তারা অনেক আত্মত্যাগের বিনিময়ে যে স্বাধীনতা অর্জন করেছিলেন, চিনা, আমেরিকান ও অন্যান্য বিদেশী পণ্য বয়কট করার মাধ্যমে আমরা কি পারবো না সেই স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে?
অম্লানকুসুম ঘোষ