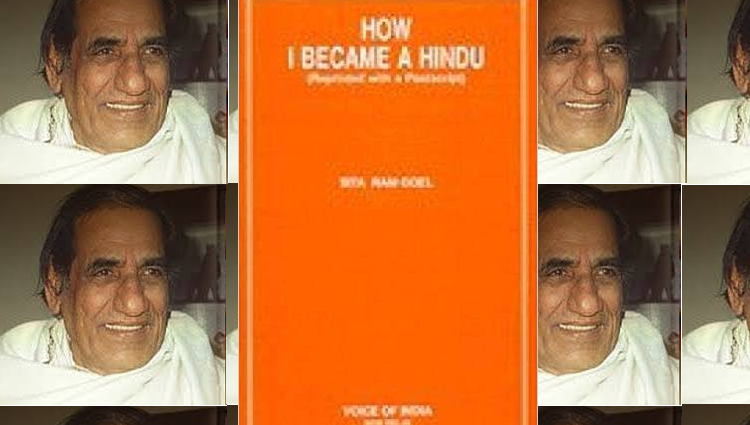(প্রথম অধ্যায়ের পর)
দুই
গান্ধীবাদ থেকে কমিউনিজম পর্যন্ত
ঐ একই সময়ে আমি অল্প কিছুদিনের জন্য জৈনদের স্থাণকবাসী শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের সংস্পর্শেও এসেছিলাম। আমি যে বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম তা ছিল শ্বেতাম্বর জৈনদের দ্বারা পরিচালিত একটি প্রতিষ্ঠান। সে সময় যে আত্মীয়ের বাড়িতে আমি থাকতাম, তিনিও ছিলেন জৈন। ঐ বিদ্যালয়ে জৈন ধর্মের মূলতত্ত্বগুলি শিক্ষা দেবার জন্য প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময় বাঁধা ছিল। কিন্তু যে জৈন সম্প্রদায়টিকে আমি খুব কাছ থেকে দেখবার সুযোগ পেয়েছিলাম তা আমার চোখে অত্যন্ত অবক্ষয়প্রাপ্ত, আত্মস্বার্থসর্বস্ব, এবং নীরস ঠেকেছিল। ওখানকার স্থাণকগুলিতে (জৈন সাধুদের আশ্রমবিশেষ) কয়েকজন জৈন সাধুর দেওয়া যেসব বক্তৃতা আমি শুনেছিলাম সেগুলির বক্তব্য হ’ত সংকীর্ণমনা এবং সাম্প্রদায়িক প্রকৃতির, এবং আমার কাছে ঐ বক্তব্যগুলি অর্থহীন ঠেকত। শ্রীকৃষ্ণের জৈন সংস্করণটি আমার পক্ষে সবচেয়ে পীড়াদায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ওঁকে এরা একটি ধূর্ত চরিত্র হিসেবে উপস্থাপিত করত। আমাকে শুনতে হ’ত যে তাঁর প্ররোচনায় যেসব প্রাণহানি ঘটেছিল সেইগুলির কারণে শ্রীকৃষ্ণ নরকের পঞ্চম ধাপে অধঃপতিত হয়েছেন, এবং তিনি নাকি এখনো সেখানে আবদ্ধ রয়েছেন। ভগবান মহাবীর এবং জৈন পরম্পরাকে বুঝে উঠতে আমায় এরপর বহু বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল; এবং তা সম্ভব হয়েছিল বুদ্ধ এবং বৌদ্ধ পরম্পরাকে জানার সুবাদে। আমি জানতে পেরেছিলাম যে এঁরা উভয়েই হিমালয়সদৃশ আধ্যাত্মিক উচ্চতার শিখরে বিচরণ করতেন।
একদিন আমার এক বন্ধু তথা সহপাঠী আমায় রম্যাঁ রলাঁ রচিত শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস এবং স্বামী বিবেকানন্দের জীবনীগ্রন্থগুলি পড়তে দেয়। ঐ বইগুলি প’ড়ে আমি অভিভূত হয়ে পড়ি এবং বেদান্তদর্শনের প্রতি তীব্র আকর্ষণ বোধ করতে আরম্ভ করি। দিল্লীর যে গ্রন্থাগারটিতে আমি প্রায়শই ঢুঁ মারতাম সেখানে স্বামী বিবেকানন্দ এবং স্বামী রাম তীর্থের সম্পূর্ণ রচনাবলী পেয়ে গেলাম, দুটিই আট খণ্ডে সম্পূর্ণ। আমি এর সবগুলি পড়ে ফেললাম। কিন্তু যা উদ্ধার করতে পারলাম তা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। আসলে তখন যে ভুলটা আমি করেছিলাম তা হচ্ছে এই : যোগীর চেতনা, যা কেবল একাই পারে বেদান্তের সত্যগুলিকে প্রত্যক্ষ করতে, সেই চেতনাকে আমি নেহাত মননের বিষয় অথবা বড়জোর বিশেষ কোনো একখানি বৌদ্ধিক অবস্থান অবলম্বনের বিষয় বলে ধ’রে নিয়েছিলাম। এর বহু বছর বাদে ফের রামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দ উভয়েই আমাদের সুমহান আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক পরম্পরার মূর্ত প্রতীক রূপে আমার কাছে ফিরে আসবেন।
পুরনো মুদ্রাব্যবস্থার হিসেব অনুযায়ী তখনকার যুগে পাঁচ পয়সার মূল্য আমার কাছে নেহাত কম ছিল না। কিন্তু ফুটপাতের এক পুরনো বই-বিক্রেতার সংগ্রহে থাকা নিউ টেস্টামেন্টের একটি ক্ষুদে সংস্করণের বিনিময়ে ঐ পাঁচ পয়সা হাতছাড়া করতে আমি সানন্দে রাজি হয়ে গিয়েছিলাম। সে সময় আমার জানা ছিল না যে যেকোনো খ্রিস্টান চার্চ অথবা মিশনে গিয়ে স্রেফ চাইলেই আমি ওর চেয়ে অনেক ভালো একখানি সংস্করণ বিনামূল্যে পেয়ে যেতে পারতাম। সে সময় আমি ওরকম কোনো সংস্থার কথা জানতামই না। নিউ টেস্টামেন্টের গসপেল অংশটি আমি তক্ষুনি তক্ষুনি প’ড়ে ফেললাম। বাকিটা আমায় তেমন টানেনি। কিন্তু ক্রুশের উপর বিদ্ধ যীশুখ্রিস্টের সত্তাটি আমায় এতদূর মুগ্ধ করেছিল যে আমি খ্রিস্টের একখানি ছবি কিনে সেটি আমার ছোট্ট এককামরা ঘরের দেওয়ালে মহাত্মা গান্ধী, শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ এবং স্বামী রাম তীর্থের ছবির পাশে টাঙিয়ে ফেললাম। আমার কাছে দ্য সর্মন্ অন দ্য মাউন্ট (পর্বতশীর্ষে দেওয়া উপদেশাবলী) এবং মহাত্মা গান্ধীর বাণী মিলেমিশে একাকার হয়ে উঠল।
প্রায় একই সময়ে আমি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সংস্পর্শেও এসে পড়লাম। ততকাল অব্দি আমার কাছে সম্পূর্ণ অজানা এই সংগঠনের সদস্য ছিল আমার বেশ কয়েকজন সহপাঠী। তারা বিজয়া দশমী উপলক্ষে গান্ধী ময়দানে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে আমাকে যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানাল। সেখানে সকলের সমবেত কসরত অনুশীলন এবং মশালবাহী মিছিল দেখে তো আমি যারপরনাই উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়লাম। কিন্তু শ্রী বসন্তরাও-এর বক্তৃতা শুনে আমি হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। অন্যান্য কথার মাঝখানে তিনি বলেছিলেন : “দুর্বলতা পাপ তথা অপরাধ। বেদে কোনো একটি যজ্ঞে সিংহ বলি দেবার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সিংহ ধরবে কে? তাই তার বদলি হিসেবে ধরা হ’ল বেচারা ছাগলকে। কেন? ছাগল দুর্বল, স্রেফ এই কারণে।” আমি অনেকবারই সুরদাসের বিখ্যাত ভজন “নির্বল কে বল রাম” (দুর্বলের বল হলেন রাম) গানের সঙ্গে গলা মিলিয়েছি। যীশুও বলেছেন যে যারা তুচ্ছ তারাই একদিন পৃথিবী ভোগ করবে। কাজেই এইভাবে দুর্বলকে খাটো করা এবং শক্তিমানকে মহিমান্বিত করা সেই সময় আমাকে প্রবল অস্বস্তিতে ফেলেছিল। বসন্তরাও যে আসলে একটি নির্মম সত্যকে তুলে ধরেছিলেন সেকথা আমি প্রাচীন এবং আধুনিককালের ইতিহাস থেকে বহুতর শিক্ষাগ্রহণ করবার পর তবেই বুঝে উঠতে পেরেছিলাম। দুর্বল হয়ে থাকা সত্যিই পাপ এবং একটি অপরাধও বটে। শক্তিশালী ব্যক্তিই কেবল পারেন ধর্মের জন্য সংগ্রাম করতে এবং ক্ষমা অনুশীলন করতে।
একদিকে যদিও আমার নৈতিক এবং বৌদ্ধিক জগত মহাত্মা গান্ধীর শিক্ষার উপর ভিত্তি ক’রে দৃঢ়ভাবে গ’ড়ে উঠছিল, তবু অন্যদিকে আমার অনুভূতির জগতটি এমন একখানি বৈপ্লবিক পরিবর্তনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল যা আমি আগেভাগে একেবারেই আঁচ করতে পারিনি। এখানে তাড়াতাড়ি বলে রাখি যে এর সঙ্গে কিন্তু প্রেম-ভালবাসার কোনো সম্পর্ক ছিল না। এই টানাপোড়েনের চরিত্র ছিল একেবারেই আলাদা। প্রথমে মৃদুভাবে শুরু হ’লেও পরের দিকে ক্রমশঃ আমার মনে খুব জোরালোভাবে এই প্রশ্ন জাগতে শুরু করে যে নিখিল জগতসংসারকে এবং আমি যার মধ্যে বাস করি সেই মানবসমাজটিকে চালিত-নিয়ন্ত্রিত করে এমন কোনো নৈতিক নিয়মশৃঙ্খলা আদৌ আছে কি না। যে সাধুসন্ত এবং মনীষীদের আমি এতকাল হৃদয়ের শ্রদ্ধা অর্পণ ক’রে এসেছি তাঁরা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে এই জগতের স্রষ্টা এবং নিয়ন্তা হলেন একজন ঈশ্বর, যিনি একাধারে সত্য, শিব ও সুন্দর। কিন্তু আমার চারপাশে আমি যা দেখতে পাচ্ছিলাম তার অধিকাংশই অসত্য, অকল্যাণকর এবং অসুন্দর। ঈশ্বর এবং তাঁর হাতেগড়া সৃষ্টি – এ দু’টোকে আমি কিছুতেই মেলাতে পারছিলাম না।
জগতে মন্দের আধিপত্য সংক্রান্ত এই যে সমস্যাটি আমার মনে জেগে উঠে তাকে আচ্ছন্ন ক’রে ফেলেছিল তার জন্যে আংশিকভাবে হ’লেও দায়ী ছিল আমার ব্যক্তিগত জীবনের হাল। মহাত্মা গান্ধীর কাছ থেকে শেখা বিনম্রতার ভানের আড়ালে আমার মধ্যে লুকোনো ছিল এক বিশাল অহমিকাবোধ। আমি ভালো ছাত্র ছিলাম, শিক্ষালাভের প্রত্যেকটি স্তরে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের কারণে সম্মান এবং ছাত্রবৃত্তিও পেয়েছিলাম। এছাড়া বহু গ্রন্থ পাঠ করবার ফলে আমার মধ্যে একধরণের পণ্ডিতম্মন্য, জ্ঞানী-জ্ঞানী ভাব জেগে উঠেছিল। আমি নীতিবোধসম্পন্ন জীবন যাপন করবার চেষ্টা করতাম, সেটাও আমাকে অন্যদের চাইতে বেশি মহদ্ভাবাপন্ন ক’রে তুলল। আত্মগরিমা বয়ে আনবার এতগুলি স্রোতের সঙ্গমে অবস্থান করবার দরুণ আমি নিজেকে একটা কেউকেটা ব’লে ঠাউরেছিলাম এবং ধ’রেই নিয়েছিলাম যে আমার সমাজ আমায় বিশেষ সুযোগসুবিধা দিতে এবং আমার সঙ্গে মর্যাদাপূর্ণ আচরণ করতে দায়বদ্ধ। এসব শুনতে হাস্যকর হ’তে পারে; কিন্তু যে ব্যক্তি নিজেকে খুব বেশি গুরুত্ব দিয়ে ফেলেছে, তার কাছ থেকে কতটুকু আর রসবোধ আশা করা যায়?
এই যে মনগড়া জগতে বিচরণ করতে আমি ভালোবাসতাম, আমার প্রকৃত পরিস্থিতি কিন্তু ছিল তার চেয়ে একেবারেই আলাদা। আর্থিক অনটনের কারণে অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে আমায় জীবন অতিবাহিত করতে হত। আমার পাণ্ডিত্যের মূল্য যাই হয়ে থাকুক, তার দ্বারা আমার শিক্ষকগণ এবং গুটিকয়েক সহপাঠী ছাড়া আর কেউ উৎফুল্ল হ’ত ব’লে মনে হয় না। আমার চারপাশে থাকা বেশিরভাগ লোকজনই মনে করত যে আমি একটা বইপোকা, আধপাগলা গোছের কেউ। আর্য সমাজ, স্বাধীনতা আন্দোলন এবং হরিজন সেবার কাজে আমার ঝোঁক থাকার দরুণ গ্রামে বাড়ির বড়দের সঙ্গে আমার দূরত্ব ক্রমেই বাড়ছিল। তাঁদের মধ্যে একজন তো আমার গায়ে হাত পর্যন্ত তুলেছিলেন। কিন্তু এসবকিছুর মধ্যে যা আমার কাছে সবচেয়ে নির্মম ঠেকত তা হচ্ছে এই : আমাকে পছন্দ করে এমন কোনো শহুরে বন্ধুর বাড়িতে গেলে তার বাড়ির লোকেরা আমাকে নিজেদের শ্রেণিতে বিচরণের অযোগ্য, চাষাভুষো গেঁয়ো লোক ব’লে অবজ্ঞা করতে কখনোই ছাড়ত না। আমার পোশাক-আশাকের অবস্থা এতই দীনহীন ছিল যে তারা আমায় নিজেদের চাকরবাকরের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলত। একবার আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর বাবা আমার সামনেই তাঁর ছেলেকে এই ব’লে তিরস্কার করেছিলেন যে সে কুসঙ্গে পড়েছে। এই ঘটনাটা ভুলতে এবং ঐ ব্যক্তিটিকে ক্ষমা করতে আমার অনেক সময় লেগেছিল। সেসময় আমআর জানা ছিল না যে আমাদের সমাজের উঁচুতলার লোকেরা সাধারণতঃ খুব নাকউঁচু ধরণের হয়ে থাকে, আর এদের ভদ্র আচার-ব্যবহার শুধুমাত্র তাদেরই জন্য রাখা থাকে যারা আরও উচ্চশ্রেণির লোক।
কিছু সময় বাদে বুঝতে পারলাম যে এক গভীর একাকীত্ববোধ এবং হীনমন্যতা আমায় গ্রাস করছে। পাশ্চাত্য সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডিগুলি খুব বেশি ক’রে পড়বার কারণে আমার মনের এই মেঘাচ্ছন্ন ভাব আরো ঘনীভূত হয়ে উঠল। আমার সবচাইতে প্রিয় ঔপন্যাসিকদের মধ্যে থমাস হার্ডি ছিলেন অন্যতম। তাঁর প্রায় সব রচনাই আমি প’ড়ে নিঃশেষ ক’রে ফেলেছিলাম। শেক্সপীয়রের কমেডিগুলো আমি মাঝপথেই পড়া ছেড়ে দিতাম। কিন্তু তাঁর ট্র্যাজেডিগুলো গোগ্রাসে গিলতাম। হ্যামলেটের সমস্ত লম্বা লম্বা স্বগতোক্তি আমার মুখস্থ ছিল। আমি মনে করতাম যে গ্রে’র এলেজি-র[1] এই স্তবকটির মধ্যে আমার অবস্থাটি নিখুঁতভাবে ফুটে ওঠে :
“Full many a gem of purest ray serene,
The dark unfathomed caves of ocean bear;
Full many a flower is born to blush unseen,
And waste its sweetness on the desert air.”
– আমি একপ্রকার নিশ্চিত ছিলাম যে আমিও ঐসব হতভাগ্য রত্ন এবং ফুলেদেরই মত একজন, যারা ঔজ্জ্বল্য এবং সুগন্ধের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও যথাযোগ্য মর্যাদা পায় না। এই গোটা কবিতাটি আমি হিন্দিতে অনুবাদ করেছিলাম।
তবে আমার চারপাশে যে নৃশংসতা, নিপীড়ন, স্বেচ্ছাচারিতা এবং অন্যায় আমি ঘটতে দেখছিলাম তাতে মোটের উপর জগতে ভালোর উপর মন্দের আধিপত্যের সমস্যাটি আমার চোখে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। আমাকে পীড়া দিয়েছিল এমন অনেক ঘটনাবলীর মধ্যে থেকে মাত্র একটির কথা আমি এখানে উল্লেখ করব। আমাদের গ্রামে একটা বড় সংখ্যক হরিজন সম্প্রদায়ের মানুষ বাস করতেন, যাঁদের মধ্যে অনেকেই অন্য নানান জীবিকার পাশাপাশি চাষের জমিতে শ্রমিকের কাজও করতেন। ফসল কাটবার মরসুম এলে আশেপাশের অন্য অনেক গ্রামে চাষের জমিতে কাজ করবার লোকের অভাব দেখা দিত। সেই কারণে এইসব গ্রাম এই শ্রমিকদের আমাদের গ্রামের তুলনায় বেশি পারিশ্রমিক দিত। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের গ্রামের হরিজনেরা এইসব পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতে যেতে শুরু করেন, যা আমাদের গ্রামের জমির মালিক বড় কৃষকেরা ভালোভাবে নেননি। এঁদের একদল গুন্ডাবাহিনী একদিন হরিজনদের বসতি আক্রমণ করে, হরিজন সম্প্রদায়ের বেশ কয়েকজনের বাড়ি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়, এবং যদি হরিজন সম্প্রদায়ের পুরুষেরা শুধুমাত্র আমাদেরই গ্রামের জমিতে গ্রাম পঞ্চায়েতের (যেখানে হরিজনদের কোনো প্রতিনিধি ছিল না) ধার্য ক’রে দেওয়া মজুরি অনুযায়ী কাজ করতে রাজি না থাকে তাহলে হরিজন মহিলাদের শ্লীলতাহানি করা হবে এই ব’লে শাসানিও দেয়। ঘটনাচক্রে সেদিন আমি গ্রামেই উপস্থিত থাকায় হরিজন আশ্রমের কিছু ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে বস্তিটি পরিদর্শন করতে গিয়েছিলাম। ঐ ঘটনার আতঙ্কে হতভম্ব হয়ে যাওয়া জনৈকা সদ্যবিবাহিতা হরিজন রমণীর বোবা চাউনি দেখে সেবার আমি নিজের অশ্রু সংবরণ করতে পারিনি।
আমার জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে এক সহপাঠীর সঙ্গে আমার খুব ভালো বন্ধুত্ব গ’ড়ে উঠল, যে ছিল দর্শনের ছাত্র। দর্শন আমার বিষয় নয়। তার ছিল অগাধ পড়াশুনো। তদুপরি সে ছিল সুবক্তা। প্রায় যেন ঈশ্বরপ্রেরিত হয়ে সে এমন একটা সময়ে আমার জীবনে এসেছিল, যখন এরকম কারুর সঙ্গলাভ করা আমার পক্ষে খুবই দরকারি হয়ে পড়েছিল। সেসময় শহর হিসেবে দিল্লী বেশ ছোটোই ছিল, এবং যমুনার ধারে কিংবা দিল্লীর বাইরের জনবিরল রাস্তাগুলোয় দীর্ঘ সময়ের জন্য হাঁটতে যাওয়া তখন আমাদের একটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। হাঁটতে হাঁটতে সে আমায় তর্কশাস্ত্রের আরোহী এবং অবরোহী পদ্ধতি, নীতিশাস্ত্র, মনস্তত্ত্ব, এবং পাশ্চাত্য দর্শনের আরো নানান বিষয়ে শিক্ষা দিত। বিষয়গুলি ছিল খুবই মনোগ্রাহী, এবং আমার সামনে তখন চিন্তাভাবনা-ধ্যানধারণার একটা নতুন দিগন্ত খুলে গেল। এখনও আমি এই সহপাঠীটিকে আমার দুজন মহান গুরুর একজন হিসেবে গণ্য করি।
মাঝেমধ্যে সে অবশ্য তেমন সব বিষয়ের উপরেও নিজের ব্যক্তিগত মতামত এবং বিচার ব্যক্ত করত, যেগুলোর ব্যাপারে ইতিমধ্যেই আমার নিজস্ব পাকা সিদ্ধান্ত গ’ড়ে উঠেছিল ব’লে আমি মনে করতাম। একদিন আমাদের মধ্যে তীব্র বাদানুবাদ হয়েছিল; কারণ সে সেদিন বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানটিকে বর্জন করবার কথা ব’লে এই মত ব্যক্ত করল যে একজন নারী ও একজন পুরুষ যতকাল একে অপরকে পছন্দ করে ততকাল তারা স্বেচ্ছায় স্বাধীনভাবে একত্রে বাস করবার অধিকার পাওয়ার যোগ্য। তবে অহিংসার পূজারী হওয়া সত্ত্বেও আমার মাথায় খুন চেপে গিয়েছিল যখন এক সকালে সে ব’লে বসল যে গান্ধী হচ্ছেন সবরকম প্রতিক্রিয়াশীলতার মূর্ত বিগ্রহ। এই একটা নতুন শব্দ শুনলাম আমি। ব্যাপারটা নিজে যাচাই করে দেখবার জন্য সে আমায় যশপাল রচিত “গান্ধীবাদ কা শবপরীক্ষণ” (গান্ধীবাদের শব-ব্যবচ্ছেদ) প’ড়ে দেখতে বলল। আমি তো তখন কস্মিনকালেও যশপালের নাম শুনিনি, এবং সেজন্যে কোনোরকম মাথাব্যথাও আমার ছিল না। এর বেশ কিছু বছর বাদে একজন কমিউনিস্টে পরিণত না হওয়া ইস্তক আমি বইটা পড়িওনি। সেসময় আমার বন্ধুটি কমিউনিস্ট ছিল না, এমনকী সারাজীবনে সে কখনো মার্ক্সবাদীও হয়নি। কিন্তু সে ছিল বিপ্লবীদের খুব বড় ভক্ত, এবং সে বলত যে কেউ কেউ এঁদেরকে ভুল ক’রে সন্ত্রাসবাদী ব’লে বর্ণনা ক’রে থাকে। আমি অবশ্য বিপ্লবীদের অথবা সন্ত্রাসবাদীদের ব্যাপারে কিছুই জানতাম না – এক ভগত সিংহকে ছাড়া, যাঁকে মহাত্মা গান্ধী “পথভ্রষ্ট দেশপ্রেমিক” আখ্যা দিয়েছিলেন।
গান্ধীবাদের সপক্ষে আমার মনের ভেতর গ’ড়ে ওঠা যাবতীয় যুক্তি-সমর্থনের প্রতিরোধ একের পর এক ভেঙে পড়তে লাগল, যার পেছনে ছিল আমার দার্শনিক বন্ধুটির লাগাতার আক্রমণ। তাকে আমার ভালো লাগত তার কারণ সে ছিল একজন অসাধারণ মানুষ, এবং তাকে আমি আমার চাইতে জ্ঞানে এবং বুদ্ধিতে বড় ব’লে মেনেছিলাম। কিন্তু তার যে বিশ্বাসটি আমার পক্ষে কিছুতেই মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না তা হচ্ছে – এই জগত আসলে শয়তানের দ্বারা নির্মিত এবং নিয়ন্ত্রিত; মাঝেমধ্যে শয়তান মানুষের দিকে টুকরোটাকরা সুখ ছুঁড়ে দেয় যাতে ক’রে অসহায় মানুষকে সে আরো আষ্টেপৃষ্ঠে নিজের জালে জড়িয়ে নিতে পারে। এইভাবে সমস্ত আশা চিরতরে ত্যাগ করতে আমি একেবারেই তৈরি ছিলাম না। কিন্তু জড়জগত এবং জীবজগতের বিবর্তনবাদী ব্যাখ্যার যে বয়ানটি আমি দু-এক বছর আগে এইচ জি ওয়েল্স্-এর “আউটলাইন অফ হিস্ট্রি”-তে (ইতিহাসের রূপরেখা) পড়েছিলাম, সেই ব্যাখ্যাটি এখন হঠাৎ ক’রে আমার চেতনায় প্রাণ পেতে লাগল। ততকাল অব্দি এই বিশাল বইটির যে যৎসামান্য অংশ আমার মনে ছিল তা হচ্ছে এটির মধ্যে উল্লিখিত কয়েকখানি অ-গতানুগতিক মন্তব্য; যেমন, মানবেতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা হচ্ছেন অশোক, আলেকজান্ডার এবং নেপোলিয়ন হচ্ছেন দাগী অপরাধী, এবং মহম্মদ ছিলেন একজন ভবঘুরে প্রকৃতির লোক। এই সময় আমার মনে প্রশ্ন উঠতে লাগল : আসলে কি এই জগতটা সত্যিই কতকগুলো অণু-পরমাণুর কাকতালীয় সংযোগের ফল, যার ভেতরে এমন কোনো সচেতন উদ্দেশ্য নেই যা এই জগতকে একটি দৈবী পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে পারে? এর অবয়বটির কেন্দ্রে কোনো নৈতিক শৃঙ্খলাই কি নেই, যা একে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে?
গান্ধীবাদ আমার কাছে তখন হয়ে উঠেছিল একখানা কফিন, যাতে শেষ পেরেক ঠোকার কাজটি করেছিল “গান্ধীবাদ ভার্সাস সোশ্যালিজম” (গান্ধীবাদ বনাম সমাজবাদ) নামের একটি বই, যে বইটি ‘সস্তা সাহিত্য মণ্ডল’ নামক পুস্তকবিপণিতে আমার নজর কেড়েছিল। তখন অব্দি আমি সমাজবাদ সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। এর বছরদুয়েক আগে গান্ধীজী এবং সুভাষচন্দ্র বসুর মধ্যে চলতে থাকা বিতর্কই প্রথমবার এই শব্দটিকে আমার চোখের সামনে তুলে ধরে। আমি এই প্রসঙ্গটি আমার হরিজন আশ্রমের বন্ধুটির কাছে পাড়লাম। সে আমায় জানায় যে সমাজবাদীরা বম্ব পার্টির (বোমার দল) অন্তর্ভুক্ত এবং তারা সহিংস পন্থায় বিশ্বাসী। আমার কাছে তখনকার মত সেখানেই ব্যাপারটার ইতি ঘটে। কিন্তু এই বইটি পড়তে পড়তে সমাজবাদ সম্পর্কে আমার ধারণাটাই আমূল বদলে গেল। একদল প্রথিতযশা গান্ধীবাদী এবং সমাজবাদীদের মধ্যেকার বিতর্কে গান্ধীবাদীরা হেরে বসেছিলেন। যে ব্যাপারটা আমায় নাড়া দিয়েছিল সেটা হচ্ছে এই – একদিকে যখন গান্ধীবাদীরা সর্বক্ষণ রক্ষণাত্মক ভূমিকায় ছিলেন, এবং নানারকম ভাবে প্রমাণ করবার চেষ্টা করছিলেন যে গান্ধীবাদও আসলে একধরণের সমাজবাদ, তখন অন্যদিকে সমাজবাদীরা আক্রমণাত্মক ভঙ্গিমায় ঠিক এই কথাটাই তুলে ধরছিলেন যে গান্ধীবাদ আসলে সমাজবাদ তো নয়ই, বরং তা একরকমের প্রতিক্রিয়াশীল এবং পশ্চাদ্মুখী মতবাদ।
আমার মধ্যে তখন সমাজবাদ নামক এই মতবাদটিকে ভালো ক’রে তলিয়ে জানবার জন্য একটা প্রচণ্ড তাড়া জেগে উঠল। পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক চিন্তার ইতিহাসের দ্বিতীয় বর্ষের পাঠক্রম অনুযায়ী এটি আমার পাঠ্যবিষয় হিসেবে নির্ধারিত তো ছিলই। কিন্তু পরের বছর অব্দি অপেক্ষা করতে আমার তর সইছিল না। বি.এ. অনার্সের সিলেবাসে সমাজবাদ বিষয়ে উচ্চতর পাঠের জন্য অনুমোদিত বইগুলির তালিকায় সবার উপরে ছিল হ্যারল্ড লাস্কির “কমিউনিজম”। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার থেকে এই বইটির একখানি কপি ধার ক’রে বাইরের লনেই ব’সে গেলাম পড়তে। তখনো পর্যন্ত আর কোনো বই আমাকে এই বইটির মত এতখানি বিমোহিত করতে পারেনি। সেদিন আমি ততক্ষণ অব্দি পড়েছিলাম যতক্ষণ না অন্ধকার ঘনিয়ে আসার কারণে আর পড়া যাচ্ছিল না। বইটি আমি বাড়ি নিয়ে এলাম এবং যখন সেটি পড়া শেষ করলাম ততক্ষণে অনেক রাত হয়ে গেছে। এই বইটি তবু তুলনামূলকভাবে ছোট ছিল। কিন্তু পরদিন সকালে যখন আমি ঘুম থেকে উঠলাম, ততক্ষণে আমার সাধের গান্ধীবাদ ভেঙে খান খান হয়ে গেছে।
লাস্কির বইটি আমাকে পরপর আরো দুটি বই পড়বার জন্য অনুপ্রাণিত করল। দুটিই তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল। কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপকের কাছে দুটি বই-ই ছিল এবং তিনি বইগুলি আমাকে ধার দিতে সানন্দে রাজি হয়ে গেলেন, এই শর্তে যে আমি বইগুলো খবরের কাগজে মুড়ে বয়ে নিয়ে যাবো এবং কেবলমাত্র আমার ঘরের চারদেয়ালের মধ্যেই তাদের সন্তর্পণে খুলব। এই বইগুলির মধ্যে একটি ছিল জন স্ট্র্যাচির “থিওরি অ্যান্ড প্র্যাকটিস অফ সোশ্যালিজম” (সমাজবাদের তত্ত্ব ও প্রয়োগ)। অন্যটি হচ্ছে এডগার স্নো রচিত “রেড স্টার ওভার চায়না” (চীনের আকাশে লাল তারা)। বইগুলোকে আমার লাস্কির “কমিউনিজম”-এর মতোই চিত্তাকর্ষক লাগল। স্ট্র্যাচি পরবর্তীকালে কমিউনিজম ত্যাগ ক’রে ব্রিটিশ লেবার পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন। চীনা কমিউনিস্টরা শেষ অব্দি এডগার স্নো-কে সি.আই.এ.-এর দালাল আখ্যা দিয়েছিল। কিন্তু এই দু’টি বইয়ের খ্যাতি যেমন এদের রচয়িতাদের সুনামের মতোই দীর্ঘদিন অক্ষুণ্ণ ছিল, তেমনই এই দুটি বইয়ের কারণে ভারতবর্ষে যত লোক কমিউনিস্টে পরিণত হয়েছিল তত আর কোনো গ্রন্থের কারণে হয়নি।
এবার কার্ল মার্ক্স পড়বার বাসনাটি অদম্য হয়ে উঠল। প্রথমে আমি পড়লাম “কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো”। এতে মানুষের ইতিহাসের বিশাল বিশাল সব পর্ব যে গভীরতা এবং ব্যাপ্তির মাধ্যমে পর্যালোচিত হয়েছে তা এককথায় রুদ্ধশ্বাস রকমের অনবদ্য। এছাড়া এর মধ্যে দুনিয়াটাকে বদলাবার এবং চিরকালের মত শোষণ ও সামাজিক অন্যায়ের অবসান ঘটাবার জন্য একটি মহান লড়াইয়ে যোগ দেবার আহ্বানও রয়েছে। আর সবচেয়ে বড় ভরসার কথা হচ্ছে যে, সামাজিক শক্তিগুলি বিবর্তনের সিঁড়ি বেয়ে যে পরিণতির দিকে ছুটে চলেছে, যাবতীয় বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও সমস্ত শ্রেণিদ্বন্দ্বের চরম অবসান ঘটবার সেই অন্তিম এবং অবশ্যম্ভাবী উদ্দেশ্যসাধনের পথে এই বইতে বর্ণিত বৈপ্লবিক কর্মসূচী স্রেফ একখানি সহায়কের ভূমিকা পালন করবে। মার্ক্সবাদী হয়ে ওঠার জন্য আমার আর এর বেশি মার্ক্স পড়বার দরকার ছিল না। তবু আমি পাতা ধ’রে ধ’রে দু’খণ্ড “দাস কাপিটাল” পড়া শেষ করেছিলাম। খাঁটি প্রাচীনপন্থী জার্মান পাণ্ডিত্য-পরম্পরার অনুসারী মার্ক্সের এই পুঙ্খানুপুঙ্খ এবং পরিশ্রমসাধ্য রচনাটি পড়তে গিয়ে আমায় নিজের বুদ্ধিবৃত্তির সবটুকু প্রয়োগ করতে হয়েছিল। কিন্তু এটি পড়বার পর আমার মনে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ রইল না যে তিনি পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে এবং শ্রমের মূল্যায়ন সংক্রান্ত তত্ত্বের[2] সপক্ষে তাঁর তর্কটিকে ক্ষুরধার যুক্তির মাধ্যমে নথিভুক্ত তথ্য ও পরিসংখ্যানের দৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন, যার ফলে ওতে আর কোনো ফাঁকফোকর কিংবা দুর্বলতা ছিল না।
সেই সময় আমি আর কোনো ধ্রুপদী কমিউনিস্ট রচনা অথবা অন্য কোনোরকম কমিউনিস্ট লেখালেখি পড়েছিলাম কিনা তা আর মনে নেই। এটুকু নিশ্চিত ক’রে বলতে পারি যে লেনিন কিংবা স্তালিনের কোনো রচনা পড়িনি। মাও তখনো অব্দি কমিউনিস্ট তাত্ত্বিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেননি। এমনকী ভারতবর্ষের বুকে সংঘটিত কোনোরকম কমিউনিস্ট অথবা সমাজবাদী আন্দোলনের অস্তিত্বের কথাও আমার জানা ছিল না। নিত্যনৈমিত্তিক, ব্যবহারিক রাজনীতিতে আমার একটুও আগ্রহ ছিল না। সেই সময় আমি দৈনিক খবরের কাগজও বিশেষ পড়তাম না, কোনো বিশেষ দলীয় মুখপত্র তো দূরে থাক্। তখন অব্দি একমাত্র যে পত্রিকাটি আমি নিয়মিত পাঠ করতাম সেটি হচ্ছে মহাত্মা গান্ধীর সাপ্তাহিকী “হরিজন”। কিন্তু তা কোনো রাজনৈতিক আগ্রহের কারণে নয়। মহাত্মার সাপ্তাহিকীর প্রতি আমার আকর্ষণের মূল কারণ ছিল নৈতিক সমস্যাগুলির বিষয়ে তাঁর নিবিড় মনোনিবেশ। আমি তখন ভেবে বসলাম যে মার্ক্স যে পন্থা বাতলেছেন, তা ঐ নৈতিক সমস্যাগুলির আরো গভীরে গিয়ে সমাধান করতে সক্ষম। কারণ অনৈতিক সমাজে বসবাসকারী ব্যক্তির পক্ষে কখনো নৈতিক হওয়া সম্ভব নয়।
এরপরেই এলো সেই চরম বিভ্রান্তি, যা আরো অনেকের ক্ষেত্রেই ঘটেছে ব’লে আমি মনে করি। আমি মার্ক্সবাদী থেকে একজন কমিউনিস্টে পরিণত হলাম – অর্থাৎ সোভিয়েত ইউনিয়নের উপাসক বনে গেলাম। সোভিয়েত রাশিয়াতে জীবনযাত্রার মান কীরকম সে সম্পর্কে তখনো একটিও বই আমার পড়া হয়নি। তবু স্রেফ অনুমানের ভিত্তিতে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে প্রলেতারিয়েতদের বিপ্লব সংঘটিত হবার পর যে যুগ সমাসন্ন ব’লে মার্ক্স আশ্বাস দিয়েছিলেন তার সূত্রপাত নিশ্চয়ই কমিউনিস্ট নামধারী এই দেশটিতেই হয়েছে। এখন অতীতের দিকে ফিরে তাকালে আমার এই ভেবে অবাক লাগে যে তাত্ত্বিক প্রশ্নের বেলায় আমার মন অত্যন্ত সজাগ থাকলেও ঘোর বাস্তবের ক্ষেত্রে কী ক’রে আমি এত জড়বুদ্ধি হয়ে রইলাম! কিন্তু এই মতাদর্শগত প্রতারণাটি ঘটেছিল খুব মসৃণভাবে; এবং তা ঘটেছিল আমার বুদ্ধিবৃত্তির তরফ থেকে কোনোরকম প্রতিরোধ ছাড়াই। কাজেই মহাত্মা গান্ধী যখন ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ডাক দিলেন, তখন আমি নিজেকে খুঁজে পেলাম বিরোধী শিবিরে। যেসব স্বাধীনতা সংগ্রামীরা ব্রিটিশের গুলিতে প্রাণ দিচ্ছিলেন অথবা যাঁদের ব্রিটিশের জেলে পোরা হচ্ছিল, তাঁদের প্রতি কোনোরকম সহানুভূতিই আমি টের পাচ্ছিলাম না। আমার দৃষ্টি তখন নিবদ্ধ সোভিয়েত ইউনিয়নের বিস্তীর্ণ প্রসরে যে মহাসংগ্রাম লড়া হয়ে চলেছে তার দিকে। আমি দৈনিক খবরের কাগজ পড়া শুরু ক’রে দিয়েছিলাম।
ঐ একই সময়ে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে জগতের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরকে কেবলমাত্র নিম্নলিখিত তিনটি উপায়ে কল্পনা করা যেতে পারে – হয় একজন দুর্বৃত্ত রূপে, যে কিনা জগতে ঘটতে থাকা সমস্ত দুর্বৃত্তপনা অনুমোদন করে এবং তাতে অংশগ্রহণও ক’রে থাকে; অথবা একজন আহাম্মক রূপে – যে নিজের সৃষ্টিকে আর নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে না; অথবা একজন সন্ন্যাসী রূপে, যে কিনা নিজের সন্ততিদের সঙ্গে কী ঘটছে না ঘটছে সে ব্যাপারে আর পরোয়া করে না। ঈশ্বর যদি একজন দুর্বৃত্ত হয়ে থাকেন, তাহলে আমাদের কর্তব্য হচ্ছে তাঁর শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা। যদি তিনি একজন আহাম্মক হয়ে থাকেন, তাহলে তাঁকে ভুলে গিয়ে আমরা নিজেরাই এই জগতের ভার নিজেদের হাতে তুলে নিতে পারি। আর তিনি যদি সন্ন্যাসী হয়ে থাকেন, তাহলে তিনি নিজের চরকায় তেল দিতে পারেন, এবং আমরা আমাদেরটায়। শাস্ত্রসমূহ অবশ্য সম্পূর্ণ অন্য একধরণের ঈশ্বরের কথা ব’লে থাকে। সেই ধরণের ঈশ্বরকে অবশ্য অভিজ্ঞতা অথবা যুক্তির সাহায্যে যাচাই করা সম্ভব হচ্ছিল না। অতএব শাস্ত্রগ্রন্থগুলিকে আগুনে পোড়ানোই শ্রেয়, বিশেষ করে শীতের সময়ে, কারণ তাতে অন্ততঃ একটু উত্তাপ মিলবে।
আমার এই নতুন ধর্মবিশ্বাস গ্রহণ করবার কথা ঘোষণা করার ফলে একটা মজাদার পরিণতি হয়েছিল। আমি একবার আমাদের গ্রামের কিছু কৌতূহলী চিন্তাশীল লোকজনের একটি ছোটো জমায়েতের সামনে বক্তব্য রাখছিলাম। ওঁদের কাছে যখন আমি আমার নতুন দৃষ্টিভঙ্গিটি ব্যাখ্যা করছিলাম, তখন কেউ একজন এসে খবর দিল যে আর্য সমাজের সভাপতি মহাশয় হাতে একটা মোটাসোটা লাঠি নিয়ে নিজের বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন। আমি সে সময় জনসমক্ষে কি প্রচার করছিলাম সে খবরও তিনি জানতেন। এবং তাঁর নাকি বদ্ধমূল ধারণা যে তাঁর লাঠির বাড়ি আমার মাথার উপর এসে পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই ঈশ্বরকে আমি সম্পূর্ণ নতুন আলোকে দেখতে পাবো এবং জগতে ঈশ্বরের ভূমিকা সম্পর্কে আমার ধারণাও আমূল বদলে যাবে। আমায় স্বীকার করতেই হচ্ছে যে এই পরীক্ষার জন্য আমি একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না। ফলতঃ আমি পিঠটান দিলাম এবং সেই দিনই গ্রাম ছেড়ে পালালাম। আমি আশা করেছিলাম যে যথাসময়ে সভাপতি মশাইয়ের মেজাজ ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। তা-ই হয়েছিল। এরপর থেকে আমি গ্রামের শ্রোতাদের সমক্ষে আমার জঙ্গি নাস্তিকতা প্রচার করবার ব্যাপারে আগের চেয়ে অনেক বেশি সাবধানতা অবলম্বন করতে শুরু করলাম।
পাদটীকা
[1] বাংলা প্রতিশব্দ ‘শোকগাথা’; ইংরেজ কবি থমাস গ্রে রচিত “এলেজি রিট্ন্ ইন আ কান্ট্রি চার্চইয়ার্ড” শীর্ষক কবিতা থেকে লেখক শ্রী গোয়েল কর্তৃক উদ্ধৃত, কবিতাটির প্রকাশকাল ১৭৫১ খ্রিস্টাব্দ (পাদটীকা – অনুবাদক)
[2] Labour Theory of Value
মূল গ্রন্থের রচয়িতা: সীতারাম গোয়েল
বঙ্গানুবাদ : শ্রীবিজয়াদিত্য