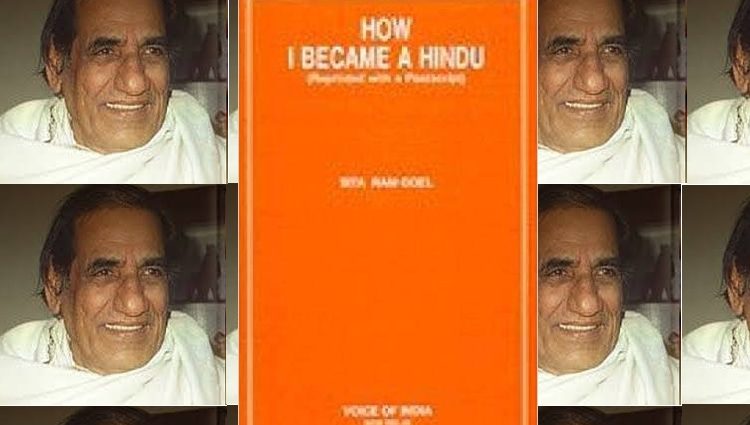অনুবাদকের ভূমিকা
সীতারাম গোয়েল এবং রাম স্বরূপ – আধুনিক কালে ভারতীয় চিন্তাজগতের নিজস্ব ঘরানার এই দুই উজ্জ্বল নক্ষত্রের লেখা বাংলা ভাষায় খুব বেশি আলোচিত হয়নি। হিন্দু সভ্যতার উপর লাগাতার ইসলামী মৌলবাদ, ইউরো-আমেরিকান-খ্রিস্টীয় সাম্রাজ্যবাদ এবং বামপন্থার ত্রিমুখী আক্রমণের ফল হিসেবে যেসব ক্ষয়ক্ষতি ঘটেছে, তার খতিয়ান স্বাধীনোত্তর ভারতে এই দুই চিন্তাবিদ যত্ন সহকারে এবং সাহসিকতার সঙ্গে দিয়েছেন।
ফল হিসেবে ব্যক্তিগতভাবে এঁদের অভূতপূর্ব ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। যে রকম তীক্ষ্ণ মেধাশক্তির অধিকারী এঁরা ছিলেন, তাতে পশ্চিমের যেকোনো প্রথম সারির বিশ্ববিদ্যালয় কি এদেশের জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের স্থায়ী আসনটি পাকা করে ফেলা এঁদের পক্ষে অতীব সহজ হ’ত; কিন্তু সেজন্য বামপন্থী-খ্রিস্টীয়-ইসলামী কায়েমি স্বার্থের পায়ের তলায় মেধা বন্ধক রাখবার যে শর্তটি পূরণ করা আবশ্যিক ছিল তা এঁরা করেননি। কিন্তু আযৌবন এই দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মনন-চিন্তন ও বৌদ্ধিক চর্চা সেজন্য থেমে থাকেনি; থেমে থাকেনি এঁদের ক্ষুরধার লেখনীও। ভারতের সত্যের প্রতি এঁরা সদা নিষ্ঠাবান থেকেছেন; ভারতের সত্যকে ধামাচাপা দেবার অপপ্রয়াস, এবং বিশেষ ক’রে এব্যাপারে বামপন্থী ইতিহাসবিদদের অপপ্রয়াসকে এঁরা ভারতীয়দের নব প্রজন্ম তথা বিশ্বের পাঠককুলের সামনে হাট ক’রে দিয়েছেন।
স্বভাবতঃই সুদীর্ঘ বামপন্থী শাসনের আওতায় থাকা পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি পাঠককুলের সামনে বাংলা ভাষায় এঁদের রচনা প্রকাশিত করবার কোনোরকম চেষ্টা হয়নি। আর হবেই বা কী ক’রে – যে বামপন্থীরা হিন্দুদের পৃথিবীর সবচাইতে অসহিষ্ণু প্রাণী হিসেবে দেগে দিতে সদাসর্বদা সচেষ্ট থাকেন, তাঁরা নিজেরাই তো পরমত শুনতে চান না – শুনতে পারেন না!
অধুনা তাই এঁদের অতি প্রয়োজনীয় রচনাগুলি, যা গত দুই-তিন প্রজন্মের হিন্দু তথা ভারতীয়দের ভারতবর্ষের সত্য সম্পর্কে জাগরূক করেছে, বাংলা ভাষায় অনুবাদের মাধ্যমে পরিবেশন করবার চেষ্টা করা গেল। আরম্ভ হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে শ্রী সীতারাম গোয়েলের আত্মজীবনীমূলক এই পুস্তিকাটিকে। এটি যে স্রেফ একটি সুখপাঠ্য রচনা শুধু তাই নয়, এর মাধ্যমে আপন শিকড়ের সন্ধানরত বহু হিন্দু তথা ভারতীয় নিজের ব্যক্তিগত বিবর্তনের পথনির্দেশিকা খুঁজে পাবেন; অথবা যাঁরা ইতিমধ্যেই শ্রীভগবানের কৃপায় সে শিকড়ের সন্ধান পেয়ে গেছেন, তাঁরা নিজের বিবর্তনের ইতিহাসের একখানি প্রতিফলন দেখতে পাবেন ব’লে আমার বিশ্বাস।
অনুবাদ যথাসম্ভব সরল এবং সরস রাখবার চেষ্টা করেছি; এবং সে আয়াস করতে গিয়ে লেখকের মূল ইংরেজি রচনার প্রতি যথাসাধ্য অনুগত থাকবার ব্যাপারেও চেষ্টার কসুর করিনি। এই দুই চেষ্টা অনেক সময়ই পরস্পরবিরোধী হয়ে ওঠে, আর মাঝখান থেকে তাতে ক্ষুণ্ণ হয় ভাষার সৌকর্য। কিন্তু আমার দৃঢ় প্রত্যয় এই যে অনুবাদসাহিত্য লক্ষ্য-ভাষার (টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজ) সাহিত্যের একটি মূল্যবান অঙ্গ, এবং অনুবাদে এই লক্ষ্য-ভাষার সাহিত্যেরই পুষ্টি এবং পরিবর্ধন ঘটে – উৎস-ভাষার (সোর্স ল্যাঙ্গুয়েজ) সাহিত্যের নয়। তাই আমার বঙ্গানুবাদে বাংলা ভাষার সৌকর্য এবং স্বাভাবিক সারল্যকে বজায় রাখতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি।
বঙ্গদেশ পত্রিকা এই অমূল্য সাহিত্য বাঙালি পাঠকের সামনে উপস্থাপন করবার সুযোগ দিয়ে আমায় চিরকৃতজ্ঞ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ তথা নিখিল বঙ্গভূমির এই সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক সন্ধিক্ষণের দিনে, বঙ্গীয় হিন্দু সভ্যতার সঙ্কটের ক্ষণে এই গ্রন্থের অনুবাদকর্ম একটি সদর্থক ভূমিকা পালন করবে; এটি পাঠ ক’রে অগণিত বাঙালি নিজের হৃত পরিচয় এবং গৌরব ফিরে পাবেন, এবং সর্বোপরি অদূর ভবিষ্যতে আমাদের জন্মভূমি অখণ্ড বঙ্গমাতা ভারতবর্ষের বিরাট শরীরের মধ্যে তাঁর যথাযোগ্য মর্যাদার আসনটি পুনরুদ্ধার করবেন, এই আশায় শ্রীহরির চরণকমলে তাঁরই ইচ্ছার ফল এই ক্ষুদ্র প্রয়াসটি উৎসর্গ করলাম। অতঃ কিম্।
ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।।
– শ্রীবিজয়াদিত্য
২২ ভাদ্র ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
এক
আর্য সমাজ হ’তে মহাত্মা গান্ধী পর্যন্ত
(প্রায় বছর কুড়ি আগে আমার চিন্তাজগতের ক্রমবিকাশ-সংক্রান্ত এই জীবনপঞ্জিটি লিখে দেবো ব’লে হশ্মতকে কথা দিয়েছিলাম। হশ্মত সেসময় ‘অর্গানাইজার’ পত্রিকায় “পাকিস্তান এক্স রে-ড” নামের একটি কলামে নিয়মিত লেখালেখি করত। তারপর বহু বছর যাবৎ ওর সঙ্গে আমার যোগাযোগ রক্ষা করা হয়ে ওঠেনি। কিন্তু ওকে দেয়া কথাটা ভুলে যাইনি কখনোই। এখন ভাবি, সেই কুড়ি বছর আগেকার সময়ে লিখলে এই লেখাটা কীরকম দাঁড়াত। এটাও ভাবি যে আজ থেকে কুড়ি বছর বাদে এই গল্প বলতে বসলে তার চেহারাটা ঠিক কী রকম হবে। আজকের পরিপ্রেক্ষিতে এই লেখাটার মূল্যায়ন কেমন হবে তাও আমার জানা নেই। কিন্তু লেখাটা লেখবার যে আত্যন্তিক তাগিদ অনুভব করছি তার কারণ আজকের ভারতবর্ষে স্রেফ জন্মসূত্রে হিন্দু হওয়াটাই যথেষ্ট নয়। আজ হিন্দু সমাজ ও সংস্কৃতি অনেকগুলি দিক থেকে আক্রমণের সম্মুখীন। সেই আক্রমণগুলির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে এবং সেগুলিকে প্রতিহত করতে হ’লে একজন প্রত্যয়ী এবং সচেতন হিন্দু হয়ে ওঠার প্রয়োজন আছে। প্রয়োজন আছে সনাতন ধর্মের গভীরে নিজের শিকড়টিকে খুঁজে নেওয়ার।)[1]
আমি জন্মসূত্রে হিন্দু। কিন্তু বাইশ বছর বয়েসে যখন আমি কলেজের পড়া শেষ করি, ততদিনে আমি আর হিন্দু নই। ততদিনে আমি হয়ে গিয়েছি মার্ক্সবাদী, এবং একজন আগুনখোর নাস্তিক। ততদিনে আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে ভারতবর্ষকে বাঁচাতে হ’লে যাবতীয় হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থগুলিকে আগুনের স্তূপে আহুতি দিতেই হবে।
এর পনেরো বছর পরে আমি উপলব্ধি করি যে উপরোক্ত পরিণতির পিছনে যা ছিল তা হচ্ছে ভয়ঙ্করভাবে ফুলেফেঁপে ওঠা অহং-এর উদ্গীরণ। নিজের চেতনাকে নিজে হাতে বিষিয়ে তোলার সেই দিনগুলিতে আমি একপ্রকার নিশ্চিত ছিলাম যে বিশ্বজোড়া সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলতে পারে এমন কোনো দার্শনিক অনুসন্ধানে বুঝি বা আমি ব্যাপৃত আছি।
কীভাবে আমার আত্মম্ভরিতা এই পর্যায়ে পৌঁছল যেখানে আমি আমার মনগড়া, অসুস্থ, কাল্পনিক নির্মাণগুলির বাইরে আর কিছু দেখতেই পেতাম না – সে এমন কিছু ব্যতিক্রমী কাহিনী নয়। এমনটা আমাদের মতো অনেক নশ্বর প্রাণীর জীবনে প্রায়ই ঘটে থাকে। কিন্তু নিজের হাতে বোনা এই মাকড়সার জাল কেটে বেরনোর জন্য যে অনুসন্ধানের ভেতর দিয়ে আমায় যেতে হয়েছে – আর সেজন্য যে কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে, যে সংগ্রাম করতে হয়েছে – সেটুকুই আমার এই জীবনকাহিনীতে আলোকিত হবার দাবী রাখে। কাহিনীর বাকি সূত্রগুলো আমি যথাস্থানে ধরিয়ে দিতে দিতে অগ্রসর হব।
একটা ছোটো ছেলে তার স্বাভাবিক শিশুসুলভ প্রবৃত্তি অনুযায়ী সাধারণতঃ যেসব ব্যাপারে আকৃষ্ট হয়, সেগুলোর অতিরিক্ত অন্যান্য বিষয়ের প্রতি আমার মন কী ক’রে ধাবিত হ’ল সে সম্পর্কিত আমার সবচাইতে পুরনো যে স্মৃতিটি রয়েছে তা হচ্ছে সেই সময়কার যখন আমার বয়স আট বছর। আমরা তখন কলকাতায় থাকতাম। আমার বাবা পাটজাত পণ্যের আড়তদারির ব্যাবসায় নেমে ডাহা ফেল করেন। কিন্তু গল্প-বলিয়ে হিসেবে তাঁর জুড়ি মেলা ভার ছিল। গ্রামের পাঠশালায় মাত্র দু-তিন বছর পড়াশোনা করেছিলেন, কাজেই সেই অর্থে তাঁকে শিক্ষিত বলা চলে না। কিন্তু অল্পবয়সে অসংখ্য কথকতা আর কীর্তনের আসরে অংশ নেওয়ার দরুণ অনেকখানি ইতিহাস-পুরাণ তাঁর মনে গেঁথে গিয়েছিল। হিন্দু পুরাণ, বীর যোদ্ধাদের কিংবদন্তি এবং সাধুসন্তদের জীবনকথা বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ছিল রীতিমতো ঈর্ষণীয়।
একদিন সন্ধেবেলা তিনি আমাকে মহাভারতের দীর্ঘ এবং জটিল কাহিনীটি শোনাতে শুরু করেন। পুরো কাহিনী শেষ করতে সময় লেগেছিল একমাসেরও বেশি; এবং প্রত্যেক কিস্তিতে একঘণ্টারও বেশি সময় ধ’রে কথকতা চলত। প্রবল মনোযোগ সহকারে প্রায় রুদ্ধশ্বাস অবস্থায় আমি সেই বিরাট কাহিনীর প্রতিটি পর্ব এবং ঘটনা গোগ্রাসে গিলেছিলাম। কাহিনী এগোবার সঙ্গে সঙ্গে মহাভারতের কিছু চরিত্রের অপরিসীম চরিত্রবলের যে পরিচয় পেতে শুরু করলাম, তা আমাকে দৈনন্দিন জীবনের একঘেয়েমির অনেক উর্দ্ধে উঠিয়ে নিয়ে যেতে লাগল; আর আমি সেইসব অমর চরিত্রের সান্নিধ্যে বাস করবার অনুভূতির স্বাদ পেতে লাগলাম।
সেই থেকে মহাভারত আমার সবচাইতে পছন্দের গ্রন্থ হয়ে দাঁড়াল। আমি মনে করি এই গ্রন্থটি সর্বকালের শ্রেষ্ঠ রচনা। এই অপূর্ব কাহিনীটি ছাপার অক্ষরে পড়বার যে অদম্য ইচ্ছে আমার মধ্যে জেগেছিল, তার জেরে কয়েক বছরের মাথায় আমি একটা মজার ঘটনায় জড়িয়ে পড়ি। তখন আমি হরিয়ানায় আমাদের গ্রামের ইস্কুলে পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র। এক উর্দু পত্রিকায় সেসময় মাসিক কিস্তিতে মহাভারতের আক্ষরিক অনুবাদ ছাপা হচ্ছিল। আমাদের গ্রামে মাত্র একজন ব্যক্তি সেই পত্রিকাটি রাখতেন, এবং তিনি ছিলেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশ নেওয়া একজন অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক। কিন্তু তিনি নিজের সংগ্রহে থাকা ঐ পত্রিকার সবকটি সংখ্যা নিজের বৈঠকখানায় তালাবন্ধ ক’রে রাখতেন, এবং এমনকী নিজের ছেলেকেও – যে ছিল আমার সহপাঠী – কিছুতেই ওগুলোতে হাত দিতে দিতেন না। আমরা দুজন খুব সাবধানে ঘড়ি ধ’রে সময় মিলিয়ে বৈঠকখানায় ওঁর গতিবিধির উপর নজর রাখতাম, সুযোগ বুঝে ছাদের খিড়কি বেয়ে ঘরে ঢুকতাম, এক এক ক’রে প্রতিটি কিস্তি পড়া শেষ করতাম, তারপর আবার সেগুলো যথাস্থানে রেখে দিয়ে আসতাম। এই চুরি কোনোদিন ধরা পড়েনি।
মহাভারতের যে চরিত্রটি আমার মনের উপর সবচেয়ে গভীর রেখাপাত করেছিল, সেটি নিঃসন্দেহে শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র। তাঁর মহতী বাণী এবং কীর্তি আমায় মোহিত করেছিল। পরবর্তীকালে এই মনোমুগ্ধতা আরও ঘনীভূত হয়ে উপাসনায় পর্যবসিত হয়। তাঁর পুণ্য নাম আমার কাছে হয়ে ওঠে মহামন্ত্র। শ্রীকৃষ্ণ মহাভারত গ্রন্থের ভিত্তিস্বরূপ; তিনিই এই গ্রন্থের আদি, মধ্য এবং অন্ত। একবার একজন জ্ঞানী ব্যক্তি আমায় বলেছিলেন যে আজ পর্যন্ত মানবমন সত্য, সুন্দর, কল্যাণ এবং শক্তির আধার হিসেবে যা কিছু কল্পনা করতে সক্ষম হয়েছে, শ্রীকৃষ্ণ সেই সমস্ত প্রতীকের মধ্যে সর্বোত্তম।
কিন্তু আমি গভীরভাবে আহত-বিস্মিত হই যখন শুনলাম যে আমাদের গ্রামের একজন বিদ্বান ব্যক্তি মহাভারতকে আল্হা-উদলের সমগোত্রীয় বাতলেছেন। তিনি এই বলেও সকলকে সাবধান করতেন যে এই দুই কাহিনী শোনা তো দূরে থাক্, এগুলি নিজেদের সংগ্রহে রাখাও বিপজ্জনক কারণ তাতে নাকি কলহ-বিবাদ তথা রক্তপাত অবশ্যম্ভাবী। আল্হা-উদলও আমার পড়া ছিল; মটরুমল আত্তারের ঝঙ্কারময় কাব্যে রচিত বাহান্ন পর্ব-বিশিষ্ট এই সমরগাথা আমি পুরোটাই প’ড়ে শেষ করেছিলাম। পড়বার পর আমার খুব ক’রে মনে হ’ল যে এই তুলনা একেবারেই উপর-উপর করা, এবং এই দুই গ্রন্থ সংক্রান্ত বিশ্বাসটি নেহাতই কুসংস্কার। উত্তর ভারতের হিন্দুরা মহাভারতকে দীর্ঘকাল ধ’রে অবহেলা করেছে। উত্তর ভারতের জনমানসে মহাভারতকে যে আল্হা-উদলের সঙ্গে একাসনে বসানো হচ্ছে, তাতেই স্পষ্ট হয় এখানকার বৌদ্ধিক এবং সাংস্কৃতিক অধঃপতন কতদূর অব্দি সম্পন্ন হয়েছে।
আমার জীবনকাহিনীর আলোচনায় ফেরা যাক। কলকাতায় থাকতে থাকতেই আমি আরও একখানি মহাগ্রন্থের সঙ্গে প্রথমবারের মত পরিচিত হই, সে গ্রন্থটি হ’ল শ্রী গরীবদাসের গ্রন্থসাহিব। আঠারো শতকের প্রথমার্ধে গরীবদাসের সমসাময়িক আমার এক পূর্বপুরুষ হরিয়ানার এই জাঠ সন্তের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন; সেই থেকে সন্ত গরীবদাস আমাদের পরিবারে কুলগুরু রূপে গণ্য হতে থাকেন। আমাদের কাছে তিনি সদগুরু হিসেবে পূজনীয়, সাক্ষাৎ পরমাত্মার অবতার। সম্পূর্ণ নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও তিনি প্রায় আঠারো হাজার সঙ্খ্যক গভীর ভাবময় কাব্যপঙক্তি রচনা করেছিলেন, যেগুলি আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনার সর্বোচ্চ শিখর স্পর্শ ক’রে রয়েছে। শুনেছি যে এই মহাপুরুষ আমাদের গ্রাম থেকে চার মাইল দূরে বাস করা সত্ত্বেও সকালে তাঁর দর্শন না করা অব্দি আমার ঐ পূর্বপুরুষ জলগ্রহণ করতেন না।
বরোদা থেকে প্রকাশিত হবার ঠিক পরে পরেই আমার বাবা শ্রী গরীবদাস-কৃত গ্রন্থসাহিব-এর প্রথম মুদ্রিত সংস্করণের একখানা কপি জোগাড় করেছিলেন। ঐ গ্রন্থের ‘সাখি’ ও ‘রাগ’-সমূহতে মহাপুরুষগণ এবং পরম ভক্তজনদের জীবনকাহিনীর যে বর্ণনা রয়েছে, তার সাথে নিজস্ব টীকাটিপ্পনী যোগ ক’রে আমার বাবা আমাকে এবং আমার মা-কে প্রায়ই গ্রন্থটি পাঠ ক’রে শোনাতেন। আমিও মাঝেমধ্যে বইটির পাতা উল্টে দেখতাম। তখনও ঐ বইটির মধ্যে লুকোনো নিগূঢ় বক্তব্যসকল বোঝবার মতো মানসিক কাঠামো আমার মধ্যে গ’ড়ে ওঠেনি। তবে কবীর, নানক, রবিদাস, দাদু, নামদেব, চিপ্পা, পিপা, ধন্নাদের মতো মহান সন্তদের কাহিনী আমার মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল – ঠিক যেমনটা করেছিল রাবিয়া, মনসুর, আধম সুলতাম, জুনাইদ, বায়াজিদ ও শামস তাবরেজের মতো সূফী মুসলিমদের কাহিনী। পরবর্তীকালে এই কাহিনীগুলো চিরন্তন সৎসঙ্গের মতো কাজ দিয়েছিল।
সে বছর কলকাতায় থাকতে থাকতেই আমি প্রথমবারের মত স্বাধীনতা সংগ্রামের সংস্পর্শে আসি। সে যুগে আন্দোলন ছিল একেবারে তার চরম পর্যায়ে – লবণ সত্যাগ্রহের সময়। চারপাশে তখন শুধুই মহাত্মা গান্ধী আর ভারতমাতা। মনে আছে বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ দাসের শবযাত্রা নিমতলা ঘাট শ্মশানের দিকে অগ্রসর হবার সময় অগণিত মানুষের সমাবেশ দেখে আমি অঝোরে কেঁদেছিলাম। এর কিছুদিন পরেই ভগত সিংহের মৃত্যুবরণ করবার খবর আসে। আমার দেশ যে পরাধীন সে বিষয়ে আমার মনে একটা অস্পষ্ট ধারণা তৈরি হতে থাকে। মা আমাকে বলেছিলেন যে সাত সমুদ্র পারের কোনো এক রাজ্যের সিংহাসনে আসীন এক রানী আমাদের উপর রাজত্ব করছেন।
কংগ্রেসের আন্দোলন আমাদের গ্রামীণ অঞ্চলে তেমন প্রভাব ফেলতে পারেনি, যেখানে বোলবোলাও ছিল স্যার ছোটু রামের নেতৃত্বাধীন জমিনদারা লীগ-এর। কিন্তু আর্য সমাজের সর্বগ্রাসী আন্দোলন সামনে যা কিছু পাচ্ছিল তা-ই আত্মসাৎ করতে থাকল। ততদিনে গ্রামের প্রায় সমস্ত গণ্যমান্য ব্যক্তিই আর্য সমাজী হয়ে পড়েছিলেন; এঁদের মধ্যে হাফডজন জেলখাটা স্বাধীনতা সংগ্রামীও ছিলেন। আর্য সমাজের প্রচারকর্তা এবং গাইয়ের দল আমাদের গ্রামে প্রায়ই আসা-যাওয়া করতেন। আমি এই প্রচার-বৈঠকগুলিতে উপস্থিত থাকবার জন্য বিশেষ ক’রে সচেষ্ট থাকতাম, এবং এই বৈঠকগুলি প্রায়ই গভীর রাত অব্দি চলত। এঁদের বক্তৃতা এবং ভজনগুলি থেকেই আমি জাতীয়তাবাদের প্রথম পাঠ লাভ করি। এই জাতীয়তাবাদের লক্ষ্য অবশ্য ব্রিটিশ রাজ ছিল না, ছিল মাহমুদ গজনভি, মহম্মদ ঘোরী, আলাউদ্দিন খিলজি এবং ঔরঙ্গজেবের মতো মুসলিম হানাদার তথা স্বৈরাচারী শাসকেরা। এক্ষেত্রে জাতীয় নায়কেরা হলেন পৃথ্বীরাজ চৌহান, মহারাণা প্রতাপ, ছত্রপতি শিবাজী, গুরু গোবিন্দ সিংহ, বান্দা বৈরাগী এবং ভরতপুরের রাজা সুরজমল। মহাভারতের নায়কগণ এবং শ্রী গরীবদাসের গ্রন্থসাহিব-এর সন্ত এবং সূফীদের সঙ্গে এঁরাও আমার ধর্মীয় চেতনার অংশ হয়ে উঠলেন।
গ্রামে থাকাকালীন আমার কৈশোরের দিনগুলোতে যে আর্য সমাজকে দেখেছি, তাতে মূলতঃ তিনটি প্রধান বিষয়বস্তু ছিল, যেগুলোর দিকে লক্ষ্য রেখে ওঁরা নিজেদের অধিকাংশ কার্যক্রম চালাতেন – মুসলমান, সনাতনপন্থী হিন্দু এবং পৌরাণিক গ্রন্থাবলী। মুসলিমদের এমনভাবে উপস্থাপিত করা হ’ত যেন তাদের দ্বারা যাবতীয় ক্ষতিকর কাজকর্ম ব্যতিরেকে অন্য কিছু হওয়া অসম্ভব। সনাতনী ব্রাহ্মণদের দেখানো হ’ত পুরোহিততন্ত্রের ধারক ও বাহক হিসেবে, যারা কিনা মানবজাতিকে ভয়ঙ্কর রকম পথভ্রষ্ট করে থাকে। আর পুরাণগুলিকে দেখানো হ’ত সনাতনী হিন্দুদের মস্তিষ্কপ্রসূত কল্পনা হিসেবে, যেখান থেকেই নাকি হিন্দু সমাজে প্রচলিত যাবতীয় অন্ধবিশ্বাস এবং শিশুসুলভ প্রথাসমূহ উৎপন্ন হয়েছে।
যে মুসলিম হানাদার এবং স্বৈরাচারী শাসকদের কথা আগেই উল্লেখ করেছি তাদেরকে বাদ দিলে অন্য মুসলিমদের প্রতি আমি কখনোই কোনোরকম বিদ্বেষ অনুভব করিনি। যে এলাকায় আমাদের বাড়ি ছিল সেটা মুসলিম তেলিদের পাড়া। তাদের বেশিরভাগই ছিল হিন্দু নামধারী; যেমন শঙ্কর, মোহন ইত্যাদি। তারা হোলি এবং দিওয়ালিতের উৎসবেও অংশ নিত। কেবল তফাৎ ছিল এইটুকু যে তাদের মহিলারা সালওয়ার পরত, যা গ্রামের হিন্দু মহিলাদের বসন ছিল না। আমার মুসলিম প্রতিবেশিরা ছিল শান্তশিষ্ট, ছাপোষা এবং খুবই কর্মঠ প্রকৃতির লোক। আমরা তাদের কাকা-দাদু ব’লে ডাকতাম, ওদের মহিলাদের পিসি-কাকিমা কি দিদা বলতাম। ওদের সম্প্রদায়ের একজন বয়স্ক মানুষ একটা বেশ বড়সড় কিন্তু পরিত্যক্ত হিন্দু হাভেলি-তে একা বাস করতেন। তাঁর চরিত্রটি ছিল বেশ কঠোর, কিন্তু ভালো লাগার মতো। এই মুসলমানদের সম্পর্কে কেউ কখনো সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষমূলক মন্তব্য করে বসলে – যা আকছার করা হ’ত – আমার মোটেই ভালো লাগত না।
ব্রাহ্মণদের প্রতিও আমার সমীহ কখনো একফোঁটাও কমেনি। আমাদের গ্রামে কয়েকজন ব্রাহ্মণ ছিলেন রীতিমতো বিদ্বান পণ্ডিত। বাকিরা চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করেও নিজেদের মর্যাদাসুলভ আচরণের কারণে অন্যের কাছে অতিশয় শ্রদ্ধা আদায় করে নিতেন। এইসব শ্রদ্ধাস্পদ ব্রাহ্মণদের কেউই কিন্তু আর্য সমাজী ছিলেন না। অপর দিকে আমাদের গ্রামে আর্য সমাজের সভাপতির পদটি যে ব্যক্তি অলঙ্কৃত ক’রে ছিলেন, তিনি মোটেই সুবিধের লোক ছিলেন না। তিনি কংগ্রেসেরও সভাপতিত্ব করতেন। ওঁর জীবনের সবচাইতে বড় কীর্তিগুলোর একটি – যা নিয়ে উনি খুব বড়াই করতেন – হচ্ছে গ্রামের মন্দিরের গর্ভগৃহে মলত্যাগ করা। এই চরিত্রটিকে আমি সর্বদা এড়িয়ে চলতাম এবং গ্রামের কোনো রাস্তায় উল্টোদিক দিয়ে এঁকে আসতে দেখলে অনেক সময়েই পিছন ঘুরে প্রত্যাবর্তন করতাম।
তবে আর্য সমাজ কর্তৃক পুরাণসমূহ এবং সনাতনপন্থীদের সমালোচনাগুলি আমি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারেই নিতাম। পৌরাণিক গ্রন্থ এবং সনাতন ধর্ম আমার কাছে নারীসুলভ কোমলতা এবং অনৈতিকতার সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কবীর এবং নানকের নির্গুণ উপাসনা-পরম্পরার অন্তর্গত সন্ত শ্রী গরীবদাসের প্রভাবের ফলে আমাদের পরিবারে চিরাচরিত সনাতন ধর্মের বিশেষ কিছুই আর অবশিষ্ট ছিল না। হ্যাঁ, আমাদের বাড়ির মেয়েরা কয়েকটি ব্রত-উপবাস পালন করত বটে, কিছু আচার-অনুষ্ঠানও মানত, আর মন্দিরে শিবলিঙ্গ দর্শন করতেও যেত। কিন্তু মোটের উপর বাড়ির পুরুষরা মূর্তিপূজার অসারতা সম্পর্কে একপ্রকার নিশ্চিত ছিলেন; এবং তাঁরা সাধারণতঃ কোনো শাস্ত্রীয় আচার-অনুষ্ঠানে অংশ নিতেন না। বিবাহ কিংবা শেষকৃত্যের সময় ছাড়া আমাদের বাড়িতে কখনো ব্রাহ্মণ পুরোহিতের দেখা মিলত না। আমাদের বাড়ির সবচেয়ে বড় ধর্মীয় অনুষ্ঠান ছিল গরীবদাস-পন্থী সাধুগণ কর্তৃক গ্রন্থসাহিব-এর পাঠ। এইসব সময়ে ঐ সাধুরা আমাদের বাড়িতে টানা কয়েক সপ্তাহ ধ’রে থাকতেন। আমার পরিষ্কার মনে আছে যে আমি নিজের নির্গুণ মতের বিষয়ে খুবই উচ্চ ধারণা পোষণ করতাম; আর আমার যেসব সনাতন হিন্দু সহপাঠী ছিল তাদের মত ও পথ-কে নারীসুলভ দুর্বল মনে ক’রে নীচু নজরে দেখতাম। এদের যে ব্যাপারটা আমার বিশেষ অপছন্দ ছিল তা হ’ল দেবীপূজার সময় কাছের একটি শহরে অনুষ্ঠিত বাৎসরিক মেলায় অংশ নিতে যাওয়া। তখন আমার কাছে ঈশ্বর মানেই একজন পুরুষ সত্তা। আমি মনে করতাম যে দেবীর আরাধনা সত্য ধর্মপথকে কলুষিত করে মাত্র।
পৌরাণিক সাহিত্যের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়ের ঘটনাটি মনে করলে আজও আমি হাসি সংবরণ করতে পারিনা। সে সময় আমাদের গ্রামে লোকে সাকুল্যে একটিই পুরাণের কথা জানত এবং গ্রামে কেবল সেটিই পাওয়া যেত – শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ। সে পুরাণখানি প’ড়ে দেখবার জন্য আমার মধ্যে রোখ চেপে গেল। কিন্তু আমার মনে সারাক্ষণ এই ভয় লেগে ছিল যে সে কাজটি করবার সময় আমায় কেউ দেখে ফেলতে পারে। এর বেশ কয়েক বছর বাদে গ্রাম ছেড়ে দিল্লীর একটি স্কুলে ভর্তি হবার পর আমি সেখানকার একটি হরিজন আশ্রম থেকে শ্রীমদ্ভাগবত-এর একখানি কপি ধার ক’রে চোরের মত লুকিয়ে লুকিয়ে বাড়ি নিয়ে আসি। বইটি পড়বার সময় আমি বেশ তক্কে তক্কে ছিলাম, যাতে কেউ আমায় এই আনন্দটি উপভোগ করবার সময় দেখে ফেলে চারদিকে খবরটা রটিয়ে না দেয়। যাইহোক, বইটি প’ড়ে আমার একটুও বিবমিষা জাগেনি; শুধু ওতে বর্ণিত কয়েকটি গল্প অতিরঞ্জিত মনে হয়েছে এই যা। তবে সবমিলিয়ে বইটি আমায় সেভাবে মুগ্ধ করতে পারেনি। মহাভারত-এর শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র আমার মনে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হয়ে ছিল। ভাগবত-এ তাঁকে আমি খুঁজে পাইনি। গোপীদের সঙ্গে তাঁর লীলা আমায় নাড়া দেয়নি। যাইহোক, এর অনেক বছর বাদে আমি শেষ অব্দি উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম যে পৌরাণিক সাহিত্য সেই একই প্রাসাদোপম বৈদিক আধ্যাত্মিকতার অবিচ্ছেদ্য অংশ যার মুকুটমণি হচ্ছে মহাভারত।
আর্য সমাজে আনাগোনার কারণে আমি ক্রমে আমাদের গ্রামে সদ্যস্থাপিত হরিজন আশ্রমের সংস্পর্শে এলাম। আমি তখন দিল্লীতে হাইস্কুলের ছাত্র। গরমের ছুটিতে গ্রামে থাকাকালীন এক বন্ধু আমায় একটি পংক্তিভোজনে যোগ দিতে বলে, যেখানে হরিজনদের দ্বারা বর্ণহিন্দুদের পায়েস পরিবেশন ক’রে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আমি হরিজন আশ্রমে গিয়ে দেখতে পেলাম যে আমাদের গ্রামের প্রায় সমস্ত আলোকপ্রাপ্ত গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সেখানে সমবেত হয়েছেন। আমি ওঁদের সঙ্গে খেতে বসিনি, কারণ যে হরিজনরা পরিবেশন করছিলেন আর যে বর্ণহিন্দুরা খাচ্ছিলেন তাঁদের সকলেই ঐ প্রখর গরমের দুপুরে দরদর ক’রে ঘামছিলেন। কিন্তু সেখান থেকে বেরিয়ে আসার পরে যখন কিছু গোঁড়া লোকজন আমার কাছে জানতে চাইল যে আমি “চামার”দের দ্বারা পরিবেশিত অন্ন গ্রহণ করেছি কিনা, তখন আমি আর “না” বলিনি। ভেতরে ভেতরে আমার আফশোস হচ্ছিল – যে কাজকে সঠিক এবং উচিত ব’লে বুঝেছি, শুধুমাত্র নিজের স্বাস্থ্যসচেতনতার বাড়াবাড়ির কারণে তা করা থেকে নিরত থাকলাম!
হয়তো এই অপরাধবোধ আমার মনে কাজ করছিল ব’লেই এই ঘটনার কিছুদিনের মধ্যে আমি ফের হরিজন আশ্রমে গিয়ে উপস্থিত হলাম। আশ্রমের যিনি আধিকারিক তিনি ছিলেন আমার আপন জাতের লোক – একজন প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী যিনি বেশ কয়েকবার দীর্ঘ সময়ের জন্য জেল খেটেছিলেন। তিনি ছিলেন দৃঢ় চরিত্রের অধিকারী, এবং হরিজন সমাজের উন্নতিসাধনের লক্ষ্যে নিবেদিতপ্রাণ। কেউ কোনো বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে গেলে তিনি কোনো না কোনো ভাবে সেই আলোচনার মধ্যে হরিজনদের সমস্যার প্রসঙ্গ না তুলে ছাড়তেন না। তাঁর তিরিক্ষি মেজাজ এবং মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে যেসব বিষয়ের যোগ তিনি দেখতে পেতেন না সে সমস্তকিছুর ব্যাপারে তাঁর প্রবল অনীহা সত্ত্বেও তিনি আমার উপর গভীর প্রভাব ফেলেছিলেন। তাঁকে যখন হরিজন বালকদের দেখাশোনা করতে দেখতাম, তখন মনে হ’ত যেন হরিজনদের উন্নতিকল্পে তাঁর আত্মোৎসর্গের মাত্রাটি মহাত্মা গান্ধীর প্রতি তাঁর ভক্তিকেও ছাপিয়ে গেছে।
এঁর কাছ থেকেই আমি জানতে পারি যে আর্য সমাজ নয়, বরং মহাত্মা গান্ধীর হরিজন-উদ্ধার আন্দোলনকারীরাই ঐ পংক্তিভোজনটির আয়োজন করেছিলেন। তিনি যখন আরও জানালেন যে মহাত্মা গান্ধী আর্য সমাজী নন, বরং সনাতনপন্থী হিন্দু, তখন আমি শুধু অবাক হয়েছিলাম বললে কম বলা হবে – রীতিমতো স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিলাম। ইনি নিজেও আর্য সমাজের মত ও পন্থা ছেড়ে বেরিয়ে মহাত্মা গান্ধী অনুমোদিত উপাসনাপদ্ধতি ও মতাবলম্বী হয়েছিলেন। এই সত্য আমার কাছে প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে আমি বড় দোটানার মধ্যে পড়ে গেলাম। তখন পর্যন্ত আর্য সমাজ সম্পর্কে আমার যা কিছু জ্ঞান সেটুকু গ্রামে এই সংস্থার প্রচারকদের কাছে যা কিছু শুনেছিলাম তার মধ্যেই সীমিত ছিল। মহাত্মা গান্ধীর মত ও পন্থা সম্পর্কে তো আরোই কম জানতাম। কিন্তু সে সময় আমার দৃঢ় ধারণা ছিল যে সনাতনপন্থী হিন্দু হওয়া একরকম চরম নিন্দার্হ ব্যাপার। তাহলে মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় একজন মহৎ ব্যক্তিত্ব সনাতন ধর্মাবলম্বী হতে পারেন কীভাবে? এদিকে তাঁকে আমি আমার সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে শ্রদ্ধা করতাম। বিগত কয়েক বছর ধরেই তাঁর নামে আমি জয়ধ্বনি শুনে এবং দিয়ে আসছিলাম।
ভাগ্যক্রমে, এর কিছুদিন পর আমার তরফ থেকে বিশেষ কোনো বৌদ্ধিক আয়াস ছাড়াই এই দোটানাটি কেটে যায়। আমার সমকালীন কিন্তু বয়সে সামান্য ছোট এক যুবা, যে প্রতিদিন আমার কাছে পাঠ নিতে আসত, আমাকে একদিন জানায় যে জেলার সদর শহরে অবস্থিত তার স্কুলের লাইব্রেরি থেকে সে যেসব বই ধার করেছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে সত্যার্থ প্রকাশ। আর্য সমাজের এই গ্রন্থ-শিরোমণিটি আমাদের গ্রামের কয়েকজনের ব্যক্তিগত সংগ্রহে এবং দিল্লীর লাইব্রেরিগুলোতে সহজেই মিলত। তা সত্ত্বেও নিজের মধ্যে এই বইটির প্রতি কোনোরকম আগ্রহ আমি টের পাইনি। এখন হঠাৎ ক’রে এই বইটি পড়বার এবং এতে কি আছে তা জানার জন্য আমার মধ্যে প্রবল ঔৎসুক্য দেখা দিল।
সত্যার্থ প্রকাশ-এ নানান বিষয়ের উপর যেসব পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা রয়েছে, সেগুলি প’ড়ে আমার ঠিক কি কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা আর এতদিন বাদে আমার মনে নেই। কিন্তু আমার খুব স্পষ্ট মনে আছে যে ঐ বইটিতে কবীর এবং নানক সম্পর্কে যেসব মন্তব্য করা হয়েছে, সেগুলি প’ড়ে আমি কীরকম মর্মাহত হয়েছিলাম। আমার মধ্যে ধর্মীয় চেতনা প্রথমবারের মতো পরিস্ফুট হবার সময় থেকেই যে পবিত্র নামগুলি আমি সবচাইতে বেশি ভক্তিভ’রে মনের মধ্যে লালন করে এসেছি তার মধ্যে অন্যতম ছিল এই দুই নাম। আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে স্বামী দয়ানন্দ এই দুই মহান সন্তের প্রতি প্রয়োজনের অতিরিক্ত নির্দয় মতামত পোষণ করতেন, এবং তাঁর মত ভ্রান্ত। তখনকার মত এইখানেই আর্য সমাজের ব্যাপারে আমার মোহভঙ্গ ঘটে। এর বহু বছর বাদে যখন আমি শ্রীঅরবিন্দ রচিত বঙ্কিম, তিলক, দয়ানন্দ শীর্ষক রচনাটি পাঠ করি, তখন অনুশোচনায় এবং নবজাগ্রত শ্রদ্ধায় ফের আমি সেই পুরুষসিংহের সামনে নতমস্তক হই, যিনি বৈদিক দৃষ্টিভঙ্গিকে উদ্ধার করতে এবং হিন্দুদের মধ্যে তা পুনরুজ্জীবিত করতে যথাসাধ্য প্রয়াস করেছিলেন। একই সময়ে, আমাদের জাতির জীবনের এক সঙ্কটময় সন্ধিক্ষণে আর্য সমাজ যে গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক ভূমিকা পালন করেছিলেন তার ঠিক ঠিক উপলব্ধি এবং কদর আমার নিকট প্রতিভাত হয়।
পাদটীকা
এই মুখবন্ধটির রচনাকাল হ’ল ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দ।
মূল গ্রন্থের রচয়িতা: সীতারাম গোয়েল
বঙ্গানুবাদ : শ্রীবিজয়াদিত্য