আপনি বাম অপশাসন থেকে পরিত্রাণ চেয়েছিলেন। পাড়ায় পাড়ায় লেনিন মার্ক্সের ছবি ঝোলানো অফিস থেকে নির্দেশ আসত আপনার বাড়িতে কে ভাড়া আসবে, আপনার জমি কে চাষ করবে, ছেলে কোথায় চাকরি করবে। পরিবর্তনে আপনি পেয়ে গেলেন সততার সরকার। স্কুলে চাকরি? টাকা ফেলুন হয়ে যাবে। মেয়ের কলেজে ভর্তি? সেও টাকা ফেললেই হয়ে যাবে। পশ্চিমবঙ্গে সব কিছু, এমন কী সততার সার্টিফিকেটও কিছু টাকা ফেললেই পাওয়া যাচ্ছে। প্রমাণ চাইবেন না, প্লিজ। প্রমাণ দিতে পারব না। তবে সরকারী, আধাসরকারী অফিসে গত দশবছরে নিয়োগ, নানান কাজ কীভাবে হচ্ছে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা যাদের আছে তারা প্রমাণের তোয়াক্কা করে না। তাদের কঠিন পথে এ সত্য জানতে হয়েছে।
সত্যমেব জয়তে।
একটি মুসু মুসু কালেজীয় কেচ্ছা (১)
কন্যারত্নম পেত্থমে ব্যারাকপুর রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজে জার্নালিজম অ্যান্ড মাস কমিউনিকেশন-এ ভর্তি হয়েছিল। অনলাইনীয় কাজ কারবার। পেরায় দশ হাজার টাকা গলে গেলো। দাঁও যে কে মারছে, না কি এখন এমনই— মানে দরাদরি তো করা যায় না,
শিক্ষার দামটা বেশিই পড়ে যাচ্ছে, না কি, বুঝতে পারলাম না।
আমরা অসহায় গাজ্জেন। পোলাপাইনের ভবিষ্যৎ-ভাবিত ছাপোষা আহাম্মক। যে যেমন চায়, পুত্রকন্যা হিতার্থে, পারলে সেইটেই কবুল করি।
তো, এই প্যানডেমিক প্যান্ডামোনিয়াম-কালে মেয়ের ‘গতি’ করে খানিক নিশ্চিন্তি। এবার পুত্তুরের পরীক্ষা, তেনার রেজাল্ট সমাচার, তেনার ভর্তি— ব্যস্ত হয়ে পড়লাম, সঙ্গে জীবিকা বিড়ম্বনা— সসেমিরে অবস্থা।
এবার, পুজোর আগ দিয়ে রাত আটটা নাগাদ একটা ফোন এলো। ফোনের গলাটি খুব ব্যস্ত, উদ্বিগ্ন।
মেয়ের নাম ধরে হ্যালো হ্যালো করে বললো, কন্ঠস্বরের মালিক রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ থেকে ফোন করছে। খুবই সধমকে লোকটি বললো, রেজিস্ট্রেশন করিয়েছেন?
ধমকে ঘাবড়ে গিয়ে মিনমিন করে বললাম, ওয়েবসাইটে সেরকম কোনো ইনস্ট্রাকশন পাই নি তো!
আমরা ক্যান্ডিটেটকে মেইল করেছি। আপনারা পান নি?
করোনা কালে এমনিতেই মাথা ভোম্বল, ছোকরার ধমকধামকে আরো আউলে গেলাম! কন্ঠ আবার খুব কমান্ডিং টোনে বললো,
আজকের মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করান। নইলে অ্যাডমিশন ক্যানসেল হয়ে যাবে।
শুনে কপালে ঘাম, মাথা ভনভন, বুক ধুকপুক— বলে কী রে!
ধড়ফড় করে সাইবার ক্যাফে-তে দৌড়ালাম। কম্পুমুখো মানুষটি একটু অবাক,
রেজিস্ট্রেশন! আন্ডার গ্রাজুয়েট-এর? এখন কী!
বলেই ওয়েবসাইটে ঢু মারলো,
দেখতে দেখতে আনমনে বললো,
সে রকম কোনো নোটিশ নেই তো!
বলে, ঝুঁকে পড়ে কী একটা দেখতে দেখতে একটু ইনকফিডেন্ট— একটা লিঙ্ক অবশ্য আছে— আপনার কার্ড আছে তো?
আছে।
তারপর সদাশয় কম্পুমুখো যুবক খুটুরখাটুর করে কীসব করে টরে আমায় বললো,
পাঁচশ সত্তর।
রেজিস্ট্রেশন ফি?
হ্যাঁ।
আরো কিছু টঙ্কা খসি গেলা!
এগারোই ডিসেম্বর। এবার এলো ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশন। আমি অবাক। স্কুল কলেজ না খোলার নিদান হাঁকা হয়েছে, এই বাজারে সশরীরে যেতে লাগবে!
কিন্তু কত্তা থুড়ি কালেজীয় হুকুম, যেতে তো হবেই।
যদিও টুকটাক খোঁজ খবর করে বুঝলাম, আর কোনো কলেজেই ওই এগারোই ডিসেম্বরের আগে পরে ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশন হচ্ছে না।
একটু অবাক, সন্দিহান—
কিন্তু,
যেতে তো হবেই।
গেলাম। মার্কশিটের পিছনে স্ট্যাম্পো পড়িলো।
করোনা দশায় গাজ্জেনরা কলেজ গেট ক্রস করতে পারবেন না। শুদ্ধু এস্টুডনরা ভেতরে এন্ট্রি নেবে। কাজেই বালবাচ্চা ভেতরে গেলো, আমরা, আহাম্মক বাপ-মায়েরা তির্থের কাক হয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে রইলাম।
দাঁড়িয়েই আছি।
মাঝেমধ্যেই ছানারা ঘাবড়ে যাওয়া মুখে আসছে। বিনবিন মিনমিন করে বাপ মায়ের সঙ্গে কথা কইছে, আবার ভেতরে চলে যাচ্ছে।
আমি অধৈর্য। এতো কী! এতো কিসের সময় লাগে রে বাপু!
এমন সময় কন্যাটি ঘামলাল মুখে বাইরে এলো।
“মা, পাঁচশ কি হাজার টাকা হবে!”
“কেন বল তো!”
“লাগবে। সবাই দিচ্ছে।”
“কী বাবদে! পাঁচশ, না হাজার!”
মেয়ে একটু ফ্যালফ্যালে মুখে বললো, “যে যেমন পারছে—“
আমার নাকের ডগা নড়ে উঠলো। যে যেমন পারছে! এ আবার কেমন কথা! চল তো দেখি!
কিন্তু, দেখার উপায় নাই। আমার টাকায় করোনা নাই। কিন্তু আমিই তো করোনা ভাইরাস? গাজ্জেনদের গায়ে পায়ে থিকথিকে করোনা। হুমদো হামদা মেহেন্দিচুলো মাস্কায়িত কাকুরা ঢুকতে দিলো না।
মেয়েকে ফোন লাগালাম।
কথা বলে বুঝলাম, ওইটে ইউনিয়ন-নৈবদ্য। পাঁচশ আটশ হাজার— যে যেমন পারে।
মানে, পারতে তো হবেই। না পারা পজ্জন্ত মার্কশিট, আধার কার্ড, মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিকের রেজিস্ট্রেশন কার্ড ফেরত পাবে না।
এইবার মাইকবিহীন অমায়িকতায় চিল্লানো শুরু করলাম। গেটের এপারে আমি রাধা, ওপারে গুচ্ছ গুচ্ছ মাস্কমুখো শ্যাম।
প্রিন্সিপালের নম্বরে ফোন করলাম। বরাহ-ঘোঁতঘোঁত সহ তিনি জানালেন, কলেজ থেকে আঠারো কিমি দূরে বসে তিনি কিছুই করতে পারবেন না। এবং, ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশন বলে কিছু না কি তাঁর কলেজে হচ্ছেই না।
ভাবুন!
তাহলে কী হচ্ছে? আমাদের এতো জনকে ডেকে আনা হয়েছে কেন! মার্কশিটে স্ট্যাম্প পড়ছে? কারা দিচ্ছে?
কারা আটকাচ্ছে মার্কশিট?
আবার মেয়েকে ফোন করলাম। জানলাম, এখনো কাগজপত্র কিছু পায়নি।
অর্থাৎ আমার হাত পা বাঁধা। তবু চেঁচানো অব্যাহত রাখলাম। বারবার জিজ্ঞেস করলাম, এই টাকা কেন, কী হেতু দিতে হবে। এর কোনো নোটিফিকেশন কলেজ ওয়েবসাইটে নেই কেন?
এবার অন্য গার্জিয়ানরাও এগিয়ে এলেন। বিষয়টা যে পরিচ্ছন্ন নয়, এটা বুঝতে খুব বেশী বুদ্ধি লাগে না। কিন্তু আমরা, কিছুটা অসহায়। বাচ্চাদের কাগজ পত্র যতক্ষণ না ফেরত পাচ্ছি, ততক্ষণ খুব কিছু করা—
যাই হোক,
পেল্লায় চিল্লামিল্লির পর কাকুদের ডিমান্ড কমলো। পাঁচশ।
পাঁচশ তাদের দিতেই হবে।
এবং, আমরা দিলাম।
উইদাউট রিসিট, দিলাম। পাঁচশ।
করোনা ক্রান্তিকালের আপোষ।
(চলবে)
একটি মুসু মুসু কালেজীয় কেচ্ছা (২)
চোদ্দই ডিসেম্বর। ২০২০। যাদবপুরের আরো একটি মেধা তালিকা বের হল। কন্যারত্নম তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে অবশেষে— অবশেষে চান্স পেলেন। সেদিন রাত্রেই নাচতে নাচতে কইন্যা আমার যদুবংশীয় হয়ে গেলেন।
না হে। ভর্তির আর্থিক চাপ কমই।
গরীব ইউনিভার্সিটির ভর্তি খরচা মাত্তর এক হাজার একশত পঞ্চাশ টাকা।
সে বড়ো আনন্দের রাত। খুশিয়াল রজনী।
কিন্তু,
খুচখুচে একটা অস্বস্তি তো ছিলোই। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজের ওই স্ট্যাম্প, হিজিবিজি স্বাক্ষর যতক্ষণ না নাকচ হচ্ছে—
আমার ট্রান্সফার সার্টিফিকেট চাই।
চাই তো। কিন্তু দিচ্ছে কে!
সকাল দুপুর বিকাল সন্ধ্যা— কলেজ এবং দক্ষিণ বঙ্গ স্টেট ইউনিভার্সিটির এগারোটি ফোন নম্বরে লাগাতার ফোন করে গিয়েছি। একটা ফোনও কেউ রিসিভ করে না।
এদিকে যাদবপুরে জোরকদমে ক্লাস শুরু হয়ে গিয়েছে। সকাল এগারোটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত অনলাইনীয় ক্লাস।
এখানেও ভেরিফিকেশন হল।
অনলাইনে মার্কশিট, নাম্বার, ছবিছাবা মেলানো হল।
ব্যস।
কিন্তু, সেই সঙ্গে এটাও বলে দেওয়া হলো, ফার্স্ট সেমিস্টারের আগে যখন রেজিস্ট্রেশন হবে, তখন হয়তো ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশন হবে।
কী চাপ! আমার মেয়ের তো টিসি লাগবেই। তার মার্কশিটের পশ্চাদ্দেশে স্ট্যাম্পো আছে।
এবার মরীয়া হয়ে মাননীয় প্রিন্সিপাল মহাশয়ের ফোন নম্বরে ফোন করেছি।
এই নম্বরটিও ওয়েবসাইট থেকেই পাওয়া। নইলে তিনি আমার কুটুম্ব নন কিছু, যে নম্বরটি আমার কাছে থাকবে।
একান্ত নিরুপায় হয়েই তাঁকে ফোন করি, শুধু কলেজটি এই করোনা ডামাডোলে খোলা আছে কি না, এইটুকু জানতে।
কিন্তু তাঁর কাছ থেকে অভদ্র বিকট চিৎকার ছাড়া কিছুই শুনতে পাই নি। “আঠারো কিমি দূরে বসে”— এটা ভদ্রলোকের পেটেন্ট বুলি,
“আপনি আমাকে ফোন করছেন! কোত্থেকে আমার প্রাইভেট নাম্বার আপনি পেলেন? আপনার সাহস তো কম নয়! আঠারো কিমি দূরে বসে কলেজ খোলা আছে কি না, আমি বলবো?”
ফোন করা যে ‘এতো সাহসের’ ব্যাপার, এইটে জেনে খানিক ক্যাবলা হয়ে ফোন মুঠোয় দাঁড়িয়ে রইলাম।
অতঃপর সশরীরে তিনবার কলেজে যাওয়া।
কলেজ গেটে তালা।
অথচ ভেতরে হুমদো দাদারা দিব্য ঘুরছে। আমার মতন আরো কয়েকজন অভিভাবক, কিছু ছাত্রের সঙ্গে দেখা হয়েছে, যারা আমার মতোই হাপৃত্যেশ করে, লোহার গেটে নাক ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।
দাঁড়িয়ে থেকে থেকে একই উত্তর তিন দিন পেয়েছি,
“অফিস বলছে অফিস খোলা নেই।”
এবং, প্রত্যেক বার মাতব্বর হুমদো কাকুরা খর চোখে আমাকে মেপে নিয়েছে,
হাল্লা মাচানো থোবড়াটিকে এতো তাড়াতাড়ি ভুলবে, তা তো হতেই পারে না, না!
মরীয়া হয়ে চার জানুয়ারি আবার কলেজ গেলাম। বিশ পেরিয়ে একুশ।
এবার কলেজ খোলা। মাচো দাদারা ঘুরিতেছে। পতাকা উড়িতেছে সগৌরবে।
আমারই মতন জনা ছয়েক ট্রান্সফার-ইচ্ছুক আবোদা গাজ্জেন ফ্যালফেলিয়ে ঘুরছেন। কারণ, কেউই বলতে পারছে না, ওই পরম প্রার্থিত টিসি-টি কোন কাউন্টারে কোন পদ্ধতিতে পাওয়া যাবে।
ভাবখান এমন, যেন কেউ কোনোদিন এই কলেজ থেকে টিসি নেয়ই নি!
এগারোটা থেকে একটা,
শুধু এক থেকে পাঁচ নম্বর কাউন্টারে ঘোরা, খেপে খেপে লম্বা লাইনে দাঁড়ানো—
বার কয়েক ভেতর বাগের দরজা দিয়ে ‘অ্যাকাউন্ট’ নামক ঘরে যাওয়া।
প্রচুর লোক মুখোশ এঁটে রুমালে হাত মুছতে মুছতে ঘুরছে ফিরছে। খুবই ছুটি ছুটি মুড। চেয়ার ফাঁকা। বাইরে লম্বা লাইন, যে লাইন কেবল বেড়েই যাচ্ছে।
অবশেষে, একটি হুমদো কাছে এলেন। খুবই রোয়াবে বললেন, “এখন বুঝছেন তো, আমরা কত দরকারি?”
আমিও খুব গম্ভীরসে বললাম,
“বুঝলাম।
তো, ওই পাঁচশ-তে তোমরা ভাই কী কী কাজ করে থাকো?”
ততক্ষণে আমার পেছনে আরো দুজন অভিভাবক দাঁড়িয়েছেন। ভীষন বিনয়ে, ভীষন কাকুতি মিনতি করে তাঁদের একজন বললেন,
“ভাই, আমরা তো সেদিন কোনো ঝামেলা করিনি। আপনারা যা চেয়েছেন, তাই দিয়ে দিয়েছি, আমাদের ব্যাপারটা একটু দেখুন না!”
বিনয় বচনে গলে, আবার আমাকে মাপতে মাপতে মাতব্বর হেলায় ফেলায় অভিভাবকদের বললেন,
“আমার পেছন পেছন আসুন।”
আমিও পেছন পেছন গেলাম।
একশ টাকার বিনিময়ে একটি স্ট্যাম্প সম্বলিত কাগজ পেলাম, যেখানে ‘টিসি ফি’ লেখা আছে।
আবার লাইনে দাঁড়ানো। আবার একটু একটু করে কাউন্টারের কাছে এগনো।
কাউন্টারে পৌঁছে স্লিপটি বাড়িয়ে দেওয়া—
কাউন্টারের ওপারের ভদ্রলোক ভীষন ভুরু কুঁচকে ভীষন মনোযোগে ওই এক চিলতে কাগজ দেখতে থাকলেন। দেখতেই থাকলেন, যেন ওটা ইংরেজি নয়, সিন্ধুলিপি।
তারপর ঠোঁট চোখা করে বললেন, “কী ব্যাপার?”
“ট্রান্সফার সার্টিফিকেট—“
ভদ্রলোক তখনো চোখ গোল করে তাকিয়ে আছেন দেখে খোলসা হলাম,
“আসলে, আমার মেয়ে এখানে জার্নালিজম অ্যান্ড মাস কমিউনিকেশন-এ ভর্তি হয়েছিলো। এখন অন্য জায়গায় ভর্তি হয়েছে। তাই—“
“অনলাইনে ভর্তি হয়েছে?”
আমি তো বোকা! এ আবার কেমন প্রশ্ন! ভর্তি তো অনলাইনেই! হাঁদা হাঁদা মুখ করে বললাম, “হ্যাঁ!”
“তাহলে আর অসুবিধা কী? ট্রান্সফার নেবার কী আছে?”
পেছনে, একই কারণে আসা অভিভাবকটি এবার পারলে কাউন্টার ডিঙিয়ে ওঁর পায়েই পড়ে যায় আর কী!
হাহাকার করে বললেন,
“তা কী করে হবে! মার্কশিটে তো এই কলেজের ছাপ পড়ে গেছে!”
কাউন্টারের ওপারের ভদ্রলোক ভীষন ভাবিত হলেন।
“ছাপ পড়ে গেছে? ওহহ্!”
তারপর অনেক ভেবে টেবে বললেন, “মার্কশিট এনেছেন?”
অভিভাবক: “হ্যাঁ হ্যাঁ। এইত্তো!”
আবার ওপ্রান্তের ভদ্রলোক উঠে গেলেন। ঘুরলেন ফিরলেন। রুমাল টুমালে হাত মুছলেন। তারপর ধীরে সুস্থে বসে খুব বেজার মুখে বললেন,
“পরিশ্রমের কাজ, বুঝলেন! ছাপ পড়ে গেছে! তুলতে হবে—
আচ্ছা।
লাঞ্চ আওয়ারের পর আসুন। দেখি, কী করা যায়।”
আমরা, ফান্দে পড়া বগার দল ল্যাগোর ব্যাগোর করতে করতে বাঁধানো বেঞ্চিতে বসে পড়লাম। তখন বেলা আড়াইটা।
(চলবে)
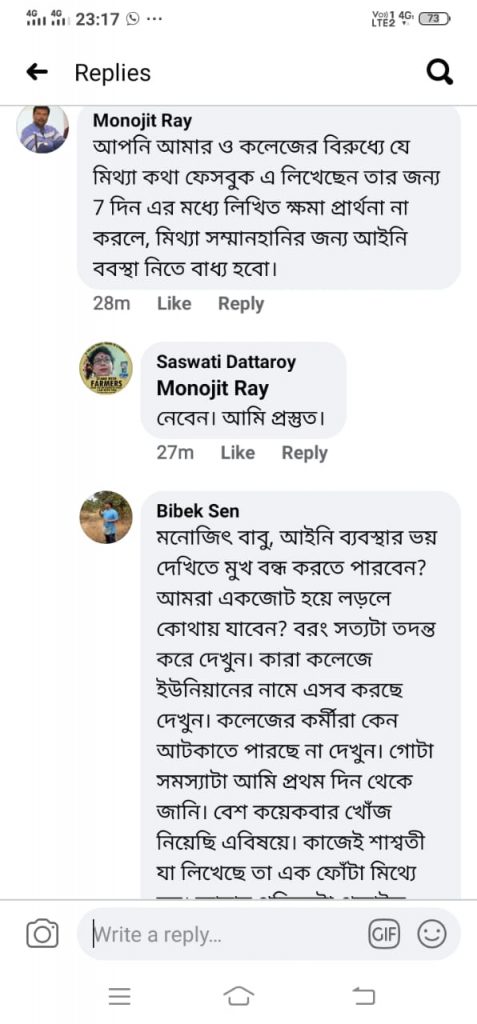
একটি মুসু মুসু কালেজীয় কেচ্ছা (৩)
এক ঘন্টা খানেক পর বাবুরা আবার রুমালে মুখ টুখ মুছে চেয়ারে বসলেন। আমরা ওই জনা ছয়েক আবার কাউন্টারের সামনে দাঁড়ালাম।
ভদ্রলোক খুবই অলস ভাবে আমাদের দেখলেন। যেন আমাদের এখানে থাকার কথাই নয়! খুব বিরক্ত হয়ে বললেন,
“আপনারা এখনো যান নি?”
আমার আগের অভিভাবক ডুকরে উঠলেন, “যাবো কি স্যর, আমার টিসিটা? আপনি এখন আসতে বলেছিলেন!”
“ও। প্রিন্সিপাল তো এখন নেই। মিটিং-এ ব্যস্ত।”
“কখন ফিরবেন!”
খুব নির্বিকার গলায় উত্তর এলো,
“কখন ফিরবেন বলা যাচ্ছে না। নাও ফিরতে পারেন।”
চুপচাপ পেছনে দাঁড়িয়ে আছি। কথোপকথন শুনছি। চোয়াল শক্ত হচ্ছে। কিন্তু কিচ্ছু করার নেই। কাউন্টারের এপারে দাঁড়ালে নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই প্রতীক্ষমানা শবরী অহল্যা।
সেই আটটায় খেয়ে বেরিয়েছি। শরীর ঝিমঝিম করছে। একজন কৃষ্ণনগর থেকে এসেছেন, আমার থেকেও আগে বাড়ী থেকে বেরিয়েছেন। সুগারের পেশেন্ট। উৎকন্ঠা উদ্বেগে ওই শীতেও ঘামছেন।
খুব উদ্বিগ্ন ভাবে আমাকে বললেন,
“ম্যাডাম, ভর্তির টাকাটা ফেরত পাওয়া যাবে? কিছু জানেন?
অনেকগুলো টাকা!”
আমাকে টপকে আর এক অভিভাবক হতাশ ভাবে বললেন,
“রিফাআআন্ড!
ওসব ভুলে যান দাদা। মানে মানে এই টিসিটা পেলে বাঁচি!”
আমি একটু উৎসুক ভাবে বললাম, “রিফান্ড চেয়ে দেখেছেন? অ্যাপ্লিকেশন করেন নি?”
কৃষ্ণনগরের অভিভাবক বললেন, তিনি অ্যাপ্লিকেশন জমা দিয়েছেন। আগে টিসি হোক। তারপর বাকিটা দেখা যাবে।
যদিও, বেশ বুঝছিলাম, একবার এই তল্লাট থেকে বেরোতে পারলে আমরা আর কেউই দ্বিতীয় বার এখানে আসবো না।
অবশেষে বহু প্রতীক্ষিত সেই মধু লগন!
চারটে নাগাদ আমার টার্ন এলো। মার্কশিট, আধার কার্ড, বার্থ সার্টিফিকেট, মাধ্যমিকের রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট সব আবার জমা পড়লো।
মার্কশিট ছাড়া অন্য কাগজপত্র ঠিক কোন কাজে লাগবে, অনেক মাথা ঘামিয়েও বুঝে উঠতে পারছিলাম না।
তবে তখন মাথা আর বিশেষ কাজও করছিলো না।
আমার আগের ভদ্রলোক অবশেষে টিসি পেলেন।
তারপর আমি।
মন দিয়ে মার্কশিটের পেছন দেখলাম। টিসি ইস্যুড। তলায় খুব আবছা স্ট্যাম্প।
একটা সই। দেখে মনে হচ্ছে, মোম গলে পড়েছে। ইনিশিয়ালেরও মাইক্রোস্কোপিক ব্যাপার।
চুপচাপ গুণে গুণে সব কাগজপত্র ফেরত নিলাম। “তাহলে, টিসি হল তো?”
ওপারের ভদ্রলোক একটা হাতের কায়দা করলেন। বরাভয়, কিম্বা ‘আরে দাড়ান’— দুটোই হতে পারে।
আবার খানিক ক্ষণ দাঁড়াবার পর দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে একটা চোতা কাগজ। ওইটেই টিসি।
মেয়ের নামের বানান যথারীতি ভুল। এতো আধার কার্ড বার্থ সার্টিফিকেট নিয়েও বানান ভুল হয় কী করে,
আশ্চর্য বাবা!
যাগ্গে।
আবার সব মন দিয়ে মেলালাম। নাঃ। সব ঠিকঠাক ফেরত নিয়েছি। যাক বাবা!
সকন্যা পেছন ফিরছি,
একজন অভিভাবক ডাকলেন।
“ম্যাডাম, মাইগ্রেশন সার্টিফিকেটও লাগবে তো! আপনি ওটা পেয়েছেন?”
ওহ্! তাও তো বটে!
আবার কাউন্টারে দাঁড়ালাম। তখন আর এক অভিভাবকের সঙ্গে তর্ক হচ্ছে। বিষয়: টাকা রিফান্ড।
হুমদো এবং মামদোদের বক্তব্য, যেহেতু রেজিস্ট্রেশন হয়ে গিয়েছে, সেহেতু আর টাকা ফেরত পাওয়া যাবে না।
খুবই ক্লান্ত, তবুও আমার লম্বা নাক একটু গলিয়ে দিলাম। রেজিস্ট্রেশন হয়েছে! তাহলে রেজিস্ট্রেশন নম্বরটা কই?
(আগামীতে শেষ পর্ব। কাল দেবো।)
একটি মুসু মুসু কালেজীয় কেচ্ছা (৪)
গিয়েছিলাম সকালের রোদ মেখে। সারা দুপুর ঠা ঠা রোদে পুড়ে ক্লান্ত। যখন হাজার গন্ডা ওভার-রাইটিং ওয়ালা টিসি-র কাগজ অবশেষে হাতে পেলাম, তখন ব্যারাকপুরের রাস্তাঘাতে ইলেকট্রিক আলো টালো জ্বলে গিয়েছে।
কাকু হুমদোদের ঘন্টাখানেক দেখিনি। কচি হুমদোরা আমাদের পাহারা দিচ্ছিলো। আর মাঝেমধ্যে ওই দুজন অভিভাবককে ডেকে কোনো স্পেশাল শলা করছিলো। আমি তো চিল্লামিল্লি করা মন্দ পাবলিক, আমার সঙ্গে শুদ্ধু মাপামাপির সম্পর্ক। খুবই কড়া খর শুভদৃষ্টি বিনিময় হচ্ছিলো।
সমস্ত কাগজ পত্তর ব্যাগজাত করে কন্যাকে সটান গাড়িতে পাঠিয়ে দিয়ে এবার মামদোদের মুখোমুখি হলাম।
“ঊণত্রিশ তারিখ এখানে রমেশ বলে একজনের হাতে ওই উইদাউট রিসিট রিফান্ডের অ্যাপ্লিকেশন জমা দিয়ে গিয়েছি। ওটা কবে পাবো?”
“পাবেন না।”
“কেন?”
এবার মামদোটি তেড়ে এলেন। “কী করে পাবেন, হ্যাঁ! কী করে পাবেন? আজ টিসি নিচ্ছেন, আর আগে রিফান্ডের অ্যাপ্লিকেশন দিয়েছেন, এমন হয় না কি?”
আমি মিটিমিটি হাসলাম। রিফান্ড হবে না, সে তো বহু আগেই বুঝে গিয়েছি। ন্যাংটার নেই বাটপারের ভয়। পেটে ছুঁচো ডনবৈঠক দিচ্ছে, কিন্তু এক্ষেত্রে মুড তো পুরা হাল্কা ফুলকা। “রিফান্ড না হবার লজিকটা কী?”
“রেজিস্ট্রেশন হয়ে গিয়েছে, এখন টাকা ফেরত চাইছেন! আজঅব!”
বলেই, বিশাল আপার হ্যান্ড নিয়ে মামদো ছোটা-হুমদোদের বললো,
“ইনাকে দেখো। এর মাইগ্রেশনের ব্যাপারটা করে দাও।”
তা বটে। মাইগ্রেশন তো লাগবে। ফ্রম সাউথ বেঙ্গল স্টেট ইউনিভার্সিটি টু যাদবপুর কেস তো।
মামদোটি খুব সিরিয়াস মুখে কাউন্টারের ওপার থেকে আমায় বললেন,
“এক নম্বর কাউন্টারে চলে যান। বারোশ টাকা জমা দিন। একটা কাগজ দেবে। ওটায় মাইগ্রেশনের অ্যাপ্লাই করুন।”
আমার পাশে দন্ডায়মান দুজন গার্জিয়ান শশব্যস্তে আমায় বললেন,
“এখনো অ্যাপ্লিকেশন জমা দেন নি! এ বাবা! দিদি, আপনাকে আবার এখানে আসতে হবে!”
আমি কিরকম দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। তখন বোধহয় পাঁচটা বেজে গেছে। খিদে ক্লান্তিতেই সব ছায়া ছায়া লাগছে, না কি সত্যিই অন্ধকার—!
তবুও—
ব্যাগ থেকে ঝকঝকে মাইগ্রেশন ফর্ম বের করলাম।
এখানে আসার আগে, মানে টিসির জন্যে এটা তো আমার তিন নম্বর ভিসিট— অনেক আগেই ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইট থেকে মাইগ্রেশন ফর্মটার প্রিন্ট আউট নিয়ে রেখেছিলাম।
এবার সেইটা বের করে বললাম,
“মাইগ্রেশন ফর্ম ফিলাপ করাই আছে। তবে অনেক খুঁজেও রেজিস্ট্রেশন নম্বরটা পাই নি।
দয়া করে যদি রেজিস্ট্রেশন নাম্বারটা দেন, আমি আজই এই ফর্মটা জমা দিয়ে যাবো।”
মামদোর মুখ তোম্বা। অন্য অভিভাবকরা মাইগ্রেশন ফর্ম-এর ওপর ঝুঁকে পড়েছেন—-
“একেবারে প্রিন্ট আউট বের করে নিয়ে এসেছেন, দিদি!”
অভিভাবকটির বিস্ময়ে অবাক হলাম। এ তো এমন কিছু হাতী ঘোড়া বিষয় নয়! কিন্তু যথেষ্ট বিস্মিত হবার মতোও আর এন্থু তখন ছিলো না। খুব ক্লান্তভাবে হ্যাঁ-বাচক মাথা নেড়ে মামদোকে বললাম,
“রেজিস্ট্রেশন নাম্বারটা একটু বলুন, প্লিজ।”
“রেজিস্ট্রেশন নম্বর কোথায় পাবো!”
আমি তো খুবই ট্যাটন প্রজাতি, আমার আসপাশের সব পাব্লিকই এইটে সম্যক জানেন। আমার নষ্টামি বুদ্ধি আবার তিড়িং বিড়িং নাচলো।
মাইগ্রেশন ফর্মের বাঁ দিকের চৌকো খোপ্পা দেখিয়ে বললাম,
“বারশ টাকার গপ্পোটা কী ভাই? এখানে তো লেখা আছে মাইগ্রেশনের জন্য সাড়ে চারশ টাকা লাগবে!”
মামদো ভীষন বিরক্ত। অভিভাবকরা উৎকর্ণ। কারণ ইতিমধ্যে বেচারারা বারোশ টাকা দিয়ে ফেলেছেন। বাচ্চা দুটি ছেলে, চন্দননগর শ্রীরামপুর থেকে টিসির জন্যে এসেছে, তাদের কাছে বারোশ টাকা আজ নেই বলে তারা খুবই বিপন্ন হয়ে দাঁড়িয়েছিলো,
এবার তারাও এগিয়ে এসেছে।
মামদো আর আমার দিকে তাকাচ্ছেন না। আমার মাথার ওপর দিয়ে তাকিয়ে বললেন,
“বারোশ টাকা দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে।”
“মানে, রেজিস্ট্রেশন এখনো হয় নি?”
একটু ইতস্তত করে মামদো বললেন,
“অনলাইনে হয়েছে।”
“তাহলে সেই অনলাইন রেজিস্ট্রেশনের নম্বর দিন। আমি মাইগ্রেট করবো।”
“অনলাইন রেজিস্ট্রেশনের নম্বর আমরা জানি না। এখানে যা হবে, সব অফলাইন, ফিজিক্যাল।”
“ওহ্! সব অফলাইন! শুধু অনলাইনে অ্যাডমিশনটা আপনারা অ্যাক্সেপ্ট করবেন? বাঃ! বা বা বাহ্!”
অভিভাবক দুজন হায় হায় করে উঠলেন।
“রেজিস্ট্রেশন হয়ই নি! তাহলে আমরা যে দু-হাজার টাকা দিলাম!”
এবার আমি থ!
দু হাজার টাকা দিলেন মানে? বারোশ দিয়েছেন না?
একজন গার্জিয়ান হাঁউমাউ করে বললেন,
“ওই তো, এনারাই তো বললেন, ওই ছেলেগুলোকে দু-হাজার মতো দিলে আজকের মধ্যেই ওরা মাইগ্রেশন করিয়ে দেবে!”
অ! ওইজন্যেই কাকু হুমদোদের ঘন্টাখানেক দেখছি না!
পাঠক, আপনারা টাকা যোগ করছেন তো? দেখুন, যোগ করুন,
কী পরিমাণ দোহন চলছে, ভাবুন!
আমার হাতে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট আছে। রেজিস্ট্রেশন এখনো হয়ই নি। অথচ টুপি পরিয়ে বারোশ টাকা দিয়ে চার ঘন্টার মধ্যে রেজিস্ট্রেশন নম্বর পাইয়ে দেওয়ার জন্য হুমদোদের আরো দু-হাজার করে টাকা দিতে হয়েছে।
বলা হয়েছে, ওরা না কি মাইগ্রেশন করিয়ে দেবে।
বাৎসল্যে ডুবুডুবু গাজ্জেনদের এরা নধর মুর্গা ভাবে।
সন্ধ্যা পৌনে ছ’টায় চত্ত্বর ছাড়লাম। বয়স্ক ভদ্র বোকা বনে যাওয়া গার্জিয়ানরা হাঁ করে তাকিয়ে আছেন।
তাঁরা এবার নতুন চক্করে জড়িয়েছেন।
যে কলেজ থেকে টিসি হয়েই গিয়েছে, তার ঊর্ধ্বতন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রেশন করাচ্ছেন! কী চক্র!
কী বিদঘুটে জাল!
রাষ্ট্রগুরুর ক্ষুরে ক্ষুরে প্রণিপাত, বাবা!
আমি বেঁচে গিয়েছি!
নে বাবা! তোরা আমার ভত্তির টাকা দিয়ে প্যানডেমিক পিকনিক কর। তোদের ওই টাকা খয়রাতি দিলাম।
(শেষ)

