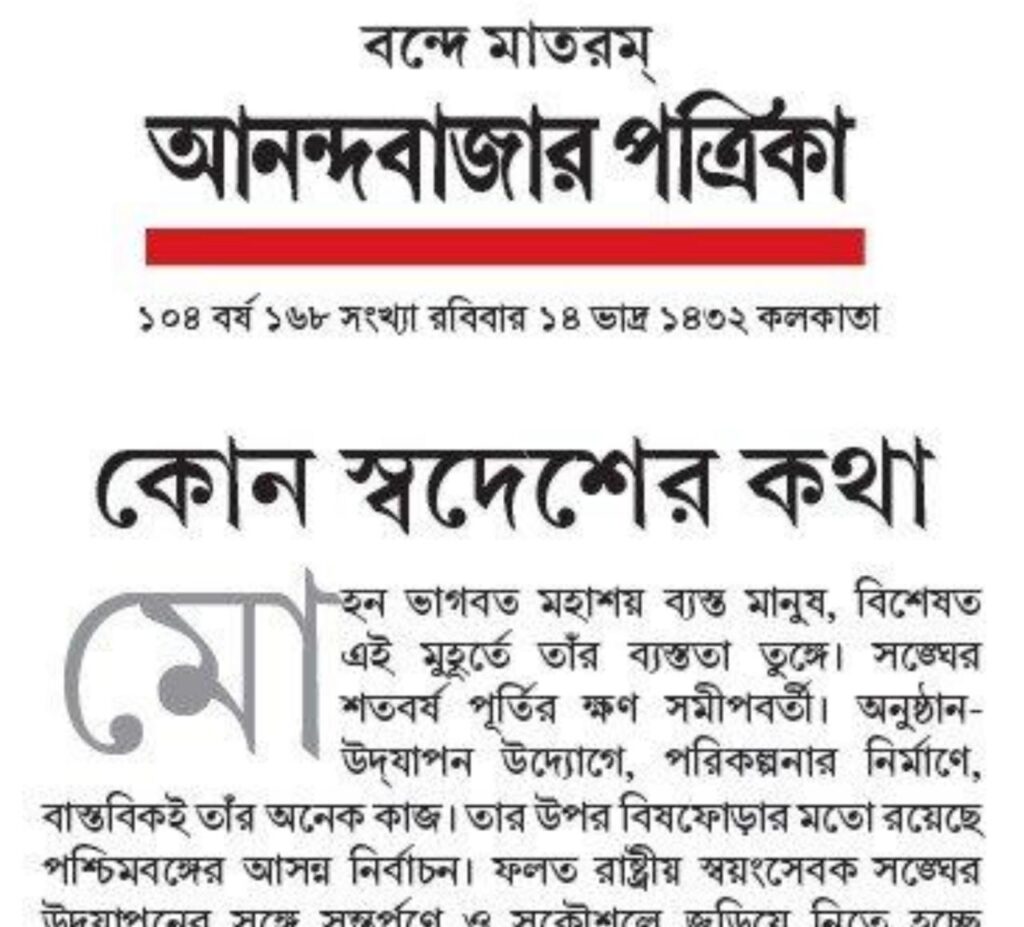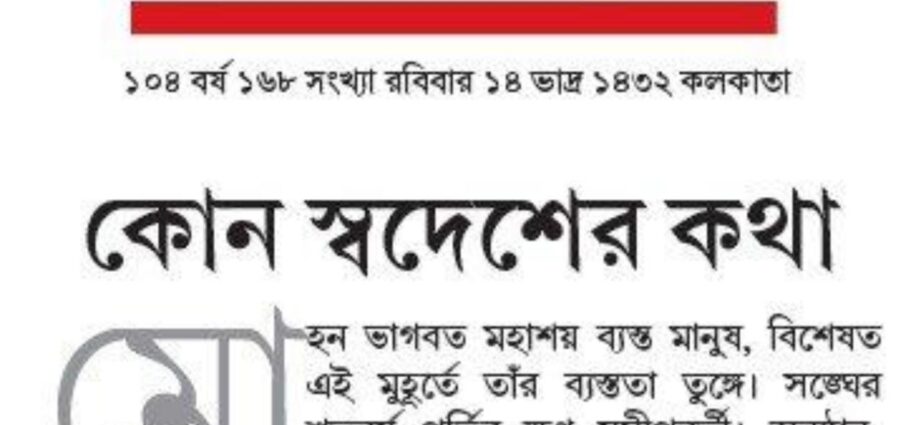আনন্দবাজার পত্রিকার ‘কোন স্বদেশের কথা’ শীর্ষক সম্পাদকীয় তে লেখকের বক্তব্য ও ভারতীয় আদর্শের ভিত্তিতে সমাজ গঠনের মধ্যে বিরোধ স্পষ্ট।
আর এস এসের সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত ভারতীয় আদর্শ কে সামনে রেখে সমাজ জাগরণের বার্তা দিয়েছেন আর নিজের বক্তব্য কে পুষ্ট করতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘স্বদেশী সমাজ’ প্রবন্ধের পুনঃস্মরণ করেছেন।
অন্যদিকে আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় তে পশ্চিমবঙ্গে আকাঙ্খিত ও প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক লক্ষ্য কে সঙ্ঘের মতাদর্শের সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে ব্যাপারটি কে দুর্বোধ্য করার চেষ্টা হয়েছে। বাংলা দৈনিকের সম্পাদকমণ্ডলীর মাথায় পশ্চিমবঙ্গের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন যে প্রভাব বিস্তার করবে তা স্বাভাবিক কিন্তু এতটাও করা উচিত কি না যে , শতবর্ষের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে সঙ্ঘের নতুন দিগন্তের বার্তা ( নয়া ক্ষিতিজ) কেও সেই নির্বাচনী হিসেব-নিকেষের মধ্যেই রাখতে হবে সে নিয়ে আলোচনার অবকাশ রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি নির্বাচনে যে হিংসাত্মক ঘটনাগুলো বাঙালির মাথা নিচু করে দেয়, তার পেছনে সবকিছুকেই রাজনৈতিক চশমা দিয়ে দেখার এই প্রবনতার প্রভাব অস্বীকার করা যায় না।
পশ্চিমবঙ্গের ‘বাঙালি’ শুধুমাত্র ক্ষমতা দখলের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের মতাদর্শের দিকে ঝুঁকে গিয়ে দীর্ঘ প্রায় চার দশকের বেশি সময় ভারতীয়ত্ব দ্বারা সিক্ত বাঙালি মনীষার থেকে ক্রমশঃ দূরে সরে গিয়েছে আর বলাই বাহুল্য ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি মনীষীদের চিন্তন, ভারতীয় সংস্কৃতির বিপরীতে ছিল না।
কিন্তু বিদেশীয় মতাদর্শের প্রভাবাধীন মস্তিষ্ক কবিগুরুর ‘স্বদেশী সমাজ’ কে বুঝতে বারবার ব্যর্থ হয়েছে এবং এবারেও যে তার ব্যতিক্রম হয় নি তা মোটেই অবাক করে না।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রবন্ধগুলো ইংরেজি তে পাঠ করে তার মর্মার্থ উপলব্ধি নাও করা যেতে পারে কারণ ভাষান্তর করলে ভাবেরও অন্তর হয়ে যায় কিন্তু ভারতের অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষার সঙ্গে এই সমস্যা নেই।
উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজেই তার ‘ভারতবর্ষের ইতিহাস’ প্রবন্ধে ‘Religion’ যে ‘ধর্ম’ শব্দটির সমার্থক নয় তা দ্বিধাহীনভাবে বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘ভারতবর্ষীয় সমাজ’ প্রবন্ধে ‘নেশন’ – এর অর্থ সম্পর্কে বিভ্রান্তি দূর করতে বলেছেন —
“এই লোকচিত্তের একতা সব দেশে এক ভাবে সাধিত হয় না। এইজন্য য়ুরোপীয়ের ঐক্য ও হিন্দুর ঐক্য একপ্রকারের নহে, কিন্তু তাই বলিয়া হিন্দুর মধ্যে যে একটা ঐক্য নাই, সে কথা বলা যায় না। সে-ঐক্যকে ন্যাশনাল ঐক্য না বলিতে পার– কারণ নেশন ও ন্যাশনাল কথাটা আমাদের নহে, য়ুরোপীয় ভাবের দ্বারা তাহার অর্থ সীমাবদ্ধ হইয়াছে।”
এমনকি ভারতীয় ভাব প্রকাশে বিদেশী ভাষার সীমাবদ্ধতা বোঝাতে বিশ্বকবি বলেছেন — “উপনিষদের ব্রহ্ম, শংকরের মায়া ও বুদ্ধের নির্বাণ শব্দ ইংরেজি রচনায় প্রায় ভাষান্তরিত হয় না, এবং না হওয়াই উচিত”।
বিদেশী ভাষাকৃত এই ‘ভাবান্তর’ থেকে রক্ষা করতে আর ‘স্বদেশী সমাজ’ কে বোঝার পৃষ্ঠভূমি তৈরি করতে কবিগুরু প্রথমে ‘নেশন কি’ প্রবন্ধ লিখেছিলেন।
তাই সম্মানীয় মোহন ভাগবত কে বারবার ‘স্বদেশী সমাজ’ প্রবন্ধের ইংরেজি অনুবাদ পড়তে বলে সম্পাদক মহাশয় কবিগুরুর ভাবের সহিত সঠিক ভাষান্তর সম্পর্কে সচেতনতা থেকে নিজেকে দূরে রেখেছেন।
কিন্তু এই দূরত্ব রেখে ‘স্বদেশী সমাজ’ কে বোঝা দুষ্কর।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজের ‘জীবনস্মৃতি’ তে বলেছেন যে নবগোপাল মিত্রের ‘হিন্দুমেলা’ থেকেই তাঁর মনে স্বাদেশিকতার বীজ বপন হয়েছিল। তাঁর জ্যোতিদাদা, রাজনারায়ণ বসু সেই হিন্দুমেলার হোতা আর ‘স্বদেশী সমাজ’ – এর ‘নায়ক’ , এই যুগে যাদের আহ্বান করেছেন সঙ্ঘ প্রধান। বুঝতে হবে এই ‘হিন্দু মেলা’ বা ‘হিন্দু’ আদর্শ কে কেন্দ্র করেই কেনো স্বদেশী সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় ঐক্যের ভিত তৈরি হয়েছিল। তাঁর উত্তর আছে ‘আত্মশক্তি’ প্রবন্ধ-সংকলনেই —- “হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খ্রীস্টান ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে পরস্পর লড়াই করিয়া মরিবে না– এইখানে তাহারা একটা সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাইবে। সেই সামঞ্জস্য অহিন্দু হইবে না, তাহা বিশেষভাবে হিন্দু। তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যতই দেশবিদেশের হউক, তাহার প্রাণ, তাহার আত্মা ভারতবর্ষের”।
বিশেষভাবে ‘হিন্দু’ হলে, তবেই আত্মাটা ভারতবর্ষের থাকে, নচেৎ নয় — এ নিয়ে কোনো দ্বিধা রাখেন নি বিশ্বকবি। তবে এ শুধু তাত্ত্বিক কথাই নয় , বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের আবহে যে ‘স্বদেশী’ আন্দোলন ইংরেজদের স্তম্ভিত করেছিল তাঁর কেন্দ্রে যাদের নাম আমরা পাই তাদের কথাতেও এই সারমর্মটিই ফুটে ওঠে — ঋষি অরবিন্দের ‘উত্তরপাড়া অভিভাষণ’ হোক বা বিপিনচন্দ্র পালের ‘The Soul of India’ , কবিগুরুর কথার প্রতিধ্বনি সর্বত্র। রবীন্দ্রনাথের ইপ্সিত নায়কেরাই সেসময় ‘স্বদেশী সমাজ’- এর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন আর সেই নায়কদের একজন কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দু’দুবার বলেছিলেন ‘অরবিন্দ , রবীন্দ্রের লহ নমস্কার’।
তাই সমাজ কে ‘স্বদেশী’ করতে ‘হিন্দু’ নেতার অর্থাৎ হিন্দু আদর্শে প্রেরিত নেতারই কেনো প্রয়োজন তার উত্তর ‘স্ব’তন্ত্রতা সংগ্ৰামের স্বদেশী যুগেই নিহিত রয়েছে।
‘যেন তেন প্রকারেণ’ ক্ষমতা দখল করে সমাজ পরিবর্তনের নীতি কে মহৎ বিবেচনা করে, সেই নীতির প্রয়োগকর্তাদের এই পশ্চিমবঙ্গে ‘নায়ক’ বানানো হয়েছে ; তাদের নামে রাস্তা হয়েছে , মূর্তি হয়েছে। তাই স্বতন্ত্রতা সংগ্রামের সময় বাংলা তথা ভারতের নায়কদের আদর্শের স্পষ্টতা আরো বেশি করে বোঝা প্রয়োজন। তবেই রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে আমরা ‘স্ব’তন্ত্রতার পথে আরো এগোতে পারবো।
সমাজের সমস্যার সমাধান ও উন্নতি কে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের অপেক্ষায় স্থগিত রাখা বা সমাজের শুধুমাত্র সরকারের মুখাপেক্ষী থাকা, ‘স্বদেশী সমাজ’ তথা হিন্দু আদর্শে রাষ্ট্রগঠনের পরিপন্থী — “সমাজকে শিক্ষাদান, স্বাস্থ্যদান, অন্নদান, ধনসম্পদ-দান, ইহা আমাদের নিজের কর্ম; ইহাতেই আমাদের মঙ্গল– ইহাকে বাণিজ্য হিসাবে দেখা নহে, ইহার বিনিময়ে পুণ্য ও কল্যাণ ছাড়া আর কিছুই আশা না করা, ইহাই যজ্ঞ, ইহাই ব্রহ্মের সহিত কর্মযোগ, এই কথা নিয়ত স্মরণ করা, ইহাই হিন্দুত্ব। স্বার্থের আদর্শকেই মানবসমাজের কেন্দ্রস্থলে না স্থাপন করিয়া, ব্রহ্মের মধ্যে মানবসমাজকে নিরীক্ষণ করা, ইহাই হিন্দুত্ব”। ( আত্মশক্তি – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)
শুধু বিদেশী ভাষাই নয় , বিদেশী মতাদর্শ কৃত ভাবান্তরের জন্যই বাঙালি সমাজ কে ‘ভারতবর্ষীয় সমাজ’ থেকে বিচ্যুত করতে ‘হিন্দু’ ও ‘হিন্দুত্ব’ কে ঘোলাটে করে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে কিন্তু বাঙালি যদি তাঁর নবজাগরণের নায়কদের অবিকৃতভাবে গ্ৰহণ করে তাহলে বিদেশীয় নায়কদের বর্জন করে যে ‘স্বদেশী সমাজ’ গড়ে উঠবে তা ভারতবর্ষ কে পুষ্ট করবে।
[ লেখক একটি উচ্চ বিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার শিক্ষক]
পিন্টু সান্যাল