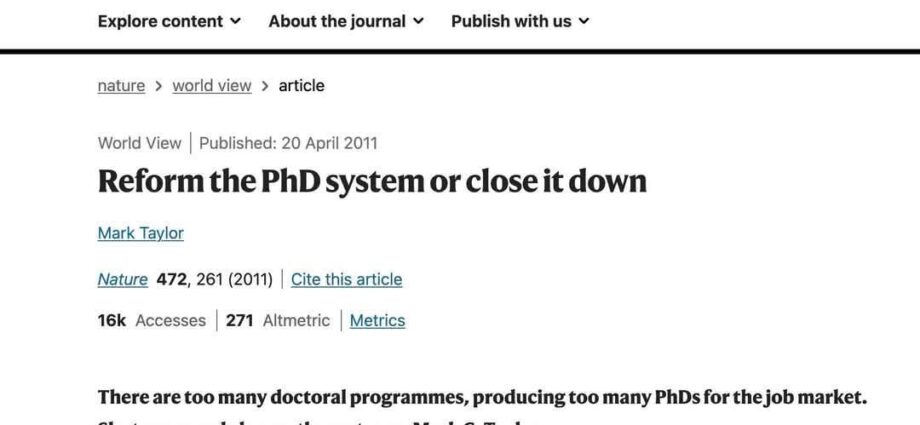কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটির প্রফেসার মার্ক সি. টেলরের নেচারে প্রকাশিত একটি লেখা ঘুরছে সমাজ মাধ্যমে। মার্ক বলছেন, অনেক বেশি পিএইচডি তৈরি হচ্ছে, যা চাকরির বাজারের তুলনায় অতিরিক্ত । তাই এই ব্যাবস্থার আশু সংস্কার দরকার। মার্ক যা লিখছেন তা আলোচনা করলাম।
পিএইচডি শিক্ষাব্যবস্থা বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অনেক দেশের জন্যই ভেঙে পড়েছে বা পড়বে। এটা নিয়ে আশু ভাবনাচিন্তার প্রয়োজন। অনেক ক্ষেত্রেই, পিএইচডি কেবল ভবিষ্যতের একটা চাকরির আশার জন্য শুরু করা হয়, যা আসলে বিভ্রম। পিএইচডি প্রোগ্রাম আসলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের স্বার্থরক্ষার কাজ করে এবং শিক্ষার্থীদের ক্ষতির কারণ হয়। বাস্তবে পিএইচডির জন্য বহু বছর ব্যয় করার পর খুব কম লোকই উপযুক্ত চাকরি যোগাড় করতে পারে।
বেশিরভাগ পিএইচডি প্রোগ্রামগুলো মধ্যযুগীয় ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয় কাঠামোর উপর ভিত্তি করে তৈরি, যেখানে শিক্ষা ব্যবস্থা আসলে আরেকজন শিক্ষক তৈরির ছাঁচ ছাড়া কিছু নয়। ফলে, শিক্ষকের চাকরির সংখ্যা আর পিএইচডির সংখ্যায় বিস্তর ফারাক। ১৯৭০-এর দশকে একাডেমিয়া নির্ভর চাকরির বাজার ভেঙে পড়লেও, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এখনো তাদের ভর্তি নীতিতে পরিবর্তন আনেনি, কারণ তাদের গবেষণাগার ও প্রকল্প চালাতে পিএইচডি গবেষকদের প্রয়োজন হয়। কিন্তু পিএইচডি শেষ করার পর, গবেষকদের আর কর্মসংস্থান নেই।
বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও বর্তমানে আর্থিক সংকটে আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয় ২০০৮ সালের আর্থিক মন্দার পর থেকে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ পুনরুদ্ধার করতে পারেনি এবং সম্ভবত কখনোই আর পারবে না। সরকারি ও বেসরকারি উভয় ধরনের অনুদান কমছে, ফলে অনেক বিশ্ববিদ্যালয় তাদের পিএইচডি শিক্ষানীতি পরিবর্তন করতে বাধ্য হবে, যদিও তারা তা করতে চাইবে না। (তবে ট্রাম্প সরকারের আর্থিক নীতি রূপায়িত হলে, এই শিক্ষানীতির পরিবর্তন হবে আর্থিক সমস্যার কারণে। এখনই অনেক বিশ্ববিদ্যালয় এবছর পিএইচডি গবেষক নিয়োগ আপাতত স্থগিত রেখেছে।আর এর ফল ভারতেও পড়বে (১)।)
এই অচলাবস্থার দুটি সম্ভাব্য সমাধান হতে পারে- এক,পিএইচডি প্রোগ্রামের মৌলিক সংস্কার করা, নয়তো, পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া।
বিভিন্ন বিষয়ে পিএইচডির প্রাসঙ্গিকতা হারাবার অন্যতম কারণ হলো, এগুলো বৃহত্তর বিষয়ের খুব নির্দিষ্ট বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। যখন সেই বিশেষ ক্ষেত্রটি সমাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়, তখন অবশ্যই সেটি ভালো। কিন্তু বাস্তবে, বেশিরভাগ সময়েই এই বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র এতটাই সংকীর্ণ হয়ে যায় যে, এটি শুধুমাত্র নির্দিষ্ট গবেষণা ক্ষেত্রের জন্যই বিশেষ দক্ষতা তৈরি করে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে কার্যকর হয় না। ফলে, অনেক গবেষক তাদের জ্ঞানকে বাস্তব জীবনের সাথে খাপ খাওয়াতে পারেন না। (তবে এটা একটু জটিল বিষয়। সব গবেষণাই বাস্তব জীবনের সঙ্গে খাপ খাবে তা হওয়া খুব মুশকিল। প্রযুক্তি আর চিকিৎসাক্ষেত্র ছাড়া যেকোন গবেষণার সঙ্গে সরাসরি সমাজের যোগ বার করা মুশকিল। যেমন, কয়েক মাইল টানেল খুঁড়ে গড পার্টিকেল খোঁজার সঙ্গে সমাজের সরাসরি যোগ নেই, স্ট্রিং থিওরির গবেষণার সমাজের সঙ্গে যোগ নেই, এগুলোই কেন সাহিত্য, ইতিহাস সব নিয়েই বলা যায়, যে এসব না হলেও চলে, কারণ এগুলো খালি একাডেমিক চর্চার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু সেটা বাস্তব মানেই সঠিক তা নয়, কারণ মানব সম্পদ উন্নয়ন ও জ্ঞান আহরণও সমাজের জন্য প্রয়োজন। নয়তো সমাজব্যাবস্থাই ভেঙে পড়ে। কোন আই টি কোম্পানি বলতেই পারে, আমি খালি সফটওয়ার ইঞ্জিনিয়ার নেব, তাতে দোষ নেই। কিন্তু কোন দেশ বা সমাজ, খালি সফটওয়ার ইঞ্জিনিয়ার দিয়ে তো চলবেনা। মানবসম্পদ উন্নয়নে সরকারকে বৃহত্তর স্বার্থে অবশ্যই ব্যয় করতে হবে (২)।)
শিক্ষাব্যবস্থাকে টিকে রাখতে হলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে নতুন কৌশল গ্রহণ করতে হবে। তাদের উচিত বহুমুখী গবেষণার প্রচলন করা, যেখানে বিভিন্ন শাখার মিশ্রণে গবেষণা হবে, যেমন জলবায়ু সমস্যা, সামাজিক অস্থিরতা, স্বাস্থ্য, এবং প্রযুক্তির পরিবর্তন। তবে এই রূপান্তর করা সহজ হবে না, কারণ বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা ঐতিহ্যগত পদ্ধতির প্রতি অন্ধভাবে অনুগত। ( বিদেশে এখন বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের বৃহত্তর কোলাবরেশানে কাজ হলেও, ভারতে এর ঝোঁক খুব কম বলেই মনে হয় (৩))। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উচিত নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা কমিয়ে সহযোগিতার পরিবেশ তৈরি করা। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় আলাদা সিদ্ধান্ত নিলে সমস্যার সমাধান হবে না। বরং সম্মিলিতভাবে একটি কার্যকর সমাধান খুঁজে বের করতে হবে। একাডেমিক জগতে মানদণ্ড এখনো বিভাগের পিএইচডি প্রোগ্রামের সংখ্যা দ্বারা নির্ধারিত হয়, ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অপ্রয়োজনীয়ভাবে এসব চালিয়ে যাচ্ছে। সমাধানের জন্য, কম প্রয়োজনীয় বা অপ্রাসঙ্গিক পিএইচডি প্রোগ্রাম বন্ধ করতে হবে। এই কঠিন সিদ্ধান্তগুলো বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, এবং একাডেমিক বিশেষজ্ঞদের পরামর্শে নিতে হবে। (যদিও ব্যাপারটা খুব শক্ত। কোনটা প্রয়োজনীয়, কোনটা অপ্রয়োজনীয় নির্ধারণ করা খুব শক্ত। মহাকাশ গবেষণা কারো অপ্রয়োজনীয় মনে হতে পারে, কিন্তু মহাকাশ গবেষণার জন্যেই আজ স্যাটালাইট মাধ্যমে আমরা পাচ্ছি, জিপিএস, ইন্টারনেট, আবহাওয়ার পূর্বাভাস সবই। সার্ণের পার্টিকল ফিজিক্সের সরাসরি ফল আজ কয়েক বছরে ১.২ এমবির ফ্লপি থেকে টিবি টিবি হার্ডড্রাইভের সহজলভ্যতা। বা, কোন সরকারের মনে হল, ভ্যাকসিন আসলে ক্ষতিকর, অপ্রয়োজনীয়, সেটা বন্ধ করে দেওয়া উচিৎ, সেটা কি সঠিক সিদ্ধান্ত হবে? বা কে ঠিক করবে, এই সিদ্ধান্ত, সেটাও প্রশ্ন। যাই হোক, এতো বিজ্ঞানের ক্ষেত্র। এবার সাহিত্যের ক্ষেত্রেও কী বলা যায় শেক্সপিয়ার বা জীবনানন্দ নিয়ে গবেষণা অপ্রয়োজনীয়? বা, মানুষের পরিযানের ইতিহাস অপ্রয়োজনীয়? (৪)।)
শিক্ষার্থীদের উচিত আরও অভিজ্ঞ শিক্ষক এবং বৈচিত্র্যময় শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাওয়া, যেখানে বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জনের ব্যবস্থা থাকবে। বাস্তবতায়, কম পিএইচডি প্রোগ্রাম চালু করা হলে এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা হলে একাডেমিক চাকরির বাজারে আরও ভারসাম্য আসবে। ( ভারতে সেই হিসেবে পিএইচডির সংখ্যা বেশি নয়। জনসংখ্যার তুলনায় নগণ্য। নেটের সাফল্যের হার পাঁচ শতাংশেরও কম। ভারতে ইউনিভার্সিটি, ইন্সটিটিউটে নিয়োগ খুব কম, ইন্ডাস্ট্রির অভাবের জন্য মনে হয়, যেন গাদা গাদা পিএইচডি ঘুরছে। আসলে এটা দূর্ভাগ্যই বলা যায় ছাত্রছাত্রীদের যারা বেসিক সায়েন্স নিয়ে কিছু করতে চায় (৫)।)
উচ্চশিক্ষার ভবিষ্যৎ এখন সংকটের মুখে। প্রযুক্তির পরিবর্তন এবং বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে। আগামী কয়েক বছরে এটি আরও কঠিন হয়ে উঠবে। সুতরাং, পিএইচডি ব্যবস্থার সংস্কার করা না হলে, এটি ধ্বংস হয়ে যাবে। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ও সমাজের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে, আমরা এখন কীভাবে সিদ্ধান্ত নিই তার ওপর। (ভারতে আমরা জানি বিভিন্ন অভিজাত প্রতিষ্ঠানেও বিজ্ঞানে পিএইচডির আগ্রহ কমছে, তাই ভারতে হয়তো নিজের নিয়মেই এটা শেষ হয়ে যাবে, আগামী কয়েক দশকে (৬)।)
আমার সংযোজনঃ (১-৬)
Collected